ভাইরাস সম্পর্কে প্রথমেই যেটা বুঝতে হবে তা হলো, এরা নির্জীব। এদের মধ্যে জীবন্ত কোষের খুব কম বৈশিষ্ট্যই উপস্থিত। এদের একটা প্রোটিনের আবরণী আছে সত্যি, কিন্তু এর ভেতরে না আছে কোন নিউক্লিয়াস, না আছে পাওয়ারহাউস মাইটোকন্ড্রিয়া, নেই কোন রাইবোজম। এসব ছাড়াও ভাইরাস কিন্তু ঠিকই তার বংশগতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিতে পারে। তাই এদের আবরনীর ভেতরে আর কিছু না থাকলেও কিছু সংখ্যক জিন ঠিকই রয়েছে।
আসলে ভাইরাস সামান্য কিছু প্রোটিনে মোড়ানো অল্প কিছু ডিএনএ কিংবা আরএনএ। কখনো কখনো এদের প্রোটিন আবরণের এখানে ওখানে টুকটাক লিপিড দেখা যায়। তবে বংশবিস্তারের ক্ষমতার বিচারে ভাইরাস যেকোন জীবিত সত্তার চেয়ে বেশি পারদর্শী। এটা সত্যি, ভাইরাসের বংশবিস্তারের জন্য তাকে অন্য কোষকে আক্রান্ত করতে হয়, সেই আক্রান্ত কোষের পুষ্টি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেই নতুন ভাইরাস জন্ম নেয়। অবশেষে আক্রান্ত কোষটি মরেও যেতে পারে। তবে এটা নিয়ে আসলে রাজনীতি করার কিছু নেই, আমরা মানুষেরাই তো বেঁচে থাকার জন্য কত কত প্রাণী মেরে ফেলি। নিজে জীবন্ত না হয়েও, নিজের সব কাজ অন্যকে দিয়ে করিয়ে নেয়ার দক্ষতাতেও কিন্তু ভাইরাস অন্য সব জীবসত্তার চেয়ে এগিয়ে।

যেহেতু ভাইরাস জীবিত নয় তাই আমাদের অনাক্রম্য ব্যবস্থা তার কিছু স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা কৌশল যেমন ‘ভাইরাস নাশক প্রোটিন’ কিংবা কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম এদের প্রতিরোধে ব্যবহার করতে পারেনা। যে বেঁচেই নেই তাকে আপনি আবার মারবেন কি-ভাবে? এই একই কারণে অ্যান্টিবায়োটিক ভাইরাসের বিরুদ্ধে অকার্যকর। তাহলে কি উপায়? ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন অস্ত্র হচ্ছে টাইপ ১ ইন্টারফেরন।
এই ইন্টারফেরন তৈরি করে সাধারণত শ্বেত কণিকা এবং সারা দেহে ছড়িয়ে থাকা যোজক কলা। যখন এরা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন টাইপ ১ ইন্টারফেরন তৈরি করে। এছাড়াও ডেন্ড্রাইটিক কোষও ভাইরাসের আক্রমনের শিকার হলে এই ইন্টারফেরনের নিঃসরন ঘটায়। যখন আশেপাশের কোন কোষ এই ইন্টারফেরনের উপস্থিতি টের পায় তখন সে নিজেকে স্বাভাবিক কার্যাবলি কমিয়ে লক ডাউন করে ফেলে, যাতে করে কোন ভাইরাস তাকে আক্রান্ত করতে না পারে।
ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ন। কিছু কিছু অ্যান্টিবডি ভাইরাসের প্রোটিনকে এমনভাবে ট্যাগ করে যাতে পরবর্তীতে ম্যাক্রোফেজ ফ্যাগোসাইটোসিসের মাধ্যমে এসব প্রোটিনকে নষ্ট করতে পারে। অনেক ভাইরাসের ক্ষেত্রেই একবার শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে গেলে বাকী জীবনের জন্য সেটাই যথেষ্ট।
তবে ঝামেলা টা বাঁধে যখন ভাইরাস রক্ত কিংবা লসিকার প্রবাহে না থেকে একেবারে কোষের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকে। তখন আর অ্যান্টিবডি এদের সহজে খুঁজে পায়না। বেশিরভাগ ভাইরাস কোষের ভেতরে বড় হয়, বংশবৃদ্ধি করে, তারপর কোষটিকে ধ্বংস করে দিয়ে ছানাপোনা ভাইরাস গুলো বের হয়ে অন্য কোষকে আক্রান্ত করে। যখন তারা এক কোষ থেকে অন্য কোষে যাচ্ছে, সেই সময়টায় অবশ্য যদি অ্যান্টিবডি এদেরকে ধরে ফেলতে পারে, তখন তার পোয়া বারো।
কিন্তু আরো অনেক ভাইরাস আছে যারা কোষের ভেতরেই জীবনের সিংহভাগ কাটিয়ে দেয়। তারা এমনভাবে থাকে এবং এত ধীরে বংশবৃদ্ধি করে যাতে কোষটি মারা না যায়। নতুন ভাইরাস কোষ প্রাচীর দিয়ে বের হয়ে পার্শ্ববর্তী সংযুক্ত কিংবা কাছাকাছি দূরত্বের কোন কোষে ঢুকে যায়। এই ধরনের ভাইরাসের জন্য অ্যান্টিবডি কিছুই করতে পারেনা বললেই চলে। কারণ অ্যান্টিবডি কখনো কোষের ভেতরে ঢুকতে পারেনা।
এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে আসলে আমাদের কোষের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর ভরসা করতে হয়। একটি কোষ যখন ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ভাইরাস কোষের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে নিজের জন্য বিভিন্ন প্রোটিন তৈরি করতে শুরু করে তখন কোষ নিজে থেকে সেই প্রোটিনগুলোর কিছু কিছু ভেতর থেকে বের করে এনে তার প্রাচীরের গায়ে মেলে দেয় খুনে টি কোষ ওরফে CD8 টি কোষের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য।
খুনে টি কোষ যখন এই প্রোটিনগুলো পরীক্ষা করে বুঝতে পারে যে এটা ভাইরাল প্রোটিন তখন সে কোষের সাথে কিছু একটা করে এরপর অন্য কোষকে খুজে বের করে যার গায়ে একই প্রোটিন দৃশ্যমান। খুনে টি কোষ আক্রান্ত কোষকে ছেড়ে দেয়ার পরপরই কিছু একটার কারনে কোষটি কয়েক-গুন ফুলে ফেপে উঠে, এর মেমব্রেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ভেতরের সব কিছু বের হয়ে কোষটি মারা যায়।
এই কিছু একটা কি জিনিস সেটা খুঁজে পেতেই বিজ্ঞানীদের ২০ বছর লেগে যায়। কিভাবে খুনে টি কোষ এভাবে একটা কোষকে মারতে পারে? সবাই আসলে খুজছিলেন কোন একটা অস্ত্র যেমন বন্দুক, তলোয়ার বা বিষাক্ত কিছু। কিন্তু না, সেরকম কোন অস্ত্রই পাওয়া যায়নি। যখন শেষ পর্যন্ত সমাধান পাওয়া গেলো দেখা গেলো তা একই সাথে খুবই সাধারণ এবং গূঢ়, আত্মহত্যা।
সত্যিকারে যেটা ঘটে তা হলো আমাদের সব কোষেরই প্রয়োজনে আত্নহত্যার একটা প্রবণতা রয়েছে। যেটার নাম হলো অ্যাপোটসিস। এই প্রয়োজনটা একেক কোষের ক্ষেত্রে একেক রকম। ভেবে দেখেন, ভ্রূনের কিছু কোষ তার বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োজন হলেও পরে আর লাগেনা, সেই কোষগুলো নিজেরাই মরে যায়। যেমন, ভ্রূনের পাঁচ কিংবা ছয় সম্পতাহ বয়স পর্যন্ত তার হাত পায়ের চেহারা থাকে অনেকটা হাঁসের পায়ের মত। আঙ্গুলগুলোর মাঝখানে পর্দার মত থাকে। পরে এই পর্দার কোষগুলো আত্নহত্যা করে মরে গেলে সুন্দর আলাদা আঙ্গুল গুলো দেখা যায়। আবার কখনো কখনো কোষের ডিএনএ কোন কারণে এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে তা আর মেরামত করার যায়না, সেই অবস্থায়ও অ্যাপোটসিসের মাধ্যমে কোষটি মারা যায়।
সে যাই হোক, খুনে টি কোষ ভালোভাবে জানে কিভাবে কোষের আত্মহত্যা প্রবণতাকে উস়্কে দেয়া যায়। সে যখন বুঝতে পারে কোষের ভেতরে ক্ষতিকর কোন ভাইরাসের উপস্থিতি রয়েছে তখন সে কোষের দেয়ালে পারফোরিন নামের একটি প্রোটিন জড়ো করে। এর ফলে কোষের অ্যাপোটসিস প্রোগ্রাম চালু হয়, এবং সে মারা যায়।
টি কোষ অ্যাপোটসিস চালু করার আরেকটি উপায় জানে। তা হলো Fas লিগান্ড। সে যখন কোন কোষের Fas রিসেপ্টরে এই লিগান্ডটি ঢুকিয়ে দেয় তখনো অ্যাপোটসিসের মাধ্যমে কোষের মৃত্যু ঘটে।
খুনে টি কোষেরও আবার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সে তখনই কাজ করতে পারবে যখন আক্রান্ত কোষ তার ভেতরে বাড়তে থাকা ভাইরাসের প্রোটিনকে বাহিরে নিয়ে আসতে পারবে টি কোষের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য। এই প্রোটিন পার্টিকেলকে বাহিরে নিয়ে আসার কাজ করে MHC Class 1 Pathway। এই পদ্ধতি-তে কোষের প্রাচীরে MHC Class 1 প্রোটিন এবং ভাইরাসের প্রোটিন যুগপতভাবে প্রদর্শিত হয়। যদি কোষের ভেতরে এই পাথওয়েকে আটকে দেয়া যায় তখন কিন্তু খুনে টি কোষ কার্যত অন্ধ। কিছু কিছু ভাইরাস এই কাজটাই করে, তারা কোষের ভেতরে MHC Class 1 প্রোটিন তৈরিতে বাঁধা সৃষ্টি করে। তার ফলে ভেতরের খবর আর বাহিরে যায়না, স্বচ্ছন্দে চুপিসারে তাদের কাজ করে যেতে পারে। তাহলে উপায়?
এবারে আলোচনায় আসে Natural Killer Cell। এদের সংক্ষেপে NK কোষ বললেও বিজ্ঞানীরা চিনে থাকেন। প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হয়েছিলো NK কোষ ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কার্যকর। তবে পরে দেখা গেলো নির্দিষ্ট কিছু ভাইরাস দমনেও এরা দক্ষ। এদের স্ট্র্যাটেজিও খুনে টি কোষের মত, আক্রান্ত কোষের অ্যাপোটসিস উষকে দেয়া। কিন্তু কিভাবে করে সেটা নিয়ে অনেকদিন বিজ্ঞানীদের মাথা চুলকাতে হয়েছে। কেননা NK কোষে কোন রিসেপ্টর নেই যাতে করে সে ভাইরাসের কোন কিছুকে সনাক্ত করতে পারে। পরে দেখা গেলো তার পদ্ধতিটাও খুবই সাধারণ। সকল সুস্থ কোষের প্রাচীরেই MHC Class 1 প্রোটিন পাওয়া যায়। আক্রান্ত না হলেও নিজের ভেতরে প্রতিনিয়ত যেসব প্রোটিন তৈরি হচ্ছে সেসবের স্যাম্পল ধরে এনে বাইরে মেলে রাখে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে। ইমিউন সিস্টেম এই স্যাম্পলকে যাচাই করে প্রতিনিয়ত এবং দেখে সব ঠিক আছে কি না।
কোন ভাইরাস যখন MHC Class 1 তৈরিতে বাঁধা সৃষ্টি করে। কোষের প্রাচীরে যখন আর তাকে পাওয়া যায় না, NK কোষ আসলে এই অনুপস্থিতি থেকেই বুঝতে পারে কোষটিতে কোন সমস্যা আছে। অস্বাভাবিক কোষে তখন অ্যাপোটসিস ঘটে এবং মারা যায়।
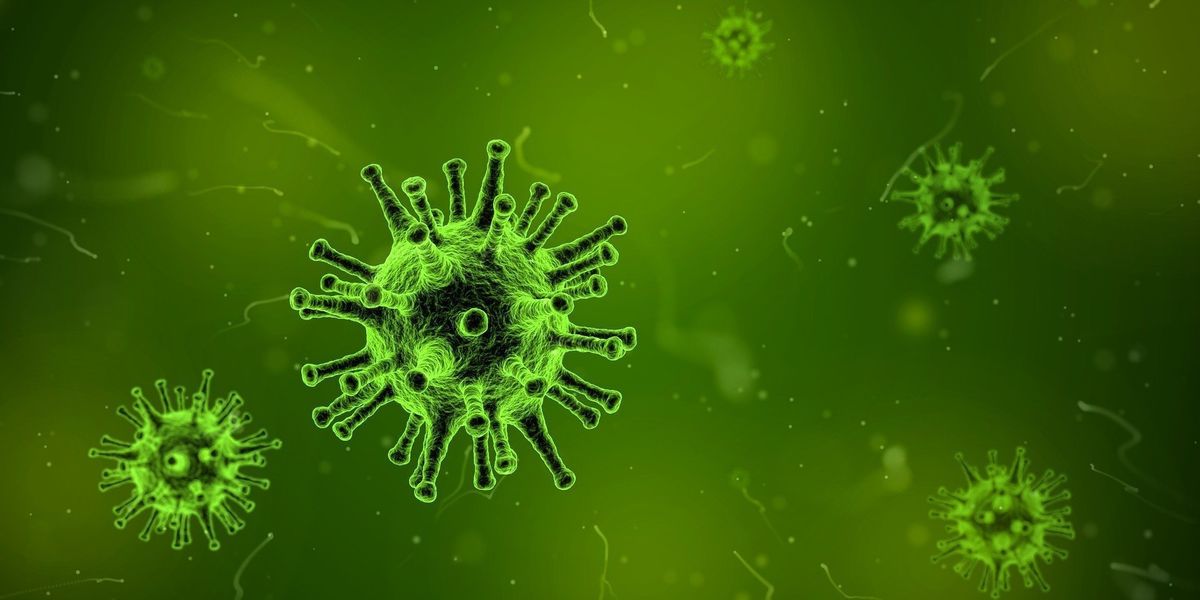
Leave a Reply