শেখার কোন বয়স নেই। হাতেখড়ির পর স্বরবর্ণ,ব্যঞ্জনবর্ণের পরিচয়ের মাধ্যমে যে পড়াশোনার পাঠ শুরু হয়, তার সমাপ্তি আদৌ নেই। প্রতিনিয়ত আমরা শিখে চলেছি। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, ক্রমান্বয়ে গতিশীল এই শেখার প্রক্রিয়া কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে? কে নিয়ন্ত্রণ করছে? দুটো প্রশ্নের উত্তর যে দিতে পারে সে হচ্ছে মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক হচ্ছে মানবদেহের আশ্চর্য অঙ্গ। রুপকথায় বর্ণিত আলাদীনের চেরাগের বাস্তব দৈত্য বলা যায়। এই মস্তিষ্ক তার বিস্তৃত কর্মকান্ড পরিচালনা করে নিউরণের মাধ্যমে। চেরাগের দৈত্যের হুকুম দেয় মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস। আমরা খালি চোখে আকাশে নক্ষত্ররাজি দেখে বিস্মিত হই। মস্তিষ্কে প্রাথমিক ভাবে প্রায় ৮৫ বিলিয়ন নিউরণ আছে – যা খালি চোখে যত নক্ষত্র দেখি তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায়। মস্তিষ্কের আজ্ঞাবহ ডাকপিয়ন হচ্ছে নিউরণ। সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিউরণ গুরু দায়িত্ব পালন করে থাকে দেহে। তড়িৎ বার্তা স্থানান্তর করে নিউরণ লিখা, চিন্তা, দেখা, লাফ দেয়া, হাঁটা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। একটি নিউরণ এক সাথে দশ হাজার অন্যান্য নিউরণের সাথে যুক্ত থেকে নতুন সংযোগ স্থাপন করে থাকে।

যখন আমরা শেখার প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করি, মস্তিষ্কে কর্মকান্ড পরিবর্তিত হতে থাকে। নিউরণগুলো আলোড়ন সৃষ্টি করে। নতুন সংযোগ স্থাপনে নিযুক্ত হয়। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় মস্তিষ্কের নমনীয়তা (neuroplasticity)। শেখার প্রক্রিয়া যতবার করা হয় অর্থাৎ অনুশীলন করা হয়, নিউরণের এই সংযোগ লাইন মজবুত হয়ে উঠে। ফলে, দ্রুত বার্তা স্থানান্তরিত হয়। ঠিক এইজন্যে, একেকজন একেক বিষয়ে তুখোড় হয়ে উঠে। কেউ পড়াশোনায়,কেউ খেলায়, কেউ সংগীতে বা অন্য যেকোন কিছুতে।
আরো ভেঙ্গে বলতে গেলে, ব্যাপারটা হচ্ছে একটা গহীন জঙ্গলে নতুন পথ তৈরী করে হেঁটে যাওয়া। হাইকিং করা যাকে বলে আর কি। প্রথম বার পথ খুঁজে পেতে সমস্যা হয়, হিজিবিজি লাগে লক্ষ্যে কিভাবে পৌঁছানো যায়। কিন্তু একবার পথ হয়ে গেলেই সে পথে চলাচল করা সহজ হয়ে উঠে। মাঝেমাঝে সোজা পথ পাল্টাতে হয়, এবড়োখেবড়ো রাস্তায় হাঁটা লাগে লক্ষ্যে যেতে। নতুন কিছু শিখতে হলে মস্তিষ্ক সেরকমভাবেই পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যেতে থাকে।
শেখার যেসব পদ্ধতি মস্তিষ্ক অনুসরণ করে থাকে
পদ্ধতি-১: পৌনঃপুনিক ভাবে নিউরণকে সক্রিয় করে তোলা। একদম প্রথম দিন থেকে কেউ সবজান্তা হয়ে উঠে না। শিশু যেমন আধো আধো বুলিতে শিখতে শুরু করে, মস্তিষ্ক ও ঠিক তাই। অসংখ্য নক্ষত্ররাজিসম নিউরণ ধীরে ধীরে জুড়ে গিয়ে পথ তৈরী করে থাকে।
হুট করে যদি জঙ্গলে হাইকিং করতে নামে যে কেউ,সে দিশেহারা হয়ে পড়বে। নতুন কিছুর প্রারম্ভে মস্তিষ্কের সেরকম দশা হয়, সময় নেয়, তারপর অভ্যস্ত হয়ে যায়। নিউরণের নতুন পথ তৈরীর সংগ্রামের সাথেই আমরা শিখতে থাকি। কখনোবা পুরোনা স্মৃতির তথ্য এসে জুড়ে গিয়ে আঠার মত কাজ করে। স্মৃতি মনে করা (recall of memory) শেখার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া।
পদ্ধতি-২: নিউরণের সক্রিয় হওয়ায় সময়ের মাঝে বিরতি দেয়া। আমরা শিখি, ভুলে যাই, আবার শিখি। এতক্ষণ জানলাম পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে মস্তিষ্ক শেখে। বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়ার মাঝে বিরতি এবং ঘুম শেখাকে অর্থবহ করে তোলে। ভুলে যাওয়ার সম্ভাব্যতাকে কমিয়ে আনে।
উদাহরণ দিয়ে বলা যাক, যদি আমরা টানা তিন ঘন্টা পড়াশোনা করি তবে ক্লান্ত হয়ে যাবো। এই পুরো সময় মনোযোগ যে একটানা দিতে পারব তার কোন গ্যারান্টি নেই। কিন্তু যদি তিন ধাপে এক ঘন্টা করে করে পড়াশোনা করি এবং প্রতি এক ঘন্টার পর বিশ মিনিট বিরতি নেই, তবে ক্লান্ত হবো না শেষে গিয়ে। আর মনোযোগ থাকবে আগের চেয়ে বেশি। এখানে মূলত যে ঘটনা হচ্ছে মস্তিষ্কে, তা হলো- এক ঘন্টা পড়ার পর যখন বিরতি নেই তখন নিউরণগুলো অবসর পায়। তারা নিজেদের সংযোগ লাইনে সমস্যা হলে তা মেরামত করে। শক্তি সঞ্চার করে থাকে এই সময়ে। এই ধরুন, ব্যাপারটা রিফুয়েলিং এর মত আর কি।
অন্যদিকে, আমরা যখন একটি কর্মব্যস্ত দিনের শেষে ঘুমাই, তখন সেটা মস্তিষ্কের জন্য উৎসবে রুপ নেয়। তারা বড় পরিসরে বিশ্রাম নেবার সুযোগ পায়, মেরামত তো চলতেই থাকে। নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠে পরবর্তী দিনের জন্য।
স্মৃতি যেভাবে শিখন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে
মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ স্মৃতি সংরক্ষণ করে। সবার চেয়ে অন্যতম হচ্ছে হিপ্পোকাম্পাস(hippocampus)। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, হিপ্পোকাম্পাস স্মৃতির বিভিন্ন অংশে সংযোগ স্থাপন করে থাকে। চলুন, উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করা যাক-
ধরুন, আপনি একটি ডিমওয়ালা মাছের একটি প্রজাতি নিয়ে জানতে চাইছেন। এটা জেনে হিপ্পোকাম্পাস প্রথমেই স্মৃতি হাতড়ে ‘মাছ’ এবং ‘ডিম’ এই দুটি শব্দ নিয়ে তথ্য হাজির করবে। তারপর এই দুটোকে জোড়া দিয়ে একটা সম্যক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবে, যা নিয়ে জানতে চাচ্ছেন।

আমরা প্রায়শ শুনি, মানুষের স্মৃতিবিভ্রম ঘটে। তার কারণ কিন্তু এই হিপ্পোকাম্পাস। মূলত, হিপ্পোকাম্পাস কাজ করা বন্ধ করে দিলে বা কোন কারণে অবশ হয়ে গেলে এই ঘটনা ঘটে থাকে। স্মৃতি ঠিকঠাক জমা থাকে মস্তিষ্কের অংশে কিন্তু তাদের জোড়া দেবার মাধ্যম থাকে না। আরেকটু ব্যাখ্যা করে বললে-
ধরুন, একটি বাসায় পাশাপাশি ঘরে দুই প্রতিবেশী থাকে। তারা একই রকমের চিন্তাধারা পোষণ করে। কেউ কাউকে চিনে না। পরিচয় হবার মত কোন উপলক্ষ্য না ঘটলে বা কেউ পরিচয় না করালে, তারা কিন্তু আজীবন অপরিচিতই থেকে যাবে। মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে স্মৃতি ও ঠিক তাই। হিপ্পোকাম্পাস পরিচায়ক হিসেবে কাজ করে স্মৃতির মধ্যে।
মস্তিষ্কের আরেকটি অংশ তথ্য মনে করতে ভূমিকা রাখে, যার নাম হচ্ছে মেডিয়াল প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স (medial prefrontal cortex)। তবে গবেষকরা মনে করেন, এর কাজ হিপ্পোকাম্পাসের থেকে আলাদা।
%27%20fill-opacity%3D%27.5%27%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23ff9d4f%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(166.97028%2012.55456%20-3.98355%2052.9795%20654.9%20490.3)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23a5a9ae%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(-102.2%20284.8%20-3)%20scale(126.04122%20262.38049)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22rotate(-132.8%20133%20249.4)%20scale(303.143%2085.86488)%22%2F%3E%3Cellipse%20fill%3D%22%23fff%22%20fill-opacity%3D%22.5%22%20rx%3D%221%22%20ry%3D%221%22%20transform%3D%22matrix(214.11835%20-192.76319%2059.28987%2065.85827%2033.7%2062.5)%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E)
চিত্রঃ- মস্তিষ্কের দুটি কার্যকরী অংশ।
মস্তিষ্ক যেভাবে ভুল সংশোধন করে
মানুষ জেনেশুনে বিপদে পড়ে কিন্তু জেনে বুঝে ভুল করে না। যদিওবা করে ফেলে, ভুল নজরে আসার পরে অনুশোচনায় ভুগতে থাকে। যেকোন উপায়ে ভুল সংশোধনের উপায় অন্বেষণ করতে থাকে।আমরা যেকোন কাজ করার প্রথমে একটা উপায় বা পথ ভেবে থাকি। সে মোতাবেক কাজ করতে শুরু করি। হুট করে ভুল করে ফেললে, যখন বুঝতে পারি তা ঠিক করার জন্য চিন্তা করি।আমরা ঘুমিয়ে গেলেও মস্তিষ্ক কখনো অলস থাকে না। সে তার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে। ঘুমিয়ে থাকার সময় তড়িৎ অনুভূতির মাধ্যমে মস্তিষ্ক নিউরণের মাধ্যমে যোগাযোগ অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করে যায়। আমাদের সকল কাজ এক বিশেষ ধরনের ইলেক্ট্রোড সেন্সর বা তড়িৎ অনুভবের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়ে যায় মস্তিষ্কে, যে প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্রাফি(electroencephalography- EEG)। এই প্রক্রিয়াকে তড়িৎ অনুভূতির ঢেউ হিসেবে আখ্যায়িত করে গ্রাফ করলে সহজে পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয়। এই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার জন্য, গবেষকরা কিছু স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে যাচাই করেন। এম আর আই (MRI) করে তড়িৎ অনুভূতি দেখে গ্রাফ চিত্রে রুপ দেন। আচ্ছা,উদাহরণ দিয়ে ঘটনা বলা যাক-
ধরুন, আপনাকে কীবোর্ডের Z বোতাম চাপতে বলা হলো হুট করে। আপনি যদি ঠিকঠাক বোতাম চাপেন তবে তড়িৎ ঢেউ গ্রাফে যেমন হবার কথা তেমনি হবে। আর যদি আপনি ভুলে F বোতাম চাপ দেন তখন কী হবে? সাথে সাথে এই ভুল মস্তিষ্কের মাস্টারমশাই ধরে ফেলবেন। তড়িৎ গতিতে একটি নেগেটিভ সংকেত পাঠিয়ে বার্তা পাঠাবে, আপনি ভুল করেছেন। এ প্রক্রিয়াকে বলে ভুল-সম্বন্ধীয় নেগেটিভ তত্ত্ব (error-related negativity -ERN )। এই নেগেটিভ সংকেত পাঠায় মস্তিষ্কের প্রথম ভাগের গভীর অংশ থেকে- যা সিংগুলেট কর্টেক্স (cingulate cortex) নামে পরিচিত। মস্তিষ্কের এই অংশ সেন্সর হিসেবে কাজ করে। ভুল দেখা মাত্রই বার্তা পাঠিয়ে দেয় মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশে একটি সংযোগ লাইনের মাধ্যমে – যা সিংগুলাম বান্ডেল (cingulum bundle) নামে পরিচিত। এই সংযোগ লাইন ব্যক্তির মনোযোগকে আকৃষ্ট করে এবং ভুল করার প্রবণতা কমিয়ে দেয়। এই তড়িৎ সংকেত এত দ্রুত পৌঁছে যায় যা কল্পনাধীন। মাত্র ১০০ মিলি সেকেন্ডের মধ্যে সংকেত চলে যায় ভুল করার পর এবং পরবর্তী ২০০ মিলি সেকেন্ড বা তার মধ্যে ব্যক্তি অনুভূতি-শুন্য হয়ে যায়। সতর্ক করে দেয় ব্যক্তিকে ভুল সম্পর্কে। এই প্রক্রিয়াকে ভুল-সম্বন্ধীয় পজিটিভিটি( error positivity) নামে পরিচিত।


ভুল যেভাবে ব্যক্তির ব্যবহার এবং শিখন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে
গবেষণায় দেখা গেছে যে, একটা ভুল করার পর আমরা ধীর গতিতে সাড়া দেই পরবর্তী পদক্ষেপে। এর কারণ হচ্ছে, মস্তিষ্ক চায় না একই ভুল বারবার হোক। যত দ্রুত ভুল-সম্বন্ধীয় নেগেটিভিটি সক্রিয় হয়, তত ধীরে পরবর্তী পদক্ষেপ পরিচালিত হয়। কিছু মানুষের ভুলের অনুশোচনা তীব্র আকারে হয়। কিছু মানুষের কম, আবার কারো হয়-ই না। যাদের ভুলের অনুশোচনা বেশি, তারা ভুল সংশোধনে বেশি আগ্রহী। তাইতো গবেষণায় দেখা গেছে, বিদ্যালয় কিংবা বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্যায়ে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী অনুশোচনায় বেশি ভোগে, তারা দারুন ফলাফল করছে একাডেমিক পড়াশোনায় বা যে কোন কাজে।
সামাজিকভাবে মস্তিষ্কের শিক্ষালাভ
মানুষ সামাজিক প্রাণী। সমাজের বিদ্যমান পরিবেশ এবং মানুষের আচরণ দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই। ব্যক্তির মস্তিষ্ক সমাজের মানুষ থেকে, তাদের আচরণ থেকে শিক্ষালাভ করে থাকে।
উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বলা যাক- ধরুন, আপনি কারো প্রেমে পড়েছেন অথবা প্রেমে ব্যর্থ হয়েছেন। কেউ জানে না সেসব অনুভূতির কথা। কাউকে বলেনওনি। একদিন ভাবলেন, কাছের বন্ধুকে শেয়ার করবেন। তাকে জানালেন সব ইতিবৃত্ত। আপনার বিশ্বাস ছিল, সে কাউকে জানাবে না। কিন্তু বিপরীত ঘটনা ঘটলো। জেনে গেলেন, আপনার ঘনিষ্ঠ সে বন্ধু সম্প্রচার করে দিয়েছে সকল মহলে এবং তুমুল ঠাট্টায় মেতেছে আপনাকে নিয়ে। এই ঘটনা থেকে আপনি একটা শিক্ষা পেলেন। তার আচরণ আপনার মস্তিষ্কে শক্তভাবে বার্তা দিল যে, গোপন কথা যে কাউকেই বলা ঠিক না।
আবার ধরুন, পরীক্ষার হলে আপনি একটা প্রশ্নের উত্তর পারছেন না। চেষ্টা করছেন পাশের বন্ধু থেকে দেখে সেটা লিখার। ঠিক তখনি দেখলেন, হলে শিক্ষক অন্য একজনকে একই কাজ করার জন্য উত্তরপত্র নিয়ে গেছে এবং অপমান করেছে দেখাদেখির জন্য। আপনি কি আর সাহস করবেন? অবশ্যই না। ঘাবড়ে যাবেন তৎক্ষণাৎ। মস্তিষ্ক বার্তা পাঠিয়ে আপনাকে সতর্ক করে দেবে, এটা কখনোই ঠিক হবে না করা।
এবার আসল কথায় আসা যাক, উপরোক্ত দুটো ঘটনা ঘটার সময় এবং আগে-পরে মস্তিষ্ক কিন্তু সজাগ ছিল। সার্বক্ষণিক হিসাব কষতে ব্যস্ত ছিল। অনুমান সঠিক ভাবে কাজ যেমন করতে পারে তেমনি ভুল ও প্রতীয়মান হতে পারে। এটাকে বলে অনুমান-নির্ভর ভুল(predictions error)। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে পেয়েছেন যে, মস্তিষ্কের দুটো অংশ সামাজিক শিক্ষা গ্রহণে ভূমিকা রাখে। একটির নাম ভেন্ট্রাল স্ট্রেইটাম (ventral straitum), অন্যটি হচ্ছে মেডিয়াল প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স(medial pre-frontal cortex)।
- ভেন্ট্রাল স্ট্রেইটাম হচ্ছে মধ্য-মস্তিষ্কের অংশ। যা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে- ব্যক্তির আনন্দ অনুভূতির সময়কে, উপভোগের সময়ক। এছাড়াও এই অংশ ব্যক্তির অনুমান প্রক্রিয়ায়ও ভূমিকা রাখে।
- মেডিয়াল প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স হচ্ছে মস্তিষ্কের সামনের অংশ( কপালের পিছনে)। যা প্রধানত চিন্তা প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে। অন্যের আচরণ দেখে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে এবং নতুন কিছু শিখতে ভূমিকা রাখে।
এই দুটো অংশ মিলেমিশে মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে থাকে। সামাজিক শিক্ষা লাভে মস্তিষ্ককে আগ্রহী করে তোলে।
তথ্যসূত্র –
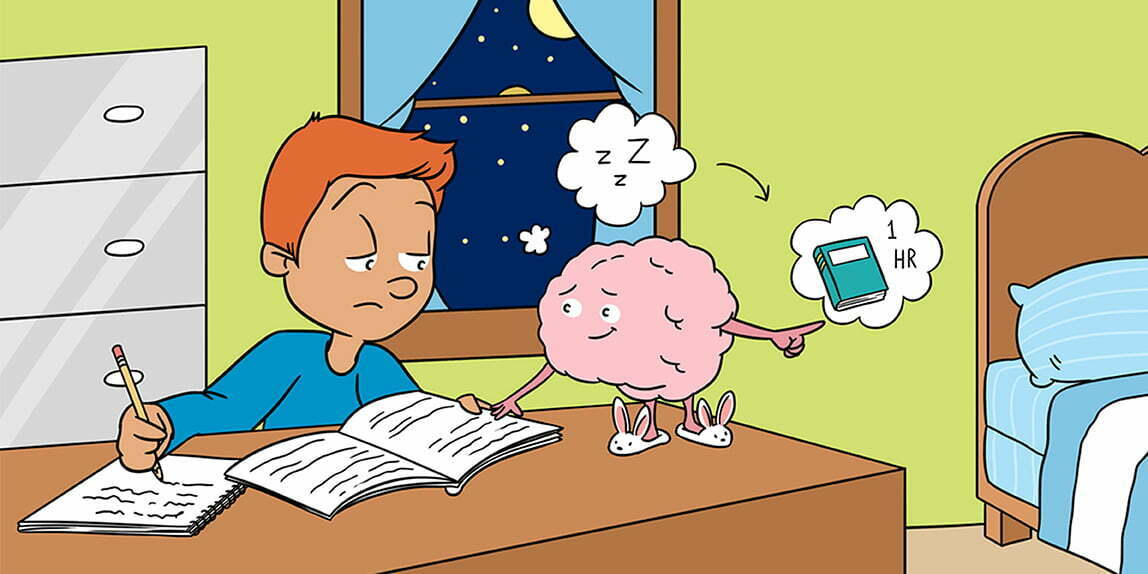

Leave a Reply