কোষ ও টিস্যু নিয়ে প্রাথমিক বিষয়গুলো জানা যাবে এবং যেগুলোর বিস্তৃতি উপলব্ধি করতে পারবো, এমন কোনো বই বাংলা ভাষায় দেখতে না পারায় বেশ আফসোস হচ্ছিল। বিচিত্র কোষজগৎ সম্পর্কে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা কি বেসিক জিনিসগুলো উপলব্ধির সাথে জানতে পারবে না? এই আফসোস দূর করে দিয়ে ২০২২ সালের বইমেলায় চলে আসে সৌমিত্র চক্রবর্তী স্যারের লেখা “জীবকোষ তা নয় যা তুমি ভাবছো”। আর এই বইটাই আমি বিজ্ঞান ব্লগ থেকে গিফট পেলাম। পড়ে তো অবাক! চলুন, সেই গল্পই জানা যাক।
বইয়ের ভেতরে
“জীবকোষ তা নয় যা তুমি ভাবছো”-বইটিতে বেশ কয়েকটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম দুই অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে কোষ আসলে কী জিনিস। অনেক জটিল সংজ্ঞা ও স্বীকার্যকে লেখক একদমই সহজ ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই দু’টি অধ্যায় পড়ে যেকোনো পাঠক কোষতত্ত্বের মূলনীতি এবং কোষের প্রাথমিক রূপ সম্পর্কে জানতে পারবে।
তৃ্তীয় অধ্যায়ে কোষ পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। কোষকে দেখার আগে নির্দিষ্ট অংশকে স্টেইনিং এর মাধ্যমে প্রস্তুত করে নেওয়া হয়, এরপর পর্যবেক্ষণ করা হয়। স্টেইনিং কী সেটা জানতে হলে আপনাকে চলে যেতে হবে বইয়ের ৩৬ নং পৃষ্ঠায়। এই অধ্যায়ে আরও বলা হয়েছে যে একটি জীবিত কোষ কখনো স্থির থাকে না।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরণের কোষীয় অঙ্গাণু (কোষগহ্বর, রাইবোজোম, প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়ন ইত্যাদি) সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ খুঁজে পাবেন। এছাড়াও বিভিন্ন বস্তুর পরিবহন, ভেদবার্গ একক এবং অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। কোষাভ্যন্তরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে এই তিনটি অধ্যায় বিশেষ ভাবে সাহায্য করবে বলে আমি মনে করি।
সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে নিউক্লিয়াস, জেনেটিক কোড, সেন্ট্রাল ডগমা অফ মলিক্যুলার বায়োলজি, মিউটেশন ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ ও সহজ কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনাগুলো বেশ প্রাণবন্ত ছিল। নবম অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদটিস্যু ও প্রাণীটিস্যু নিয়ে সহজ ভাষায় লেখা খুঁজে পাবেন। এখানকার কথাগুলো প্রাথমিক পর্যায়ের হলেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বশেষ অধ্যায়টিতে কোষ বিভাজন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টা বেশ তথ্যবহুল ও চমৎকার।
তো, বইটিতে মূলত এসকম বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।
ম্যাগনেটিক পয়েন্ট

বইটিতে ভিন্নধর্মী কিছু আলোচনা ও লাইন চোখে পড়েছে, যেগুলো পাঠকদের সামনে জীববিজ্ঞানকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। এমনই কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করছি-
১. গাড়ি চালানোর তেল বা চুলা জ্বালানোর গ্যাসের ব্যবহার আসলে লক্ষ কোটি বছর আগে সূর্যালোক হতে যে শক্তি জীবদেহের অণুগুলোর মধ্যকার রাসায়নিক বন্ধনশক্তি হিসেবে আটকা পড়েছিল সেই অণুগুলো ভেঙে শক্তি নির্গত করার প্রক্রিয়া। (পৃষ্ঠা-৮২)
২. মাকড়সা যেমন জালের কেন্দ্রে বসে জালকের প্রতিটি সুতার কম্পন নির্ণয় করে সেই অনুসারে ব্যবস্থা নেয়, সেন্ট্রোজোম তেমনি মাইক্রোটিউবিউলের গঠন ও নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র। (পৃষ্ঠা-৬৭)
৩. মুদ্রা বা কারেন্সির যেরকম মাধ্যম, পরিমাপ, মান ও সঞ্চয়-এই চারটি নীতি রয়েছে, এটিপিরও তেমনি ঐ নীতিগুলো রয়েছে। তাই এটিপিকে “শক্তির টাকা” বলা যায়। (পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪)
৪. DNA ও RNA এর ভাষা বেশ কাছাকাছি, অনেকটা বাংলা ও অহমিয়ার (ভারতের আসাম রাজ্যের বেশিরভাগ মানুষের ভাষা) মতো। (পৃষ্ঠা-১২৫)
জানতে পারলাম
“জীবকোষ তা নয় যা তুমি ভাবছো” বইটি পড়ে বেশ কিছু বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরেছি। যেমনঃ
১. মাইটোকন্ড্রিয়ন এবং প্লাস্টিড আসলে ব্যাকটেরিয়ার মতোই জীব ছিল, যারা এন্ডোসিমবায়োসিসের মাধ্যমে কোষে অঙ্গাণু হিসেবে জায়গা দখল করে নিয়েছে।
২. একটা কোষের অঙ্গাণুগুলো কখনোই স্থির থাকে না। কোষের মাঝে ভাঙাগড়ার কাজ চলতেই থাকে।
৩. মিয়োসিসের অভিব্যক্তিক গুরুত্ব ব্যাপক, যা জীবজগৎকে টিকিয়ে রেখেছে।
৪. পলিপ্লয়েডি কী, এটা কয় প্রকারের হয়-ইত্যাদি।
মতামত ও সমালোচনা
বইটি শিক্ষার্থীদের জন্যই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি এটা পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। এছাড়াও যাআ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে কিস্তিমাত করতে চায়, তারাও এই বইটা পড়ে উপকৃত হবে। আর সাধারণ জীববিজ্ঞানপ্রেমী পাঠকদের জ্ঞানের খোরাকও মেটাতে সক্ষম এই বইটি।
সত্যি কথা বলতে এই বইটা জীবকোষ নিয়ে আমাদের ধারণা বদলে দিতে পারে। আমরা বই-পুস্তকে কোষ বা টিস্যুর যেরকম ছবি দেখি, বাস্তবে কোষ-টিস্যু মোটেও ঐরকম নয়। বইটা পড়ে এই বিষয়টাই উপলব্ধি করতে পেরেছি। জীববিজ্ঞানের বেশ কিছু বিষয়ে ধ্যান-ধারণা বদলে দিবে এই বইটি।

তবে কিছু অসঙ্গতিও চোখে পড়েছে। আর কিছু জিনিসের পরিবর্তন করলে বইটা আরও চমৎকার হবে বলে আমি মনে করি। যেমনঃ
১. ৩৪ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, “…এসব অভ্যন্তরীণ লেন্সের কারণে যেহেতু কিছুটা বিবর্ধন (125x) হয়েই যায়, তাই মোট বিবর্ধন হিসাব করার সময় টিউব ফ্যাক্টর হিসেবে সেটিও যোগ করা হয়।“ আমার যতদূর মনে হয়, এখানে 125x হবে না, বরং 1.25x হবে।
২. ৯৯ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, “অনেক সময়ই অভিব্যক্তির ফলগুলো লাগসই ডিজাইন, সর্বোত্তম ডিজাইন নয়।“ আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে এই কথায় খটকা লেগেছে। কারণ জৈব অভিব্যক্তির ফলে জীব প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য বা স্ট্রাকচার লাভ করে। সেটা কি তার জন্য সর্বোত্তম নয়? (হয়ত লেখক অন্য কিছু বুঝাতে চেয়েছেন।)
৩. বইয়ের শেষে যেই রঙিন ছবিগুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলো সংশ্লিষ্ট আলোচনার মাঝে সংযুক্ত করলে পাঠকদের বিশেষ সুবিধা হতো এবং লেখনীগুলো আরও জীবন্ত হয়ে উঠতো।
৪. বইয়ের শিরোনামটা আরও সংক্ষিপ্ত এবং চমকপ্রদ করা যেতো।
তবে সবশেষে বলব, জীববিজ্ঞানপ্রেমী পাঠক হিসেবে আপনার এই বইটি পড়া উচিত। পড়ুন, জানুন এবং এই ব্লগ পোস্টটি শেয়ার করে অন্যদেরও বইটির ব্যাপারে জানান। Happy reading!
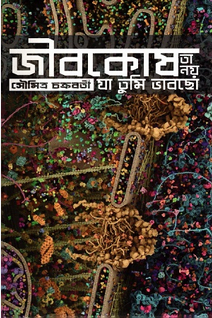
Leave a Reply