ঘুম, যে কাজে আমরা জীবনের এক-তৃতীয়াংশ সময় ব্যয় করি, বেঁচে থাকার জন্য তার অতীবগুরুত্ব ভূমিকা থাকতেই হবে। না হয় সে কাজ বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে বোধগম্য না।
ঘুমের অনেকগুলো জরুরী কাজের মধ্যে সম্ভবত অন্যতম প্রধান হলো স্মৃতি সংহতিসাধন (Memory consolidation)। নিউরোসায়েন্সের ভাষায় মেমরি কনসলিডেশন বলতে বোঝায় নতুন গঠিত হওয়া স্মৃতিকে দৃঢ়করণ, স্থিতিশীলতা বাড়ানো, ও স্বল্পমেয়াদী স্মৃতি থেকে দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতিতে স্থানান্তর।
মস্তিস্কে স্মৃতির সংহতিসাধন ঠিক কিভাবে হয়?
ইনসাইডার হলো বিজ্ঞান ব্লগের একটি সদস্য প্রোগ্রাম। বিজ্ঞান ব্লগে প্রতি মাসে মোট চারটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে। এগুলো লিখছেন আরাফাত রহমান ও সুজয় কুমার দাশ। এই লেখাগুলো কেবল মাত্র লগইন করে পড়া যাবে। আপনি যদি বিজ্ঞান ব্লগের ইনসাইডার হতে চান, তাহলে এককালীন ৫০০/= টাকা বিকাশ করার মাধ্যমে একাউন্ট তৈরি করতে পারেন। সদস্য হওয়ার জন্য ই-মেইল করুন। উল্লেখ্য, টাকা পেমেন্ট মাত্র একবারই করতে হবে, অর্থাৎ লাইফ-টাইম একসেস। পেমেন্টের প্রথম এক মাসের মধ্যে সদস্যতা বাতিল করা যাবে।
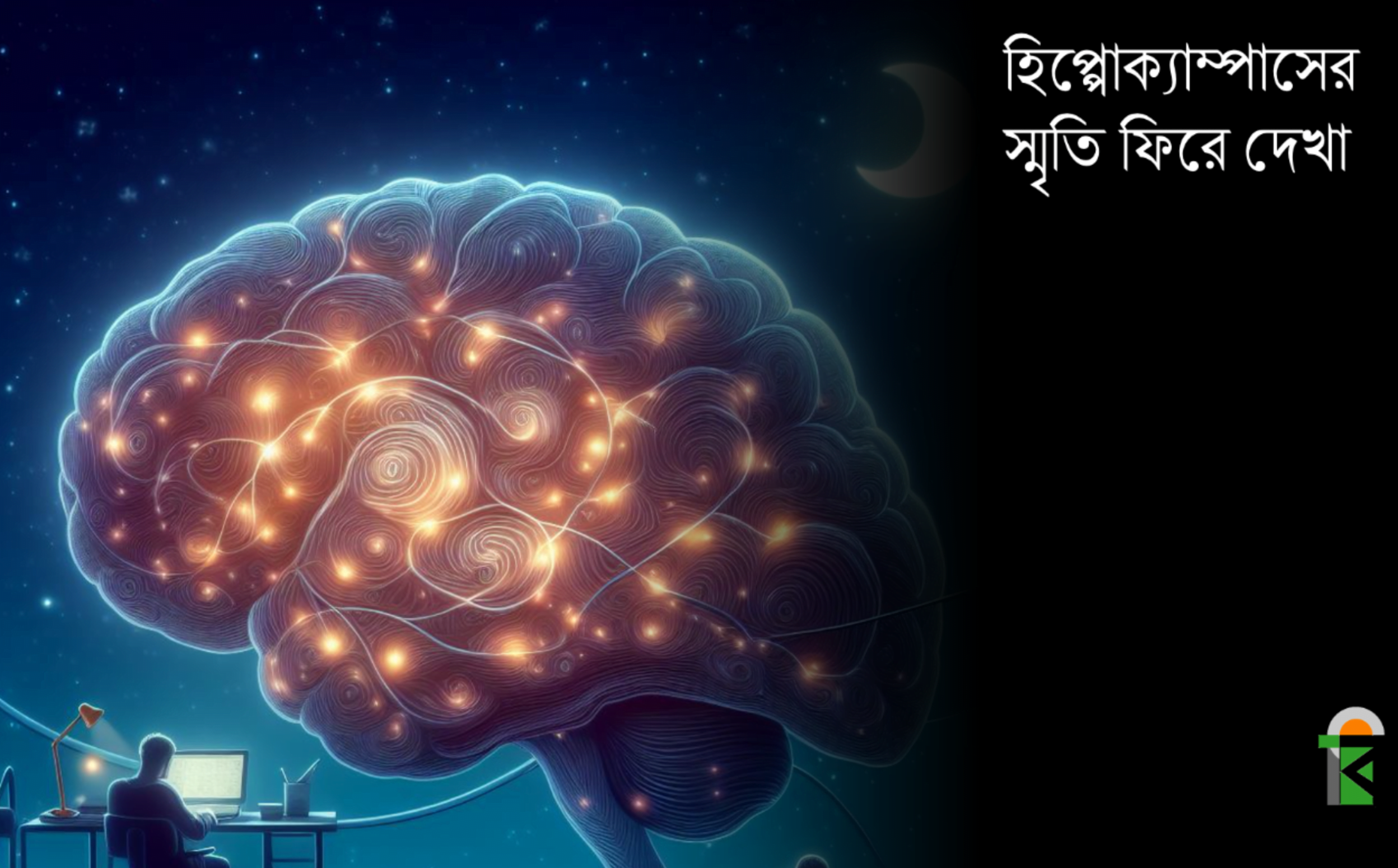
Leave a Reply