আধুনিক বিবর্তন তত্ত্বের অন্যতম এক ভিত্তি হচ্ছে মিউটেশন। একটা প্রজাতির উদ্ভব ন্যাচারাল সিলেকশানেই হোক, জেনেটিক ড্রিফটে হোক কিংবা জিন প্রবাহের মাধ্যমেই হোক—জেনেটিক ভ্যারিয়েশন ঘটার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে মিউটেশন। অর্থাৎ, বিবর্তনের মূল চালিকাশক্তিই হচ্ছে মিউটেশন। চার্লস ডারউইন যখন বিবর্তন তত্ত্ব প্রস্তাব করেন, তখন পৃথিবীবাসীর এমনকী, তাঁর নিজেরও ক্রোমোজোম, ডিএনএ, জিন ইত্যাদি নিয়ে কোনো ধারণা ছিলো না। ডারউইন বিবর্তনকে দেখেছিলেন ব্যক্তিগত প্রাণী বা উদ্ভিদ এবং প্রজাতি লেভেলে। কিন্তু, আধুনিক জিনতত্ত্বের উন্নতির সাথে সাথে আমরা বুঝতে পেরেছি যে বিবর্তন ঘটছে জিন, বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এবং পপুলেশনে।
মিউটেশনের পরিচয়, প্রকারভেদ ও আদ্যোপান্ত
একজন ছাপোষা লেখক হিসেবে আমি মোটেও আপনাদের ছোট করে দেখছি না। তাও, মিউটেশনের এই খটমটে আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আপনাদের আবারও মনে করিয়ে দিই ক্রোমোজোম, ডিএনএ(DNA) এবং জিন(Gene) কী জিনিস। কারণ, এ লেখাটিতে আপনি এত্তোবার এ শব্দগুলো পাবেন, সংজ্ঞা ভুলে গেলে রেগেমেগে পড়া বাদ দিয়ে বেড়িয়ে যেতে পারেন। যারা একাডেমিক বা নার্ডি গোছের আলোচনা পছন্দ করেন, তাঁরা আমার এসব অতি সরলীকৃত, সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা পছন্দ না-ও করতে পারেন। তাঁদের কাছে অগ্রীম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।
ক্রোমোজোম কী?
ক্রোমোজোমকে আমি বলবো একটা প্যাকেজ। তার কাজ হচ্ছে আমাদের বংশগতীয় যাবতীয় সব কাজ-টাজ সামলানো। কোষের কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস। সেই নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকে সুতার মতো এই বস্তু। ক্রোমোজোম তার নিজের ভেতর আমাদের বাপ-দাদা চৌদ্দ গোষ্ঠীর জেনেটিক রেকর্ড, আমাদের বৈশিষ্ট্য, আমাদের যাবতীয় তথ্য ধারণ করে রাখে ডিএনএ নামক এক বিশেষ অণুর মাধ্যমে। প্রতিটি কোষে কতোগুলো ক্রোমোজোম থাকবে, তা নির্ভর করে প্রজাতির ওপর। অর্থাৎ, একেক জীবে একেক সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। যেমন আমাদের ৪৬ টি (২৩ জোড়া), আমাদের চাচাতো ভাই গরিলাদের ৪৮ টি (২৪ জোড়া)। ক্রোমোজোমের অর্ধেক আসে বাবা থেকে, বাকি অর্ধেক মায়ের থেকে।

ডিএনএ কী?
আপনাকে হতাশ করে দিয়ে শুরুতেই এর পূর্ণরূপ বলি, ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড (Deoxyribonucleic acid)। আমাদের কোষের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে থাকা একটা অণু। প্রায় সব জীবকোষেই পাবেন। জীবের দেহের গঠন কেমন হবে, কোষগুলোর বিভিন্ন অঙ্গাণু কীভাবে তৈরি হবে, কতখানি করে তৈরি হবে, কোন কারণে ভেঙে গেলে মেরামত কী করে করতে হবে, ইত্যাদি হাজাররকম তথ্য এই ডিএনএর মধ্যে চারটা অক্ষর দিয়ে লেখা থাকে। সেই চারটা অক্ষর হচ্ছে, এডিনিন (A), সাইটোসিন (C), গুয়ানিন (G), এবং থাইমিন (T) নামে চারটা নাইট্রোজেন ক্ষার। এই ডিএনএ-র ভেতর আবার থাকে জিন। সেটা পরে বুঝাচ্ছি। এই ডিএনএ-কে আমরা বলি জীবন রহস্য বা নীলনকশা।
জিন কী?
সহজ করে বললে, জিন হচ্ছে আমাদের শরীরের সবকিছু তৈরির নকশা। যেকোন জীবকোষের বেঁচে থাকার জন্য অসংখ্য রকম যন্ত্রের দরকার হয়- শক্তি উৎপাদনের যন্ত্র, অক্সিজেন পরিবহণের যন্ত্র, জিনিসপত্র চলাচলের যন্ত্র। আপনার দেহের কোটি কোটি কোষ তাদের অসংখ্য যন্ত্র দিয়ে সবসময় কাজ করছে বলেই আপনি এখন এত সুন্দর বেঁচেবর্তে আছেন। তো এরকম একেকটা যন্ত্র তৈরির নির্দেশনা একেক টুকরো ডিএনএতে লেখা থাকে চারটা অক্ষর দিয়ে। এই ডিএনএ টুকরোগুলোই জিন। এই জিনে নাইট্রোজেন ক্ষারগুলি একেকটা একেক সজ্জায় থেকে একেকটা তথ্য ধারণ করে। জিন থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে সৃষ্টি হয় আমাদের দেহে প্রোটিন। প্রোটিন তৈরি হয় তিন-বেসের কোডন অনুযায়ী। সে প্রোটিনগুলিই আমাদের দেহের নানান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। যেমন ধরুন, আপনার চোখের রঙ। সেটার জন্যেও আপনার ডিএনএ তে কোথাও না কোথাও, কোনো লোকেশানে আলাদা নাইট্রোজেন বেইস এর কম্বিনেশন আছে। সেই ইউনিক কম্বিনেশনকে ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করে চোখের জন্য তৈরি হওয়া প্রোটিনটিই আপনার চোখের রঙ প্রকাশ করেছে। এভাবে আপনার প্রকাশিত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে জিন। গায়ের রঙ কেমন হবে, বড় হয়ে চুরি বাটপারির প্রবণতা থাকবে কিনা, কতোটা লম্বা হবেন, দেখতে কেমন হবেন—সবকিছু কেবল চারটা অক্ষরে বিভিন্ন ভাবে সাজানো থাকে। জিনকে আপনি ব্লুপ্রিন্ট বা নীলনকশা ভাবতে পারেন।
মিউটেশন কী?
আপনারা আগে থেকেই এটুকুও হয়তো জানেন যে, আমাদের ডিএনএর মধ্যে নানা কারণে পরিবর্তন হয়। পরিবর্তন কথাটার একটু রাশভারী অনুবাদ হল মিউটেশন। বাংলায় আবার এটাকে কেউ কেউ বলেন পরিব্যক্তি বা পরিবর্তন। আবার বইয়ের ভাষায় বলতে গেলে বলবো মিউটেশন মানে হচ্ছে জীবের বংশগতীয় বস্তুতে আকস্মিক পরিবর্তন। আরও ঘুরিয়ে বললে, মিউটেশন হচ্ছে জিন অনুক্রমে পরিবর্তন। যেহেতু আমাদের জিনেই নাইট্রোজেন ক্ষারগুলো নানান সজ্জায় সজ্জিত থেকে আমাদের নানান রকম তথ্য ধরে রাখে, সে তথ্যের পরিবর্তন ঘটালে জীব দেহেও এর বড়সড় পরিবর্তন চলে আসে।
কথার কথা, ধরুন THE CAT RAN FAR টাইপের জিন সিকোয়েন্সের জন্য কোনো প্রাণীর ২ টা ডানা হয়। এবার ধরুন সে জিনোম সিকোয়েন্সে কোনোভাবে এই অক্ষরগুলির সিকোয়েন্স উলটাপালটা হয়ে লিখা হয়ে গেলো THE TAC RAN FAR । সেক্ষেত্রে আর অর্থ কি একই থাকলো? THE CAT RAN FAR এর জন্য সে প্রাণিতে যে ধরণের প্রোটিন সৃষ্টি হতো, THE TAC RAN FAR এর জন্য অন্য ধরণের পরিবর্তন আসবে। হয়তো আকার পালটে যাবে কিংবা হয়তো আরও একটা বাড়তি ডানা যোগ হবে। মিউটেশন ব্যাপারটাও আসলে এভাবেই ঘটে। তবে কিছু নিয়মের ভেতরেই, কিছু কারণেই মিউটেশন ঘটে। কীভাবে ঘটে, কেন ঘটে তা জানতে ক্রোমোজোম আর তার ভেতরের ডিএনএ-তে প্রবেশ করবো আমরা। এবার আমরা ঢুকবো গম্ভীর আর গভীর আলোচনায়। চলুন দেখি কীভাবে এই মিউটেশন ব্যাপারটা বিবর্তনের কারণ হয়; কীভাবেই বা এটা মাংশাসী ডায়নোসোরকে মুরগীতে রূপান্তরিত করে, শেয়ালের মতো দেখতে প্রাণী হয়ে যায় তিমি—সৃষ্টি হয় বিচিত্র্য সব প্রাণের স্পন্দন।
এর আগে সংক্ষেপে মিউটেশনের ইতিহাসটা জেনে নেয়া যাক। চার্লস ডারউইন বিবর্তন তত্ত্ব প্রস্তাব করার সময় তিনি সঠিক কোনো ব্যখ্যা দিতে পারেন নি, কীভাবে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলো জীবে আসে। এ নিয়ে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ব্যখ্যা হাজির করেন অগাস্ট ভাইজম্যান, ম্যান্ডেলিফের জিনতত্ত্ব নিয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কারের পর। ১৮৮০ সালে অগাস্ট ভাইজম্যান তাঁর জার্মপ্লাজম-সোমাটোপ্লাজম তত্ত্বে (Germplasm-Somatoplasm) উল্লেখ করেন যে, জীবের জননাঙ্গে অবস্থিত জননকোষে থাকে জার্মপ্লাজম, আর দেহের অবশিষ্ট কোষে থাকে সোমাটোপ্লাজম। তিনি বলেন, সোমাটিক সেল বা দেহকোষ প্রজননে কোনো ভূমিকা রাখে না। শুধুমাত্র জার্ম সেল বা গ্যামেট ভূমিকা রাখে। তিনি এই জার্মপ্লাজমের এ ধারণাকে কে সংযুক্ত করেন চার্লস ডারউইনের প্রস্তাবিত বিবর্তনের সাথে। তিনি বললেন, প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটে মূলত জীবের জার্মপ্লাজম স্তরে। তার এই নতুন অনুকল্প দ্বারা মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিটেন্সের নতুন নতুন দ্বার খুলে গেল। এর মাধ্যমে মেন্ডেল আর ডারউইন—উভয়ের গবেষণাকে অনেকটা এক সূত্রে গেঁথে দেয়া হলো। জীবের প্রজননের সময় জনন কোষে ঘটা মিউটেশনের কারণেই প্রকরণের(variation) উদ্ভব ঘটে। কোনো প্রজাতিতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে নানাবিদ প্রকরণের ফলে উদ্ভব ঘটে নতুন প্রজাতির। এর ফলে সৃষ্টি হয় নতুন প্রজাতির।
কথা হচ্ছে, সব মিউটেশন জীবের মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করে না। নতুন বৈশিষ্ট্য তখনই জীবের মধ্যে যুক্ত হয় যখন মিউটেশন জার্মলাইন কোষে (যেমন ডিম্বাণু বা শুক্রাণু) ঘটে এবং প্রজননের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মে সেই পরিবর্তন চলে যায়। অন্যদিকে, যদি মিউটেশন সোম্যাটিক কোষে (যেমন ত্বক বা যেকোনো শরীরের কোষ) ঘটে, তবে সেটি সেই জীবের শরীরে পরিবর্তন আনতে পারে, কিন্তু তা উত্তরাধিকার সূত্রে যায় না। একই সাথে বলে রাখা ভালো যে, সব মিউটেশন উপকারী না। ধরুন, মিউটেশনের ফলে কোনো জীবে একটি বৈশিষ্ট্য যোগ হলো, যার ফলে সে সেই পরিবেশে টিকে থাকার মতো সুবিধা পাচ্ছে, তাহলে সে মিউটেশনকে আমরা উপকারী মিউটেশন বলতে পারি। এই আর্টিকেলের পরবর্তী অংশে মেরু অঞ্চলের ভাল্লুকদের উদাহরণ দিয়েছি। এবার প্রশ্ন আসছে যে মিউটেশন কীভাবেই বা ঘটে? কতো প্রকার?
মোটাদাগে মিউটেশন ২ প্রকারঃ
(১) ক্রোমোজোমাল মিউটেশন ও
(২) জিন মিউটেশন।
এই দুই প্রকার মিউটেশনেই জিন সিকোয়েন্সে পরবর্তন ঘটে। একটু করে জেনে নিই এ দুটো আসলে মিউটেশন কী, কীভাবে ঘটে আর কেন ঘটতে পারে।
১. ক্রোমোজোমাল মিউটেশনঃ আমারা আগেই জেনেছি ক্রোমোজম হচ্ছে আমাদের কোষে থাকা এমন এক ফিতা যা আমাদের সকল তথ্য ধরে রাখে। কারণ, ক্রোমোজোম ধারণ করে ডিএনএ, আর ডিএন-তে থাকে জিন। এই জিন যেভাবে যে সিকোয়েন্সে আছে, তা পাল্টে গেলেই তো মিউটেশন, তাই না? এখন একবার ভেবে দেখুন তো, যদি আমাদের এই ডিএনএ, জিন যেই ফিতেটায় আছে, সেই ফিতেটার আকার আকৃতি যদি পরিবর্তন করে দিই, তাহলে ফিতের ভেতর থাকা তথ্য পালটে যাবে কীনা? নীচের উদাহরণটা দেখুন। ধরুন, একটা কল্পিত ক্রোমোজোমে লিখা আছে “তোমার বাড়িতে থামা যাবে”। এখন, ক্রোমোজোমের যে অংশে “থামা” কথাটা আছে, সে অংশে ধরুন কেউ ক্রোমোজোম কেটে “মা” কে আগে রাখলো, “থা” কে পরে রাখলো। পুরো কথার অর্থ পালটে হয়ে যাবে “তোমার বাড়িতে মাথা যাবে”। মনে হচ্ছে না কোনো সাইকোপ্যাথের পাঠানো চিঠি?
অনেকটা এভাবেই ঘটে ক্রোমোজোমাল মিউটেশন। ক্রোমোজোমের গঠন বা সংখ্যা পরিবর্তনকেই আমরা ক্রোমোজোমাল মিউটেশন বলি। এই মিউটেশন জিন মিউটেশনের মতো কেবল অল্প কিছু জিনকে প্রভাবিত করে না, একসাথে অনেক জিনকে প্রভাবিত করতে পারে। এই ক্রোমোজোমাল মিউটেশনের মাধ্যমে জিন সিকোয়েন্স পরিবর্তিত হয়ে প্রাণি, উদ্ভিদ সহ জীব জগতের প্রায় সব ডোমেইনেই বিবর্তন ঘটে। একটু পরেই আমরা পলিপ্লয়ডি সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভিদের নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটার উদাহরণ দেখবো, মানুষের বিবর্তনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা-ক্রোমোজোম-২ জোড়া লেগে যাওয়া, ডাউন সিনড্রোম হওয়া—এমন অনেক কিছু ঘটেছে, ঘটে ক্রোমোজোমাল মিউটেশনের কারণেই।
ক্রোমোজমাল মিউটেশন নানা ধরণের হতে পারে। একেকভাবে ক্রোমোজোমের গঠন পরিবর্তন হওয়ার ক্ষেত্রে নির্ভর করছে ক্রোমোজোমাল মিউটেশনের ধরণ। যেমন, কোনো একটি ক্রোমোজমের অনেকখানি অংশ আলাদা হয়ে যেতে পারে (deletion) । আবার, সেই আলাদা হয়ে যাওয়া অংশ আরেকটা ক্রোমোজমে যেয়ে জোড়া লাগতে পারে। এখন এই ব্যাপারটা একই টাইপের ক্রোমোজমে হলে সেটা duplication, আলাদা টাইপের ক্রোমোজমে যেয়ে জোড়া লাগলে translocation. বা ক্রোমোজমের কোনো অংশ উল্টে যেতে পারে (inversion) । আবার কখনো কখনো ক্রোমোজমের দুই প্রান্ত জোড়া লেগে যায়, সেটাকে তখন ring chromosome বলে। ক্রোমোজমের টেলোমিয়ার অংশ সাধারণত এমনটা হতে বাধা দেয়, তবে টেলোমিয়ার না থাকলে তারা জোড়া লেগে যায়।
২. জিন মিউটেশনঃ জিন মিউটেশন হলো জিনের ডিএনএ সিকোয়েন্সে স্থায়ী পরিবর্তন। এই পরিবর্তন ছোট বা বড় পরিসরে হতে পারে—কখনও একটি মাত্র ডিএনএ বেস পেয়ারকে প্রভাবিত করে, আবার কখনও একাধিক জিনসহ পুরো ক্রোমোজোমের অংশকে পরিবর্তন করতে পারে।
খুলেই বলি আপনাকে। জীব কোষ মাত্রই তার কোষ বিভাজন ঘটে, তাই না? সে বিভাজন জার্মালাইন এবং সোমাটিক—উভয় কোষেই ঘটবে। এবং কোষ বিভাজনের সময় ডিএনএ-রও বিভাজন হয়। অর্থাৎ ডিএনএ-র বিশাল লম্বা কোডগুলোর কপি তৈরী করতে হয় নতুন কোষ সৃষ্টির সময়। যাতে নতুন কোষে হুবুহু আগের কোষের মতই ডিএনএ কোডগুলো থাকে। এই কোড অনুযায়ী এমিনো এসিড পাশাপাশি জোড়া লাগিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন তৈরী করা হয়, যা প্রকাশ করে জীবদেহের নানান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু, রেপ্লিকেশনের সময় ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম সবসময় হুবুহু কপি করতে পারে না মাতৃ ডিএনএ থেকে। নানা কারণে কোডগুলো কপি করার সময় কিছু পরিবর্তন এসে যায়। জিনের কোথায় কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে সেটার ওপর নির্ভর করে এটা কোন ধরণের মিউটেশন। এই বেস পেয়ার কপিতে ছোটো একটা ওলটপাল্টের জন্য জীবের পুরো দেহেই কোনো না কোনো পরিবর্তন চলে আসে। এই পরিবর্তনটাকেই বলছি জিন মিউটেশন [১]।
এখন আপনি ADHD তে ফেঁসে থাকলে, এইটুকু কাটখোট্টা আলোচনা আপনার না পড়লেও চলবে। তাও আমি নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করে রাখছি। মন চাইলে পড়তে পারেন। উপরে বলেছি, মাতৃ ডিএনএ থেকে অপত্য নতুন ডিএনএ সৃষ্টির সময় নতুন ডিএনএ সূত্রকে মাতৃ ডিএনএ-র অক্ষরগুলি হুবহু কপি হয় না বলেই পরিবর্তিত এই ডিএনএ সিকোয়েন্স মিউটেশন ঘটায় জীবদেহে। এখন, জিনের কোথায় কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে সেটার ওপর নির্ভর করে এটা কোন ধরণের মিউটেশন। খুব সংক্ষেপে বলি। যেমনঃ
- পয়েন্ট মিউটেশন (Point Mutation) – ডিএনএ সিকোয়েন্সের শুধু একটা নির্দিষ্ট বেস পেয়ার (Adenine, Guanine, Cytosine, Thymine) একটি মাত্র বেস পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, মাত্র একটা বেস ভুল কপি হচ্ছে। যার ফলে প্রোটিনের একটি অ্যামিনো অ্যাসিড বদলে যেতে পারে। আবার যদি এমন জায়গায় মিউটেশন হয় যেটা কোনো কিছু প্রকাশ করল না, বা পরিবর্তন আনল না, অর্থাৎ, মিউটেশনের ফলে আসা নতুন কোড আদতে আগের কোডেরই আরেকটা ভার্সন, মানে এটাও একই এমিনো এসিডের জন্যেই কোড হয় তবে সেটাকে আমরা বলব সাইলেন্ট মিউটেশন।
- ইনসারশন (Insertion) – যখন ডিএনএ সিকোয়েন্সে এক বা একাধিক অতিরিক্ত বেস যুক্ত হয়, তখন ইনসারশন মিউটেশন ঘটে।
- ডিলিশন (Deletion) –ডিলিশন মিউটেশন তখন ঘটে যখন ডিএনএ সিকোয়েন্স থেকে এক বা একাধিক বেস বাদ পড়ে যায়। এই মিউটেশন প্রোটিন তৈরির গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা মুছে ফেলতে পারে।
- ফ্রেমশিফট মিউটেশন (Frameshift Mutation) – একটু জটিল, তবে সহজ করে দিবো। ফ্রেমশিফট মিউটেশন ঘটে যখন ইনসারশন বা ডিলিশন তিনের গুণিতকে না হয়, ফলে ডিএনএ পড়ার প্যাটার্ন (reading frame) বদলে যায়। যেহেতু প্রোটিন তৈরি হয় তিন-বেসের কোডন অনুযায়ী, ফ্রেমশিফট হলে প্রতিটি পরবর্তী অ্যামিনো অ্যাসিড পাল্টে যায়, যা সাধারণত অকেজো প্রোটিন বা পূর্ববর্তী স্টপ কোডনের জন্ম দেয়। উদাহরণ দিই। ধরি, THE CAT RAN FAR টাইপের জিন সিকোয়েন্সের জন্য কোনো প্রাণীর ডানার গঠন নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে প্রতিটাই তিনটা করে বেস আছে। একদম ডিএনএর মতই প্রতিটা শব্দ তিনটা অক্ষর দিয়ে বানানো। প্রতি তিনটা অক্ষর মিলে একটা অর্থবহ শব্দ হয়। যার ফলে আরামসেই প্রোটিন তৈরি হতে পারবে এই কোডনগুলি থেকে। কিন্তু কোনোভাবে যদি এখানের THE থেকে E এর ডিলিশন ঘটে, অর্থাৎ বাদ পড়ে, তাহলে কি দাঁড়ায়?
THC ATR ANF AR
কিছু অংশ আগের মতোই তিনটা অক্ষর মিলে একটা করে শব্দ তৈরী করেছে। কিন্তু এই শব্দগুলো আমাকে কোনো তথ্য দিচ্ছে না। অর্থাৎ, এরা যদি কোনো এমিনো এসিডের জন্য কোড হত তাহলে আমি উক্ত এমিনো এসিডের কোনোটাই তৈরী করতে পারতাম না।
মিউটেশন ঘটার কারণ
মিউটেশন অনেকভাবে ঘটতে পারে। অনেক কিছু মিউটেশনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করতে পারে। তবে এখানে তিনটা কারণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলি মিউটেশনকে নানানভাবে প্রভাবিত করে। পরোক্ষভাবে বিবর্তনকেই প্রভাবিত করে। কারণ তিনটি হলোঃ
১. স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন
২. ইনডিউসড মিউটেশন
৩. জীব প্রক্রিয়া ও কোষীয় চাপ
১. স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশনঃ স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন প্রাকৃতিকভাবে, এলোমেলোভাবে ঘটে। যেমন ডিএনএ রেপ্লিকেশনে ত্রুটি। যখন কোষ বিভাজন হয়, তখন ডিএনএ সিকোয়েন্স কপি করা হয়। মাঝে মাঝে নতুন ডিএনএ তে ভুল বেস ঢুকে পড়ে।ঘটে যায় মিউটেশন। আমাদের ডিএনএ-র মেরামত প্রক্রিয়া বেশিরভাগ ত্রুটি সংশোধন করে, তবে কিছু ভুল ঠিক থেকেই যায়। আবার ডিএনএ বেসের (যেমন, অ্যাডেনিন, থাইমিন, সাইটোসিন, গুয়ানিন) রাসায়নিক গঠনে সাময়িক পরিবর্তন ভুল বেস-পেয়ারিং তৈরি করে মিউটেশন ডেকে আনে। এটাকে বলি আমরা টটোমারিক শিফট। মাঝে মাঝে ডিএনএ তে থাকা নাইট্রোজেন ক্ষার সাইটোসিন থেকে একটি অ্যামিন গ্রুপ হারিয়ে ইউরাসিল-এ রূপান্তরিত হয়, যা পয়েন্ট মিউটেশন ঘটাতে পারে।
২. ইনডিউসড মিউটেশনঃ বাংলায় এটাকে বলা যায় প্ররোচিত মিউটেশন। এই ইনডিউসড মিউটেশন স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশনের উলটো এবং বেশ দ্রুত সময়েই ঘটতে পারে। অর্থাৎ, বাহ্যিক কোনো প্রভাবক দ্বারা ডিএনএ-র জিন সিকোয়েন্সে পরিবর্তন ঘটে এখানে। বিজ্ঞানীরা এই প্রভাবকগুলিকে বলেছেন মিউটাজেন। এই মিউটাজেন আবার বায়োলজিকাল হতে পারে, রাসায়নিক, ভৌত বা ফিজিকালও হতে পারে। আলাদা করে এই ৩ প্রকার মিউটাজেন নিয়ে জেনে রাখলেও ক্ষতি নেই। আবার জানতে না চাইলে আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন। অনেক মজার কিছু তথ্য মিস করবেন যদিও।
- রাসায়নিক মিউটাজেন – 5-bromouracil নামক এক প্রকার রাসায়নিক কম্পাউন্ড নকল নাইট্রোজেন বেইস সেজে ডিএনএ তে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে। ডিএনএ অনুলিপনের সময় ভুল-ভাল বেইস পেয়ারিং ঘটিয়ে মিউটেশন ঘটায়। মাস্টার্ড গ্যাস, EMS এর মতো কিছু অ্যালকাইলেটিং এজেন্ট ডিএনএ বেসে অ্যালকাইল গ্রুপ যোগ করে বেস-পেয়ারিংয়ে ত্রুটি ঘটিয়েও মিউটেশন ঘটাতে পারে। অন্যদিকে কিছু ইন্টারক্যালেটিং এজেন্ট ডিএনএ বেসের মধ্যে প্রবেশ করে ডিএনএ-র বেস এর ইনসারশন বা ডিলিশন ঘটায়। যেমন, অ্যাক্রিডিন ডাইস। সিগারেটের সাথে থাকা নিকোটিনও একটা শক্তিশালী রাসায়নিক মিউটাজেন। যেটা মিউটেশন সৃষ্টির মাধ্যমে ক্যান্সার ঘটাতে পারে।
- জীববৈজ্ঞানিক মিউটাজেন – কিছু ভাইরাস তাদের জেনেটিক উপাদান হোস্টের ডিএনএতে ঢুকিয়ে দিয়ে মিউটেশন ঘটাতে পারে। বিস্তারিত বলা যাক কেমন? সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা জানাচ্ছে, ভাইরাস সংক্রমণ পরোক্ষভাবে মানব বিবর্তনকে প্রভাবিত করেছে ইতিহাসে অনেকবার। বিশেষ করে স্নায়বিক এবং কগনিটিভ কার্যক্রমের সাথে জড়িত জিনগুলির উপর সিলেক্টিভ প্রেশার প্রয়োগ করে [২]। কিছু ভাইরাস নিজেদের জিনোম কপি তৈরি করে এবং সেই কপিকে তার হোস্টের জিনোমের অন্য কোথাও ঢুকিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে ট্রান্সপোজিশন বলা হয়। এবং ভাইরাসের ডিএনএ থেকে প্রাপ্ত এই এলিমেন্টগুলিকে বলে ট্রান্সপোজেবল এলিমেন্ট। এদের জাম্পিং জিনও বলা হয়। এই ট্রান্সপোজিশনের জন্যও মিউটেশন ঘটতে পারে। উদাহরণ হিসেবে নেয়া যায়, আমাদের ভাষা রপ্ত করার ক্ষমতা অর্জনের জন্য দায়ী FOXP2 gene কে। FOXP2 জিনের উদ্ভব সহ নানান কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টের পেছনে দায়ী মিউটেশন গুলো ঘটেছে এনডোজেনাস রেট্রোভাইরাল ইন্টিগ্রেশন এর কারণে। বলে রাখা ভালো যে, এনডোজেনাস রেট্রোভাইরাল ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে এমন একটি ট্রান্সপজিশন প্রক্রিয়া যেখানে একটি রেট্রোভাইরাসের রিভার্স-ট্রান্সক্রাইবড ডিএনএ এর কপি কোনো জীবের ক্রোমোজোমে সংযুক্ত হয়, যার ফলে সে জীবে ঘটে মিউটেশন [৩] । শুধু এ ব্যাপারটা নিয়েই গোটা এক আর্টিকেল লিখা যাবে, সেটা নাহয় অন্যদিনের জন্য তোলা রইলো।
- ভৌত মিউটাজেন – সূর্যের আলোতে থাকা অতিবেগুনী রশ্মি থাইমিন ডাইমার তৈরি করে, যা ডিএনএ অনুলিপিতে বাধা দেয়। পারমাণবিক দুর্ঘটনা বা অতিরিক্ত মেডিকেল ইমেজিং(এক্স রে, গামা রশ্মি) থেকে আসা আয়নায়িত রশ্মি ডিএনএ স্ট্র্যান্ড ভেঙে মিউটেশন ঘটিয়ে দেয়। যেমন, Drosophila melanogaster (ফলমাছি)-এর ওপর এক্স রে ব্যবহার করে দেখা গেছে, তাদের ডিএনএতে এমন মিউটেশন হয় যা চোখের রং বা ডানার আকৃতিতে পর্যন্ত পরিবর্তন এনে ফেলে। চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনার পর, আশেপাশের প্রাণী ও উদ্ভিদ উচ্চ রেডিয়েশনের পরিবেশে থাকতে থাকতে এদের ডিএনএ তে অনেকপ্রকার মিউটেশন ঘটে জেনেটিক ডাইভার্সিটি তৈরি হয়। কিছু প্রজাতি এমন বৈশিষ্ট্য তৈরি করে, যা তাদের ওই রেডিয়েশনপূর্ণ পরিবেশে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। এইতো, এ বছরেরই(২০২৪) মার্চ মাসে ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্কের অধ্যাপকেরা চেরনোবিল দূর্ঘটনাগ্রস্থ এলাকায় পাওয়া নেমাটোডা পর্বের এক কীটের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখেন, এরা রেডিয়েশনের বিরুদ্ধেও রেজিস্ট্যান্স গড়ে তুলেছে [৪] ।
৩. জীব প্রক্রিয়া ও কোষীয় চাপঃ এটা যদিও এতো বেশি ঘটে না, তবে ঘটে। কোষের স্বাভাবিক বিপাকীয় ক্রিয়ায় Reactive oxygen species (ROS) নামক এক প্রকার উপজাত তৈরি হয়। এই ROS ডিএনএ, প্রোটিন এবং লিপিডের ক্ষতি করতে পারে। কখনো কখনো ROS-এর কারণে বেস পরিবর্তন, স্ট্র্যান্ড ভাঙন বা ক্রস-লিংকিং হতে পারে যা জিন সিকোয়েন্সে প্রভাব রাখে। ঘটে যেতে পারে মিউটেশন। ডিএনএ রেপ্লিকেশনের সময় ভুল-ভাল কপি হওয়া বেইস-পেয়ারগুলোকে মেরামত করার কাজটা ব্যর্থ হলে রেপ্লিকেশন স্ট্রেস সৃষ্টি হতে পারে। এটাও মিউটেশন ঘটাতে পারে।
এতোক্ষণ জানলাম যে, কীভাবে মিউটেশনের মাধ্যমে জীবে নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ হয় এবং সে পরিবর্তন পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে যায় এবং কালের বিবর্তনে সেসব নতুন বৈশিষ্ট্যের ফলে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে ন্যাচারাল সিলেকশানের মাধ্যমে। পরবর্তী পর্বে দেখাবো কীভাবে এই নতুন প্রজাতির উদ্ভব বা স্পিসিয়েশন প্রভাবিত হয়।
তথ্যসূত্র–
- [১] Semi-Conservative DNA Replication: Meselson and Stahl
- [২] Viral Integration and Consequences on Host Gene Expression – PMC
- [৩] Chronic inflammation as a promotor of mutagenesis in essential thrombocythemia, polycythemia vera and myelofibrosis. A human inflammation model for cancer development? – ScienceDirect
- [৪] Environmental radiation exposure at Chornobyl has not systematically affected the genomes or chemical mutagen tolerance phenotypes of local worms. Proceedings of the National Academy of Sciences, 121(11).

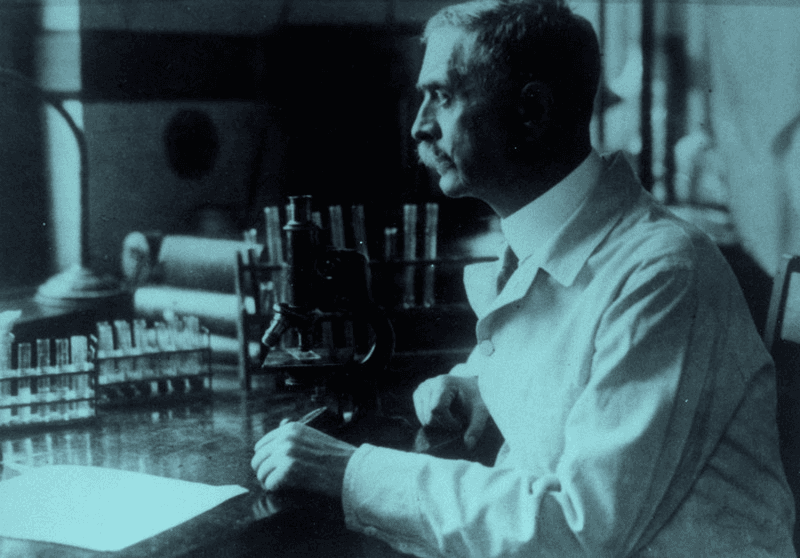






Leave a Reply