কয়েক বছর আগে, আমার হার্নিয়া অপারেশন করা হয়। এমন একটা অভিজ্ঞতা, যেটা প্রতি চারজনের একজন ব্রিটিশ পুরুষের হয়। তার মানে প্রতি একশ জনে পঁচিশ জন, বেশ ভাবানোর মত একটা সংখ্যা। হার্নিয়া এমন একটা রোগ, যেখানে অন্ত্রের একটা অংশ ঝিল্লি ফুঁড়ে নিচে নেমে আসে, আর নিম্নাঙ্গে বিচ্ছিরি এবং বিপজ্জনক একটা স্ফীতি তৈরি হয়। অপারেশনের কাজটা একজন সার্জনের, নিঃসন্দেহে উনি আগেও আরো কয়েকশ বার একই জিনিস করেছেন।

কিন্তু, এতো বেশি মানুষের এই সমস্যাটা হয় কেন? কাহিনীর শুরু আসলে অনেক আগে, যখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা সাগরে সাঁতরে বেড়ানো মাছের পর্যায়ে ছিল। সেই ‘গেছে যে দিন সুখে’র সময়ে, জননকোষ বা অন্ডকোষ শরীরের অনেক গভীরে, লিভারের কাছাকাছি জায়গায় ছিলো (আমাদের জলজীবি আত্মীয়দের মধ্যে এখনো ঠিক তেমনি আছে)। দুটো সোজা নালিকার মধ্য দিয়ে এই জননকোষগুলো বাইরের সাথে যুক্ত ছিল। তারপর ধীরে ধীরে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটল। জলজীবন থেকে প্রাণ উঠে এল ডাঙায়, শীতল রক্ত থেকে উত্তরণ ঘটল উষ্ণ রক্তে। এই পরিবর্তনের অনেক সুফল ছিল। তবে পুরুষ সদস্যদের জন্য একটা সমস্যাও একই সাথে দেখা দিলো। সমস্যার কারণ অন্ডকোষ- শুক্রাণু উৎপাদনের এই জটিল যন্ত্রপাতি- কম তাপমাত্রায় সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করে (সম্ভবত ডিএনএ কপি করার কাজে ভুল কম রাখার জন্য এই ব্যবস্থা)। রক্ত উষ্ণ হওয়ায় এই কাজে কিছুটা ভজঘট হয়ে গেল।
কিছুটা জগাখিচুড়িভাবে সমাধান হল এই সমস্যার। বিবর্তনের ধাপে ধাপে অন্ডকোষ নিচের দিকে নেমে এলো, শরীর থেকে বেরিয়ে এসে তৈরি করল এলিগ্যান্ট অন্ডথলি (এই জায়গাটায় এসে ছাত্রদের পড়াতে আমি ভুলি না- কাজের দিক থেকে হোক আর দেখার দিক থেকে হোক, পুরুষের শরীরে এটাই সবচেয়ে ‘কুল’ অংশ…)। এই নেমে আসার পথে, সেই যে টিউবগুলো ছিল, সেই টিউবগুলো শ্রোণিদেশের(কোমরের ঠিক নিচে) হাড়ের চারধারে অনেকবার পাক ঘোরে, শরীরের ভেতরে একটা পর্দার মতো অংশ তৈরি করে তোলে। বেশ দুর্বল একটা জায়গা এই পর্দাটা, ইনটেস্টাইন যে জায়গাটা প্রায়ই ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে।
কাজেই, হার্নিয়া হচ্ছে এভোলুশন বা বিবর্তনের একটা অসমাপ্ত প্রক্রিয়ার ফলাফল, যেখানে সমন্বিত হয়েছে ধাপে ধাপে ঘটা অসংখ্য ‘সফল কিন্তু ভুল সিদ্ধান্ত’ এবং বৈরি পরিবেশে মানিয়ে চলার ক্রমাগত চাপ। তবে সার্জনের এত কিছু জানার দরকার হয় না। সমস্যার গোড়ার কথাটা না জেনেই, ‘ওরিজিন ওব স্পিশিজ’ প্রকাশিত হবার অনেক আগেই, প্রথম হার্নিয়া অপারেশন করা হয়ে গিয়েছে। আর আমার মনে হয়, যে ডাক্তার আমার অপারেশনটা করেছিলেন, তাঁরও এসব জানা ছিলো কিনা সন্দেহ!
এখন, আমাদের হাতে এসেছে এভোলুশন, জীববিজ্ঞানের গ্রামার, ব্যাকরণ। কিন্তু দিনকেদিন, অনেক ছাত্র এটা আর পছন্দ করে উঠছে না। আমি এখন আর মেডিকেল বিষয় পড়াই না, তবু অনেক জীববিজ্ঞান ছাত্রের সাথে যোগাযোগ আছে, বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে এবং স্টুডেন্ট কনফারেন্সে নিয়মিত যাওয়াও হয়। গত দশক জুড়ে আমি দেখেছি- অনেক মানুষ আধুনিক বিজ্ঞানের এই সত্যগুলোকে মেনে নিতে পারছে না।

লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে আমাদের বেশ কিছু মুসলিম শিক্ষার্থী আছে। তাদের প্রায় সবাই নিবেদিতপ্রাণ, কর্মঠ মানুষ। এদের মধ্যেই কিছু মানুষ, দুর্ভাগ্যক্রমে, ধর্মবিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক বলে ডারইউনের সূত্রকে ত্যাগ করতে চায়। কিছু খ্রিস্টান ছাত্রও এই কাজ করে থাকে। এমনকি কয়েক বছর আগে এক তুর্কি এভোলুশনবিরোধী বক্তাকে(যতদূর মনে পড়ে, কোনো এক ড. বাবুনা) ক্যাম্পাসে আমন্ত্রণ করা হয়, ‘দ্যা ওরিজিন’ কেন ভুল সেটা বলার জন্য। উনি নিজের দেশের এভোলুশনবিরোধী একটা বিত্তশালী সংগঠনের অনুগামী। এই সংগঠন সুন্দর ছবিওয়ালা হাজার হাজার সৃষ্টিতত্ত্ববাদী(creationist – যারা দাবি করে প্রাণ বিবর্তিত হয়নি, সৃষ্ট হয়েছে) বই ছড়িয়ে বেড়ায় এবং ডারউইনিজমকে নাৎসিইজম বা আরো খারাপ কিছুর সাথে তুলনা করতে পছন্দ করে।
মুসলমান সেই ছাত্রদের এসব প্রোপাগান্ডা খ্রিষ্টান মৌলবাদ থেকে তুলে আনা হয়েছে, আর তারা সেটা ব্যবহার করছে, সেবিষয়ের নির্মম কৌতুকটা চোখ এড়াবার নয়। আমি দুপক্ষের আন্ডারগ্রাজুয়েট ছাত্রদের দিক থেকেই ‘ধর্ম বিনাশের’ মৌখিক অভিযোগ পেয়েছি। আরো কিছু ছাত্র আছে যারা আমার সাবজেক্টের লেকচারগুলো থেকে অব্যাহতি নিতে চায়, অথবা সরাসরি অগ্রাহ্য করতে চায়।
স্কুল কলেজের অবস্থা আরো খারাপ: লেকচারে অংশ নেবার চেয়ে চলে যেতে তাদের উৎসাহ বেশি। শিক্ষকদের মধ্যেও অনেকে এই কাজের কাজী। আমি সবচেয়ে বিষাক্ত আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিলাম উত্তর লন্ডনের একটা নামী স্কুলের পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষক- অন্য শিক্ষকদের বিব্রত করে তোলা একজন- তার কাছে। তিনি আমাকে আটকাতে চেষ্টা করেছেন বারংবার একই কথা বলে- ডারউইনিজম নাকি থার্মোডিনামিক্সের সূত্রের সাথে সাংঘর্ষিক। স্বভাববিরুদ্ধভাবে, আমি রূঢ় হতে বাধ্য হয়েছিলাম।
যে কেউ, অবশ্যই যা ইচ্ছে তা বিশ্বাস করতে পারে। কিন্তু তাহলে জীববিজ্ঞানী বা ডাক্তার হবার মানে কী, যেখানে তুমি তোমার সাবজেক্টের মূল স্বীকার্যকেই অস্বীকার করতে চাও? একজন ইংরেজির ছাত্রের ইংরেজি গ্রামার অবিশ্বাস করাটা যে রকম, বা একজন ফিজিক্স ছাত্রের অভিকর্ষ বল অস্বীকার করাটা যেরকম, জীববিজ্ঞানের একজন ছাত্রের এভোলুশন মেনে নিতে অস্বীকার করাটাও ঠিক তেমনি। এই অস্বীকারের কোনো মানেই দাঁড়ায় না। একই কথা ডাক্তারদের ক্ষেত্রেও খাটে। তুমি একটা শরীরকে ঠিক করবে কীভাবে, যখন শরীরের এই বিগড়ে যাবার গোড়ার কথাটাই তুমি জানো না?
আমি আলাদাভাবে ছাত্রদের কাছে জানতে চেয়েছি, আমার লেকচারের কোন অংশটাতে তাদের আপত্তি: উত্তরাধিকারের সূত্রে, বা মিউটেশনে, ম্যালেরিয়া বা ক্যান্সারের প্রতিরক্ষক জীনগুলোর বিষয়ে, বৈশ্বিকভাবে মানুষের ত্বকের রঙ বিভিন্ন হওয়ার ব্যাখ্যায়, নিয়ান্ডারথাল মানবের ডিএনএতে, অথবা বানর গোত্রীয় প্রাণীদের সাথে মানুষের বিবর্তনগত পার্থক্যে? তাদের ভাষ্যে, আলাদাভাবে, প্রতিটা বিষয়ই খুব ইন্টারেস্টিং। তারপর আমি যখন বলি, তাহলে তো তারা ডারউইনের তত্ত্বের পুরো বিষয়টাই মেনে নিচ্ছে, ঠিক তখনই তারা ভীতিকর চিন্তাটা প্রত্যাখ্যান করতে চেষ্টা করে। কেউ কেউ সেইক্ষণেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ভাগ্যিস, বাকিরা চিন্তান্বিত মুখ নিয়ে ফিরে যায়।
সমস্যাটা আসলে কোনো নির্দিষ্ট ‘বিশ্বাস ব্যবস্থা’-র নয়, বরং ‘বিশ্বাস’ বিষয়টার মাঝেই নিহিত। স্যার ফ্রান্সিস বেকন বলেছিলেন, “একজন মানুষ যদি সিদ্ধান্ত নেবার পরে (জানতে) শুরু করে, সে শেষটায় গিয়ে দ্বিধার মাঝে পড়বে। আর দ্বিধা নিয়ে যদি জানার পথে এগিয়ে যায়, তবেই শেষে সিদ্ধান্তটায় গিয়ে পৌঁছুবে।” অন্য কথায় বলতে গেলে, তুমি যদি নিশ্চিত হয়ে বসে থাকো যে, যতই প্রমাণ-উপাত্তের বিরোধী হোক না কেন, তোমার কথাই ঠিক, তাহলে তুমিই শেষে সমস্যায় পড়বে। কিন্তু তুমি যদি বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিবর্তনের সাথে নিজের মনকে মানিয়ে চলতে পারো, এই ভুবন কীভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে তখন তোমার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে।
আমার মাঝে মাঝে ভাবতে অবাক লাগে, এত মানুষ যে তাদের আদরের সৃষ্টিতত্ত্ব মতবাদ নতুন প্রজন্মের কানে ঢালছে, এদের মাঝে কতজন ভেবে দেখে যে তারা কতখানি ক্ষতি করছে? না, আমার বিজ্ঞানটুকুর নয়, তাদের ধর্মেরই ক্ষতি। সোজাসাপ্টা কিছু সত্যি, যেগুলো ব্যাখ্যা দেয় জীবনের উৎপত্তির মৌলিক কিছু প্রশ্নের, যেগুলো জীবনের উৎপত্তি নিয়ে রূপকথা শোনায় না, সেই সত্যিগুলোর বদলে একজন শিক্ষার্থীর অন্য কোনোকিছু বিশ্বাস করতে হবে কেন? কেন তার প্যাস্টর, রাবাই, বা ইমামের কথায় তাকে সত্যিটার বদলে অন্যকিছু মেনে নিতে হবে? কেন একটা অসত্যে পূর্ণ ধ্যানধারণা লালন করতে হবে, যেখানে এখন আমাদের হাতে অগণিত সত্য, এবং আরো বহু সত্য আবিষ্কৃত হবার অপেক্ষায় রয়েছে?
সত্য-অস্বীকারের এই প্রাবল্য আসলে একটা ব্যর্থতার কাহিনী। শিক্ষার্থীদের ব্যর্থতা নয়, ব্যর্থতা তাদের শিক্ষকদের, সব শ্রেণীর শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত। আমার মনে হয়, আমরা নিজেদের যথাসাধ্য সেরা চেষ্টা করে চলেছি। তবে বিশ্বাসীদের দঙ্গলের শূন্যসার অজ্ঞতা দেখে মাঝে মাঝে মনে হয়, হেরে যাওয়া একটা লড়াই লড়বার চেষ্টা করছি কেবল। কয়েক হপ্তা আগেই একটা উত্তেজক বক্তৃতা দিলাম, “কেন এভোলুশন ঠিক এবং সৃষ্টিতত্ত্ববাদ ভুল” শিরোনামে। তারই শেষে একটা কাঠিন্যপূর্ণ আলোচনা চলে। সেই আলোচনায় এক ছেলে আমাকে একটা কথা বলে ব্যাকফুটে ঠেলে দেয়- বিজ্ঞান সার্বজনীনভাবে অনিশ্চয়তা এবং পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল, এবং বিজ্ঞানী হিসাবে আমার “কেন এভোলুশন ঠিক” এজাতীয় নিশ্চিত সুরে কথা বলা ঠিক হয়নি- এই ছিল তার বক্তব্য। আমি কম্প্রোমাইজ করলাম, বললাম এখন থেকে এই বক্তৃতাটার নাম হবে “কেন এভোলুশন ‘সম্ভবত’ সত্যি, এবং সৃষ্টিতত্ত্ব নিশ্চিতভাবে ভুল”। কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, এভাবে আসলে সমস্যাটার সমাধান হবে না।
[এই লেখাটি ‘দ্যা টেলিগ্রাফ’ পত্রিকায় প্রকাশিত স্টিভ জোন্সের একটি প্রবন্ধের ভাবানুবাদ। লেখাটির লিংক এখানে। ]
[বিজ্ঞান ব্লগ সম্পাদকের পাদটীকা: এই অনুবাদটি করেছেন অবর্ণন রাইমস। যে খবরের প্রেক্ষিতে এই লেখাটি আসলো তার লিঙ্ক এখানে।]

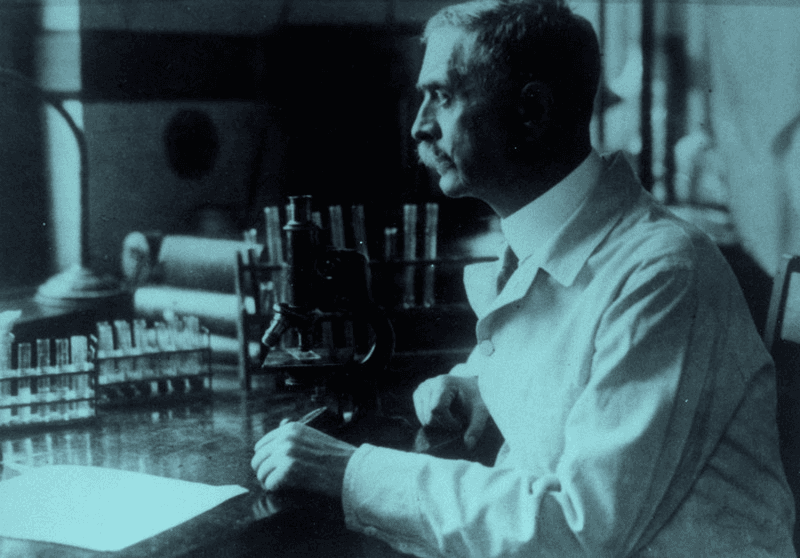


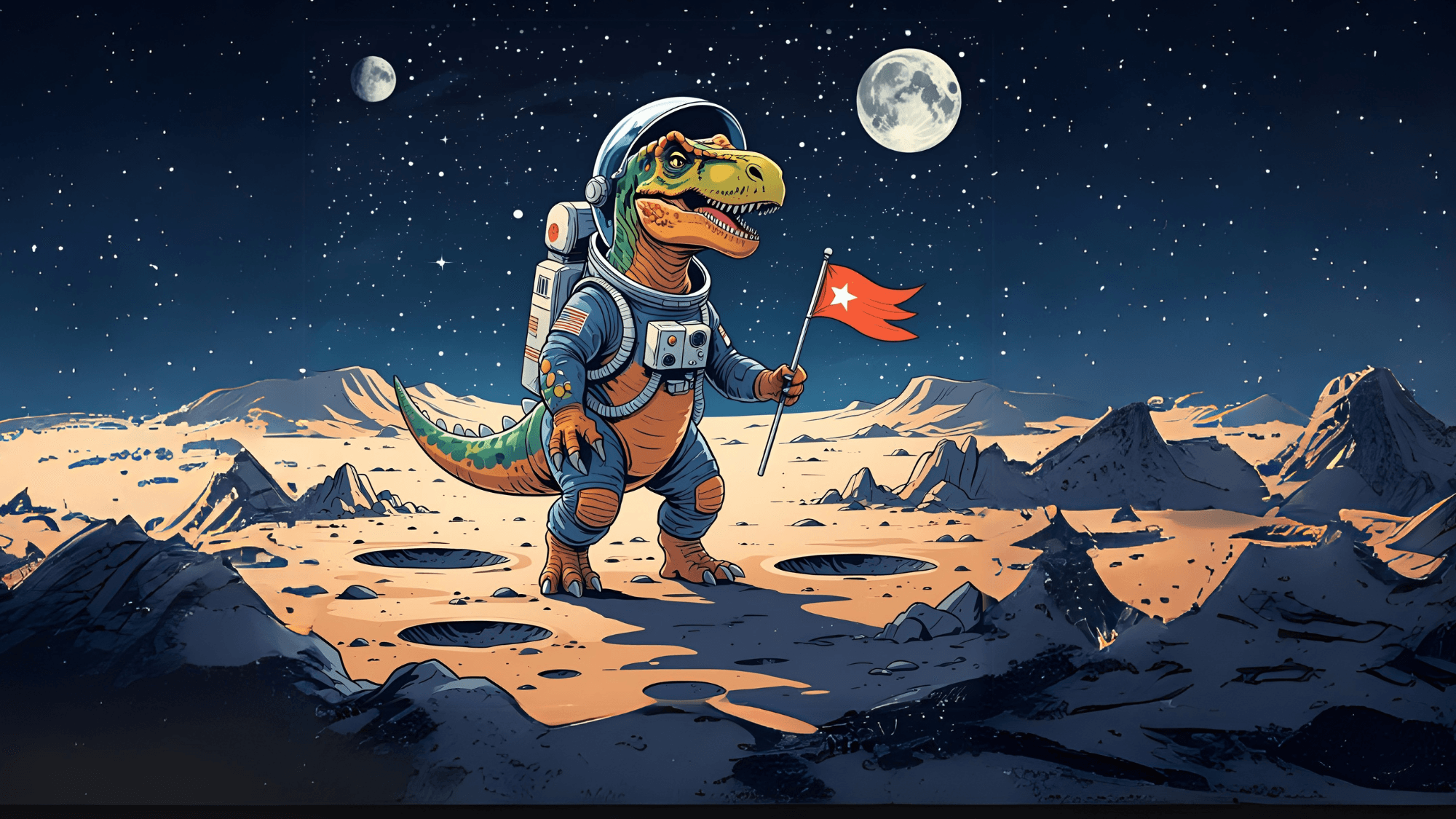
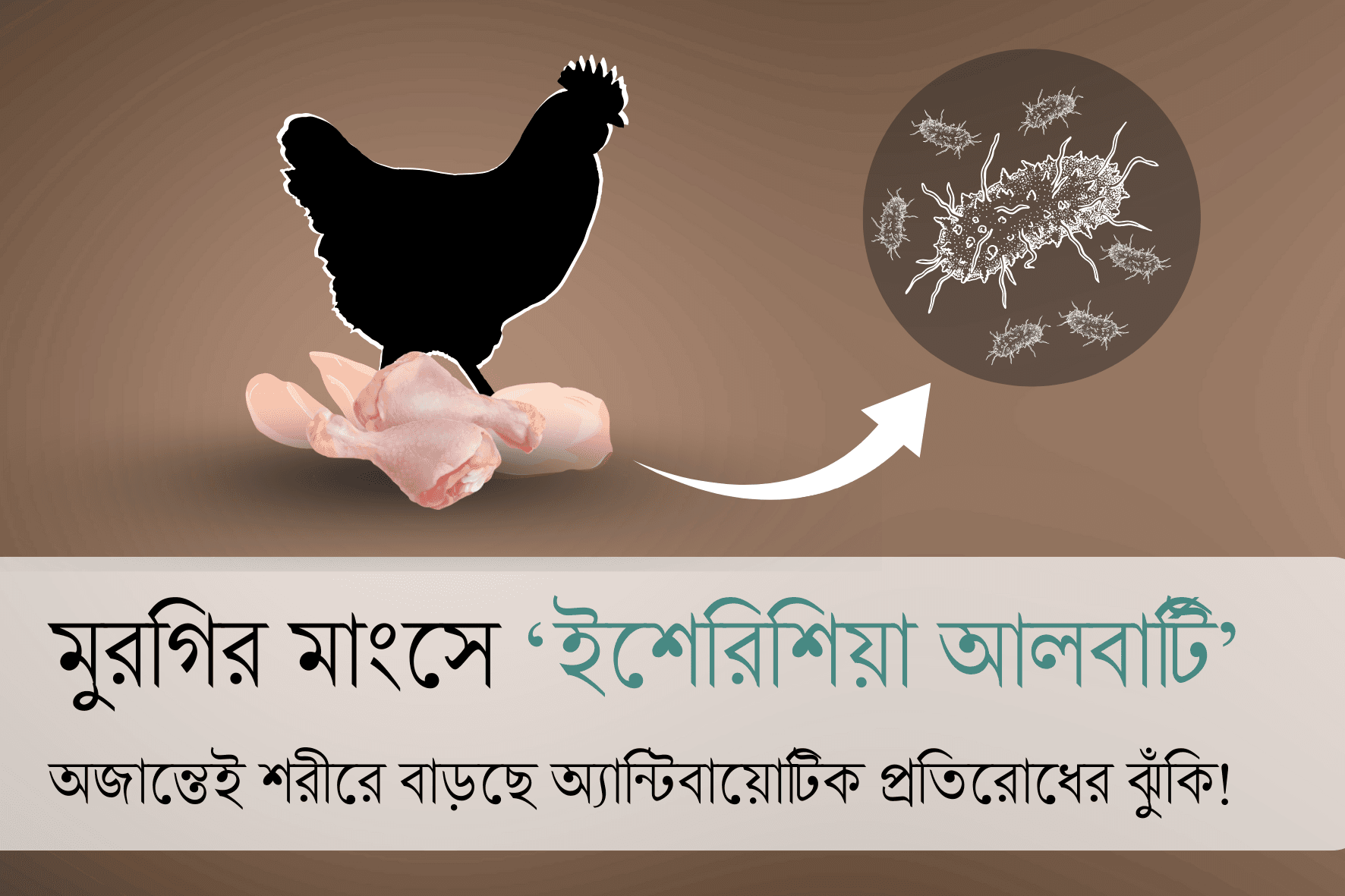


Leave a Reply