(কন্টিনেন্টাল ড্রিফট)
১ম পর্ব
আজকের পৃথিবীর সবথেকে উঁচু যে পর্বতমালা হিমালয় তা একসময় এমন ছিল না। যে হিমালয় তার উচ্চতার গুনে উত্তর দিক থেকে আসা কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসকে ঠেকিয়ে রেখে আমাদের রক্ষা করে, সে হিমালয় একসময় এখনকার সমতল ভূমির মতই নিচু ছিল। সামগ্র্ ভারতীয় উপমহাদেশও একসময় এশিয়ার সাথে লেগে ছিল না। আলাদা একটি অংশ ছিল এই ভারত। আর ভারত বলতে তো আমাদের বাংলাদেশকেও বোঝানো হয়। ভারত নামের ভূখণ্ডটি এক সময় চলতে চলতে এশিয়ার ভূখণ্ডের সাথে মিলিত হয়। মিলিত হবার সময় প্রচণ্ড রকমের যে ধাক্কা বা চাপের সৃষ্টি হয়েছিল সে প্রবল চাপের ফলেই ভারত ও এশিয়ার সংযোগ স্থলে কিছু মাটি উপরের দিকে উঠে যায় এবং তাতেই হিমালয়ের সৃষ্টি হয়। সে চাপ এতই বিশাল পরিমাণের ছিল যে তার ফলে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্টের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি এখনো দিন দিন হিমালয়ের উচ্চতা বেড়ে চলছে। আজকের দিনেও সে বৃদ্ধি পাবার প্রক্রিয়া বহাল রয়েছে।
মহাদেশ গুলোর কিংবা ভূখণ্ডগুলোর হেটে হেটে চলে বেড়ানোর এই প্রক্রিয়াকে বলে কন্টিনেন্টাল ড্রিফট বা মহাদেশীয় বিচ্যুতি। অনেক জায়গায় এই Continental Drift শব্দটির পরিভাষায় ‘মহাদেশীয় সঞ্চরণ’ কিংবা ‘মহী-সঞ্চরণ’ অথবা ‘মহাদেশীয় প্রবাহ’ও ব্যাবহার করা হয়।
পৃথিবীর প্রধান কটা স্থলভাগ দিনের পর দিন হেটে হেটে বেড়ায় এমন মজার একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছিলেন জার্মানের ভূতত্ত্ববিদ আলফ্রেড ভেগেনার [১]। (Alfred Wegener জার্মান ভাষায় W এর উচ্চারণ ভ এর মত।) সর্বকালের সেরা কয়েকটি আবিষ্কার যদি তালিকা করা হয় তাহলে এই মহাদেশীয় বিচ্যুতি তাদের মাঝে একটি। সেরা ১০ টি ভূ-বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাঝে মহাদেশীয় বিচ্যুতি প্রথম দিকের একটি হিসেবে অবস্থান করবে। আজ থেকে একশ বছর আগের কথা, আলফ্রেড ভেগেনার এক মনে তাকিয়ে ছিলেন একটি ভূ-গোলকের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল আফ্রিকা মহাদেশ আর দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে যদি একসাথে এনে জুড়ে দেয়া হয় তাহলে তারা যেন খাপে খাপে মিলে যায়। শুধু আমেরিকা আর আফ্রিকাই না খেয়াল করলে দেখা যাবে অনেক বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডই অন্য দিকের কোনো ভূখণ্ডের সাথে মিলে যায়। এটা যেন জিগস পাজল [২] মেলানোর মত কোনো কিছু।

তার কাছে মনে হল এমনও তো হতে পারে বহু বছর আগে মহাদেশ গুলো একত্রে লেগে ছিল। কালে কালে একটু একটু করে সরতে সরতে আজকের এই অবস্থানে এসে পড়েছে। তার অনুমান করা এই তত্ত্ব তিনি উপস্থাপন করলেন ১৯১৫ সালে। স্বভাবতই যুগান্তকারী এই তত্ত্ব নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে কথা হবে। এর জন্য একটা ব্যাখ্যা দরকার যে কেন পৃথিবীর বড় বড় ভূখণ্ড গুলো এমন হেটে বেড়ায়? এর একটা ভাল ব্যাখ্যা হল পৃথিবী সৃষ্টির সময় তার তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি ছিল। এতই বেশি ছিল যে পানিটুকু পর্যন্ত থাকার ফুরসত হত না। আস্তে আস্তে নানান প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর বাইরের দিকের অংশটা ঠাণ্ডা হতে লাগল। একসময় ঠাণ্ডা হয়ে প্রাণ ধারণের উপযোগী হল। কিন্তু উপরিভাগটা কোমল ঠাণ্ডা হলেও ভেতরের অংশটা আগের মতই রয়ে গেছে গরম। সেখানকার তাপমাত্রা ছয় হাজার ডিগ্রীর চেয়েও বেশি [৩] । এই প্রচণ্ড তাপ প্রবাহিত হয়ে চলে আসে উপরের কম তাপমাত্রার দিকে। কেন্দ্রের দিক থেকে বেশ অনেকটা উঁচু পর্যন্ত উঠে আসতে তাপমাত্রার কোনো সমস্যা হয় না কারণ পৃথিবীর অভ্যন্তরের সে অংশটা তরল এবং তাপ পরিবাহী। কিন্তু এরও উপরের কঠিন স্তরে এসে তাপের জন্য একটা বাধা পড়ে যায়। তাপ আর আগের মত স্বাভাবিকভাবে মাটিতে পরিবাহিত হতে পারে না। সে তাপটা কঠিন মাটির তল ঘেঁসে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। এই যে ছড়িয়ে যায় তার প্রভাবেই অতি সামান্য পরিমাণে মহাদেশের প্লেট গুলোও সরে যায়। পরিমাণটা এতই সামান্য যে চোখে ধরার মত না। কিন্তু যতই সামান্য হোক না কেন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর পর কিন্তু সে সামান্য করে করেই হয়ে যায় বিশাল কিছু। একটু একটু করেই আজকে আমেরিকা আর আফ্রিকা মহাদেশের মাঝে দূরত্ব হয়েছে হাজার হাজার মাইল। উল্লেখ্য আলফ্রেড ভেগেনার মহাদেশ হেটে চলার এই তত্ত্ব দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু মহাদেশগুলো কেন হেটে চলে তার ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। উপরের ব্যাখ্যাটি তিনি দিতে পারেন নি। তিনি অনুমান করেছিলেন পৃথিবী প্রতিনিয়তই যে নিজের অক্ষের উপর ঘুরে চলছে সে চলার ফলে পৃথিবীর বাইরের দিকে একটা বহির্মুখী ধাক্কার সৃষ্টি হচ্ছে। সে বহির্মুখী ধাক্কার প্রতিক্রিয়াটা প্রভাব রাখছে মহাদেশের সঞ্চরণের উপর। এখন আমরা জানি এটা সঠিক নয়। আর তার তত্ত্বের প্রমাণের জন্য তিনি তাছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার ফসিল, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সাথে সাথে আফ্রিকার প্রাচীন ফসিল ও প্রত্ন সামগ্রীর মিল দেখিয়েছেন।
যেমন নিচের চিত্রে একটি মেসোসরাসের ফসিল যা ব্রাজিল (দক্ষিণ আমেরিকা) ও আফ্রিকাতে পাওয়া যায়। এটি একটি কুমির জাতীয় প্রাণী।

এই প্রাণীর পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিল না মাঝের এত বড় মহাসগর পাড়ি দিয়ে আফ্রিকা থেকে ব্রাজিল যাওয়া কিংবা ব্রাজিল থেকে আফ্রিকা যাওয়া। আমাদের এখনকার সময়েরই সামান্য যে বনজঙ্গলে নদীর মাঝে দ্বীপ থাকে, কিংবা একটা স্থলভূমির এলাকা চারিদিক থেকে পানি দিয়ে ঘেরা থাকে। সে দ্বীপের বাস্তু-সংস্থান জঙ্গল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অথচ তাদের মাঝের দূরত্ব একদমই কম। জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীদের পক্ষে সেখানে নদী সাতরে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাই এত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও অনেক অনেক পার্থক্য থাকে তাদের মাঝে। আর উপরের মেসোসরাস ফসিল তো হাজার হাজার মাইল দূরে। এটা সম্ভব হতে পারে যদি ধরে নেয়া হয় ভূমি দুটি আগে একসাথে একত্রে লেগে ছিল। এরকম অনেক প্রাণীর ফসিলে মিল পাওয়া গিয়েছে যারা হাজার হাজার মাইল দূরে কিন্তু দেশ গুলোকে একত্রে জুড়ে দিলে যেন তারা একটি সুন্দর লাইনে চলে আসে। নিচের ছবিতে তাদের প্রাপ্তির এলাকা বা বিচরণস্থল গাড় লাইনে দেখানো হল।

শুধু প্রাণীর ফসিলই না ভু-প্রকৃতি, খনিজ সম্পদ, পরিবেশ ইত্যাদি অনেক কিছুর মাঝেই তাদের এলাকা ভিত্তিক মিল পাওয়া গেছে। তার মানে স্পষ্টই একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় আগে কোনো এক সময় আফ্রিকা ও আমেরিকা একসাথে ছিল। সাথে সাথে অন্য মহাদেশ গুলোও একত্রে মিলে ছিল।
পরের অংশ দেখুন দ্বিতীয় পর্বে।






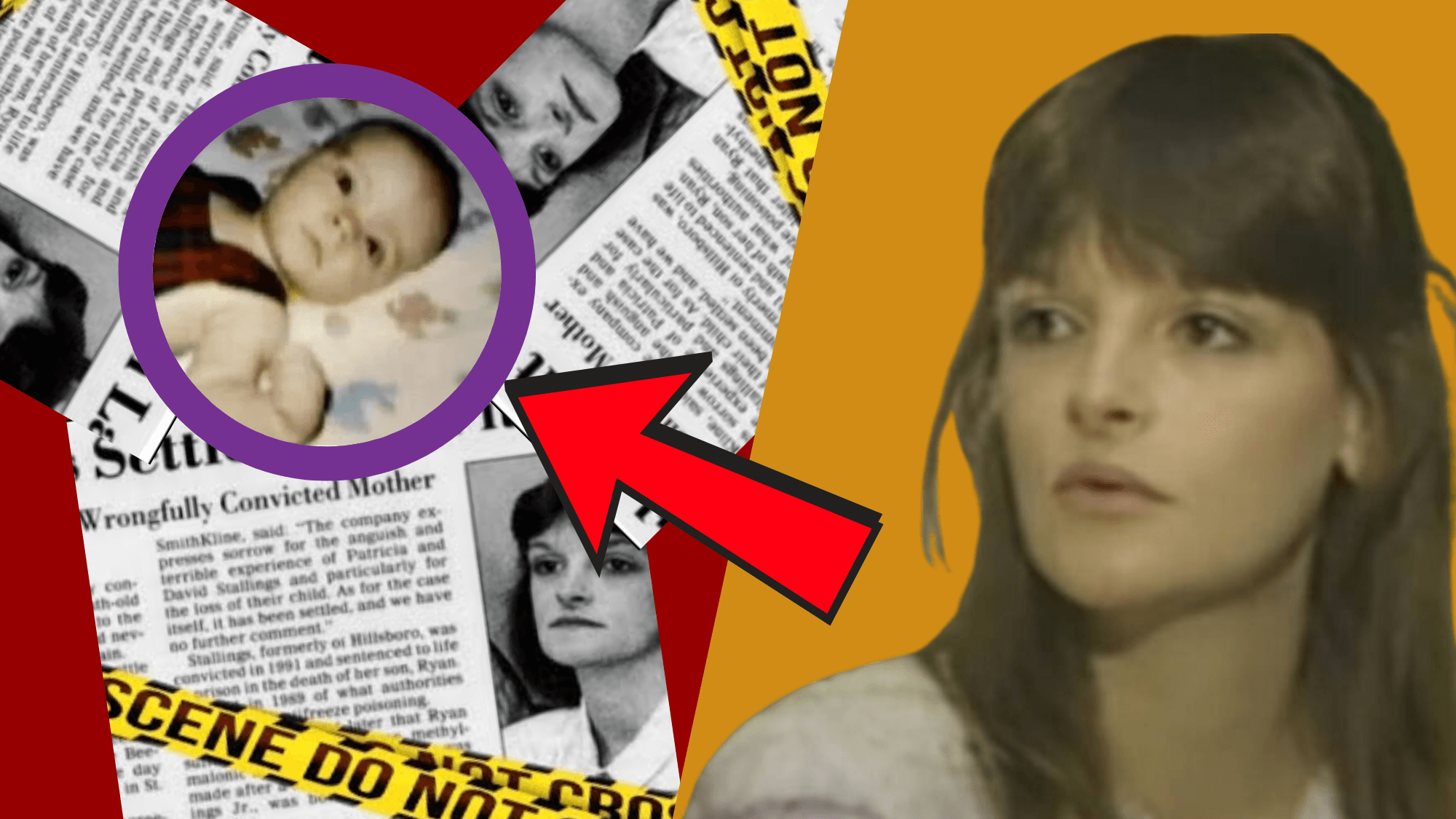

Leave a Reply