যখন ছোট ছিলাম তখন খাওয়ার আগে আর বাথরুম থেকে আসার পর হাত ধোয়ার জন্যে বিটিভিতে সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন দেয়া হত। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতাম। আর মা তো লেগেই থাকতো খাবার আগে ভালো করে হাত ধোয়ার জন্যে। তখন যেটা জানতাম জীবাণু হচ্ছে আমাদের জন্মের শত্রু! এরা আমাদের শরীরে ঢুকে আর আমাদের বারোটা বাজিয়ে দেয়। তাই জীবাণুর প্রতি no ভালোবাসা, Only ঢিসুম ঢিসুম with লাইফবয়! কিছুটা বড় হওয়ার পর দুর্ভাগ্য কিংবা সৌভাগ্যক্রমে অণুজীববিজ্ঞান বিভাগে অনার্সে ভর্তি হলাম। দেখি এতদিন যাদের জীবাণু বলে জানতাম তাদের একটা ভদ্র নাম আছে ‘অণুজীব’, ইংরেজিতে Microorganism. মনে মনে বলি micro নামের মধ্যে একটা ব্যাপার আছে, ভাব ই আলাদা! আর কতদিন পর দেখি অণুজীবদের জীবাণু বললে শিক্ষকরা রাগ হন। অণুজীবরা নাকি অনেক ভালো! এদের ১ভাগ নাকি রোগবালাই তৈরি করে বাকি ৯৯ ভাগ আমাদের জন্যে শুধু উপকারীই নয় বরং দরকারি। মনে মনে বলি ভালোই তো!
তবে সমস্যা হচ্ছে প্রথম প্রথম যখন কেউ ভার্সিটিতে ভর্তি হয় তখন তার মাথায় অনেক উচ্চমার্গিয় চিন্তাভাবনা ভর করে। আমার বেলাও তাই হয়। প্রথম যখন ভর্তি হই তখন খালি ভাবতাম যত রোগবালাই আছে তার পিছনের জীবাণু বের করব আর এন্টিবায়োটিক আবিস্কার করে জীবাণুর বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব। তবে দিন যত যাচ্ছে শুধু অণুজীবের ভালো দিকগুলো চোখে পড়ছে। এখন মনে হচ্ছে ভালো দিকগুলো যাতে ঠিক ঠাক কাজ করে এজন্যেও কাজ করা দরকার!
যাই হোক এবার নিজের গীত বন্ধ করে কাজের কথায় আসি। এই যে এতক্ষণ অণুজীব নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করলাম সেই অণুজীব কোথায় থাকে? উত্তর হচ্ছে সবখানে। মাটিতে, বায়ুতে, পানিতে সব জায়গায়তেই মহাশয়রা বিদ্যমান। তবে আজকে কথা বলব সেইসব অণুজীব নিয়ে যারা আমাদের শরীরে থাকে। হা ঠিক শুনেছেন আমাদের শরীরে! আমাদের শরীর হলো অণুজীবদের আড্ডাখানা! আমাদের শরীরে কোষের সংখ্যা হচ্ছে ১০ ট্রিলিয়ন। আর অণুজীবের সংখ্যা হচ্ছে ১০০ ট্রিলিয়ন!!! তার মানে আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আপনি কি? আপনার উত্তর হওয়া উচিত আমি ১০ ভাগ অণুজীব ১ ভাগ মানুষ! আপনার কোলনে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন । আমাদের শরীরে যে পরিমাণ ব্যাকটেরিয়ার জিন আছে তা আমাদের শরীরের তুলনায় প্রায় ১০০ গুন। অদ্ভুত! আমাদের শরীরে যে অসংখ্য অণুজীব বাসা বেধে রেখেছে তাদের একটা গাল ভরা নাম আছে ‘Human Microbiome’ এটা এমন কিছু নাহ, আমাদের শরীরের যেসব অণুজীবদের কথা বলছিলাম এদেরকে একসাথে Microbiome বলে।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে এঅণুজীবগুলো আমাদের শরীরে কি করছে? এরা অলসভাবে বসে নেই। কিছু ভিটামিন আছে যাদের আমাদের শরীর তৈরি করতে পারে না। যেমনঃ ভিটামিন কে, বায়োটিন। অণুজীবরা এসব ভিটামিন আমাদের জন্যে তৈরি করে দেয়। একই সাথে আমরা যেসব জটিল পলিসেকারাইড খাই সেগুলো হজমে অণুজীব সাহায্য করে। আমাদের খাবারের ৩০% শক্তি আমরা অণুজীবের কারণে পাই।
এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। একটা প্রশ্ন তো হতেই পারে অণুজীবরা আমাদের শরীরে আসে কিভাবে? এরা আসে আমাদের মা থেকে। শিশু জন্মগ্রহণ করার সময় মা’র শরীর থেকে অণুজীব শিশুর কাছে চলে আসে। এখন শিশু যদি মায়ের জরায়ু পথে জন্মগ্রহণ করে তাহলে মায়ের জরায়ুতে যেসব অণুজীব আছে সেগুলো শিশুর শরীরে চলে আসবে। আর যদি সিজারের মাধ্যমে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে মায়ের শরীরের ত্বকে যেসব অণুজীব আছে সেগুলো শরীরে প্রবেশ করে। এখানে বলে রাখা দরকার জরায়ুর অণুজীব আর ত্বকের অণুজীব কিন্তু মোটেই এক নয়। আমাদের শরীরের এক এক জায়গায় এক এক ধরণের অণুজীব থাকে। এমনকি আমাদের দাঁতের মাড়িতে ২মি.মি. দূরত্বেও একই ধরণের অণুজীব পাওয়া যায় না।

আমাদের শরীরে বিভিন্ন জায়গায় কেবল বিভিন্ন ধরণের অণুজীব থাকে শুধু তাই কিন্তু না। প্রত্যেকটি মানুষের শরীরের অণুজীব বা microbiome আলাদা। এটা অনেকটা মানুষের আঙ্গুলের ছাপের মত! অদ্ভুত না! তো যেখানে ছিলাম মা থেকে শিশুতে অণুজীব প্রবেশ করে। তারপর যখন সন্তান মায়ের দুধপান করে তখন দুধ থেকে অণুজীব শিশুতে প্রবেশ করে। সেই অণুজীবের কাজ হচ্ছে দুধে যে সুগার থাকে সেটাকে হজমে সাহায্য করা। তারপর শিশু যখন খেলাধুলা করে, খাবার খায় তখন অণুজীবরা শিশুর দেহে প্রবেশ করে। এখন জানতে চাইতে পারেন এটা শিশুর জন্যে ক্ষতিকর কি না! না, এটা শিশুর জন্যে দরকার! অণুজীবরা যখন শিশুর শরীরে প্রবেশ করে তখন তারা একটা বিশাল কাজ করে। আমাদের শরীরের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা বাহির থেকে কোন কিছু প্রবেশ করলে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে আর তার একটা এন্টিবডি তৈরি করে রাখে। এভাবে অণুজীবরা শিশুর রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে তুলে! দেখা গেছে যেসব শিশু খুব বেশিমাত্রায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে থাকে তখন সে নানা ধরণের রোগে আক্রান্ত হয়ে পরে। তার মধ্যে আছে এজমা, ডায়েবেটিস। এধরণের পরিক্ষা ইঁদুরের উপর করা হয়েছে। দেখা গিয়েছে যেসব ইঁদুর জীবাণুমুক্ত পরিবেশে বড় করা হয়েছে সেগুলো ডায়েবেটিসে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু যেসব ইঁদুরকে নোংরা পরিবেশে বড় করা হয়েছে তাদের ডায়েবেটিস হয় নি। ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের শরীর অণুজীবদের সাথে থেকেই অভ্যস্ত। আমরা আর অণুজীবরা একই সাথেই বিবর্তিত হয়েছি।
একজন মানুষ মোটা আর একজন চিকন এখানে কি অণুজীবের হাত থাকতে পারে? বিজ্ঞানীরা বলছেন পারে। দেখা গেছে যেসব লোক মোটা তাদের শরীরে Firmicutes এর সংখ্যা Bacteroidetes থেকে অনেক বেশি। আর চিকন লোকদের দেহে Bacteroidetes এর সংখ্যা মোটা লোক থেকে বেশি। এখন যদি মোটা লোকটি ডায়েট করা শুরু করে তাহলে দেখা যায় তার শরীরে Bacteroidetes এর সংখ্যা বাড়ছে!

চিকিৎসার ক্ষেত্রে আরেকটি নতুন সংযোগ হলো Fecal transplantation। হা ঠিকই শুনেছেন। এক্ষেত্রে সুস্থ মানুষের মল অসুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করানো হয়। দেখা যায় যে অসুস্থ মানুষটি সুস্থ হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে Fecal transplantation এর মাধ্যমে অসুস্থ মানুষের microbiome এর ভারসাম্য ঠিক করা হয়। শুনতে খারাপ লাগলেও এটি চিকিৎসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হতে পারে।
আচ্ছা আমাদের মানসিক অবস্থার উপর কি অণুজীবদের হাত আছে? বিজ্ঞানীরা বলছেন আছে। আপনি হয়তো একটু আগেই কাউকে দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন কিন্তু এখন হয়তো বিরক্তি বোধ করছেন। এর পিছনে অণুজীবের হাত থাকতে পারে। বিজ্ঞানীরা একটি চিন্তাগ্রস্থ ইঁদুরের মল একটি সুস্থ ইঁদুরের অন্ত্রে প্রবেশ করিয়ে দেখেছেন সুস্থ ইঁদুরটিও চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও সত্য! অণুজীবরা ভেগাস নার্ভ আর স্পাইনাল কর্ডের মাধ্যমে ব্রেইনের কার্যকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে! তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অণুজীব দিয়ে মানুষের মানসিক অবস্থা পরিবর্তন সম্ভব। এই চিন্তা থেকে নতুন ধরণের একটি ওষুধের কথা ভাবা হচ্ছে। যার নাম ‘সাইকোবায়োটিক’। মানসিক অসুখের ক্ষেত্রে এ ওষুধটি ব্যবহার করা হবে। যদিও এ নিয়ে গবেষণা খুবই সাম্প্রতিক। আরও অনেক গবেষণার দরকার রয়েছে।
তাহলে দেখা যাচ্ছে অণুজীবরা আমাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের সব ধরণের কাজে অণুজীবের হাত আছে। তাই আমাদের নিজেদেরকে ভালোভাবে বোঝার জন্যে অণুজীবদের ভালোভাবে বোঝা প্রয়োজন। আমাদের নিজেদেরকে ভালোভাবে বোঝার জন্যে ১৯৯০ সালে শুরু হয়েছিল The Human Genome Project. কিন্তু বর্তমানে চলছে The Human Microbiome Project। Human Microbiome Project এর কাজ হলো আমাদের শরীরে যেসব অণুজীব আছে তাদের জিনোম সিকুয়েন্স বের করা। আমরা যদি তা জানতে পারি চিকিৎসাবিজ্ঞান এক অসীম উচ্চতায় আরোহণ করবে।
শেষ করছি Helicobacter pylori দিয়ে। Helicobacter pylori পেপটিক আলসারের জন্যে দায়ী। কিন্তু এর একটি বিশেষ দিকও রয়েছে। আমাদের পাকস্থলী দুই ধরণের হরমোন তৈরি করে। Ghrelin আর leptin. আমাদের খিদে লাগলে ghrelin ব্রেইনে নির্দেশ পাঠায় যে এখন খাওয়া দরকার। আর leptin নির্দেশ পাঠায় পাকস্থলী পূর্ণ হয়ে গিয়েছে আর খাওয়ার দরকার নেই। আর H. pylori ghrelin নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ খিদে নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা যদি H. pylori এর জন্যে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি তাহলে দেখা যাবে আমরা বেশি খাচ্ছি ফলে ওজন বেড়ে যাচ্ছে। কারণ যখন ghrelin কমে গিয়ে মস্তিস্কে নির্দেশ পাঠানোর কথা ছিল H. pylori না থাকার কারণে খিদে না থাকার পরও তার নিঃসরণ চলে। ফলে আমরা বেশি খাই এবং মোটা হয়ে পড়ি। অণুজীবরা নানাভাবে আমাদের উপকারে সর্বক্ষণ লেগে আছে। কিন্তু আমরা যেভাবে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে তাদের ধ্বংস করছি। এবার তারা যদি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন কি হবে?!
তথ্যসূত্রঃ
1. Meet your Microbe (https://www.youtube.com/watch?v=RVvNTCJE5oI)
2 .Microbiome – making better use of bacteria (https://www.youtube.com/watch?v=A-IqdPch9t0)
3. The invisible universe of human microbiome (https://www.youtube.com/watch?v=5DTrENdWvvM)
4. You are mainly Microbe – meet your microbiome (https://www.youtube.com/watch?v=4BZME8H7-KU)
5. The human microbiome and what we do to it (https://www.youtube.com/watch?v=EEZSuwkx7Ik)
6. Microbes, brain and behavior (https://www.youtube.com/watch?v=fRrje-F35A0)
7. The Ultimate Social Network by Jennifer Ackerman (Scientific American June 2012) এ অংশটুকু ভাবানুবাদকৃত।
* লেখাটি ই-ম্যাগাজিন বায়োজেনিতে প্রকাশিত

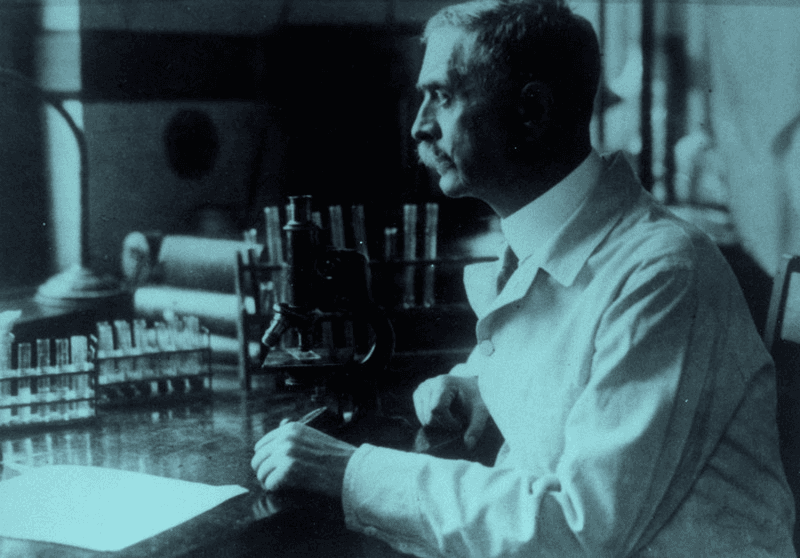






Leave a Reply