দীপেন ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন ধরে মৌলিক বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লিখে আসছেন। বাংলাভাষায় প্রতিবছর অনেকগুলো সাইফাই প্রকাশিত হয় একুশের বই মেলায়, মুহাম্মদ জাফর ইকবাল কিংবা হুমায়ুন আহমেদের মতো লেখক বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লিখে বহু খ্যাতি কুড়িয়েছেন। মূলধারার বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী একটা পরিচিত ছকের মধ্যে পড়ে গেছে বহু আগেই – গল্পের মধ্যে যে কোনভাবে রকেট, মহাকাশে ওয়ার্মহোল ভ্রমণ, ভিনগ্রহের প্রাণী, অতিরিক্ত-বুদ্ধিমান কম্পিউটার/রোবট, স্থান-কালের আপেক্ষিকতা ঢুকিয়ে দাও; ব্যাস, কল্পকাহিনী তৈরি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী প্রথমত: যে একটা “কাহিনী” যার একটা “প্লট” থাকবে; যার নায়ক-নায়িকারা মানুষ, সে মানুষের যে একটা সমাজ-প্রেক্ষিত আছে, সুতরাং বেশ কিছু পিছুটান ও দ্বন্দ্ব থাকবে; তারা একটা মানবিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে, সে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পাঠক নায়ক-নায়িকার চরিত্রের বিকাশ দেখবে; আর কল্পবিজ্ঞানের “কল্পিত-বৈজ্ঞানিক-ব্যাপার-স্যাপার” গাঁজাখুরী কোন আকাশ-কুসুম কল্পনা হবে না, কল্পিত বৈজ্ঞানিক উপাদান কাহিনীর সমাজ-বাস্তবতার সীমা হাস্যকর-ভাবে অতিক্রম করবে না – এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর প্রতি যথাযথ মনোযোগের অভাবে মূলধারায় সস্তা-ফ্যান্টাসির স্তর অতিক্রম করতে পেরেছে এরকম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী হাতে গোনা যাবে। এর কারণ হয়তো বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখাকে হালকা চালে নেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি, কিংবা দ্রুত পাঠকপ্রিয়তা অর্জন, অথবা বাণিজ্য। তবে দীপেন’দা বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী লেখাকে সহজ ভাবে নেন নি; তাঁর তিনটি উপন্যাস অভিজিৎ নক্ষত্রের আলো (২০০৬), দিতার ঘড়ি (২০১২) ও নক্ষত্রের ঝড় (২০১৫)-র পাঠ যে কোন বুদ্ধিদীপ্ত পাঠককে এ বার্তা পৌঁছিয়ে দেবে।

আমি তাঁর প্রথম উপন্যাস অভিজিৎ নক্ষত্রের আলো পড়ি সম্ভবত ২০০৬ কি ২০০৭ সালে। এর আগে তিনি একটি বিজ্ঞান-কল্প-গল্প সংকলন নিওলিথ স্বপ্ন (২০০২) প্রকাশ করেন। এছাড়াও তিনি বেশ কিছু বিজ্ঞান-ধর্মী ছোট-গল্প লিখেছেন যা অন্তর্জালে বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে [১]। এ পরিসংখ্যান অনুযায়ী তিনি লিখেছেন খুবই কম। সৌভাগ্যক্রমে আমি তাঁর সকল গল্পই পড়েছি – মৌলিক কল্পকাহিনী লেখার ক্ষেত্রে তিনি যে পথে এগিয়েছেন তা অভিনব ও মৌলিক। তাঁর বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে পদার্থ বিজ্ঞানের কোয়ান্টাম মেকানিক্স কিংবা সমান্তরাল মহাবিশ্বের মতো আধুনিক-পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব-নির্ভর ধারণাগুলো তিনি সফল ভাবে যুক্ত করেন; কিন্তু বিজ্ঞানের ঐ ধারণাগুলো তাঁর গল্পের ভরকেন্দ্র থাকে না, মূল আগ্রহের জায়গা হিসেবে পাঠক একটা নিটোল প্লট উপহার পান যেখানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-ধারণাগুলো ভিত্তি হিসেবে কাজ করে; এবং তাঁর উপন্যাস শেষ পর্যন্ত একটা কাহিনী থাকে না, পাঠকের কাছে সরবরাহ করে মানুষ, মানুষের সভ্যতা, তার সমাজ, ইতিহাস ও আগামী ভবিষ্যৎ বিষয়ক কিছু সুচিন্তিত ভাবনা। আমি সম্প্রতি তাঁর নক্ষত্রের ঝড় পড়লাম; আমার পাঠ প্রতিক্রিয়া এই লেখাতে উত্থাপন করছি।
নক্ষত্রের ঝড়
নক্ষত্রের ঝড় দু’মলাটের মাঝে বইরূপে প্রকাশের আগে মুক্তমনায় প্রকাশিত হয়েছিলো ভিন্ন শিরোনামে: ‘অদৃশ্য সমচ্ছেদ’। মুক্তমনার অনলাইন সংস্করণ থেকে কাহিনীর পরিসর বেড়েছে বইটিতে। উপন্যাসটির মূল প্লট কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট ধারণার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স আমি বুঝিনা খুব একটা, মোটা দাগে বলা যায় কোয়ান্টাম মেকানিক্সে মৌলিক বস্তু কণিকাগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে বলে ধারণা করা হয়। জোড়ার কণিকা একটি অপরটির সম্পূরক, একটির দশা পরিবর্তন হলে অপরটিও বদলে যাবে, কণিকা দুইটি কাছে বা বহুদূরে যেখানেই থাকুক না কেন। নিচের ছবিতে এ বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মাঝে একটা পার্থক্য হল সচেতনতার পর্যায়। আমরা যেভাবে উন্নত চিন্তা করতে পারি, কার্যকারণ বের করতে পারি, যুক্তি দিয়ে জাল বুনতে পারি – সেই পর্যায়ের সচেতনতা অন্যান্য প্রাণীদের নেই। এ বিষয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে, তবে সাধারণভাবে আমরা উপসংহার টানতে পারি এই বলে যে মানব-মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল-কর্টেক্স সুবিকশিত, এধরণের সুগঠিত ফ্রন্টাল-কর্টেক্স অন্য প্রাণীদের নেই। এ ফ্রন্টাল কর্টেক্সই মানুষের উন্নত চিন্তার জন্য দায়ী। মস্তিষ্কের যাবতীয় কার্যপ্রণালী একেবারে প্রাথমিক স্তরে স্নায়ুকোষের জটিল বিন্যাসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হবে। স্নায়ুকোষেরা তথ্য নিয়ে কাজ করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বৈদ্যুতিক বিভব পরিবর্তনের মাধ্যমে। লেখক কল্পনা করেছেন, মস্তিষ্কের এ স্নায়ু-জালিকার বিবিধ কর্মতৎপরতার কারণে একটি বিশেষ ক্ষেত্র তৈরি হয়। লেখক আরও ভেবেছেন যে মানুষের সচেতন চিন্তার ফলে যে “চিন্তা-ক্ষেত্র” তৈরি হয় তা অন্য ইতর-প্রাণীর মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ড হতে উৎপন্ন “চিন্তা-ক্ষেত্র” থেকে ভিন্ন হবে।
পরিশেষে লেখক একটি বিশেষ কোয়ান্টাম কণিকা-তরঙ্গের কথা ভেবেছেন, যারা সচেতন ও বুদ্ধিমান প্রাণীর চিন্তা-ক্ষেত্রের সাথে বিক্রিয়া করে, কিন্তু অন্য প্রাণীর চিন্তা-ক্ষেত্র এড়িয়ে যায়। ব্ল্যাকহোলের শক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম কোন বুদ্ধিমান প্রাণী এ তরঙ্গ ব্যবহার করে মহাবিশ্বে অন্য বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব খুঁজতে পারবে উল্লিখিত মূলনীতি ব্যবহার করে। এ তরঙ্গের মূল কাজ বুদ্ধিমান প্রাণীর খোঁজ করা হলেও সে মানুষের ক্ষণিক আনমনা-অবস্থার সুযোগ নিয়ে, কিংবা যখন তাকে অন্য কেউ দেখছে না, তখন তিন-মাত্রার জড়-কাঠামোর বর্তমান জগত থেকে হাওয়া করে ফেলে। “অন্য কারো পর্যবেক্ষণ” না থাকাটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুযায়ী একটি কোয়ান্টাম জগতে একটি কণা একই সাথে সকল অবস্থা বা দশায় থাকতে পারে এবং ফলে একটি তরঙ্গ-ধর্ম প্রদর্শন করে; কিন্তু যখনই তাকে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন সে সুনির্দিষ্ট একটি দশা বেছে নেয়।
২০৪১ সালে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ উপন্যাসে এমন একটি কোয়ান্টাম তরঙ্গ আছড়ে পড়তে দেখা যায়। ফলাফল: পৃথিবী জুড়ে অজস্র মানুষের হঠাৎ করে হারিয়ে যাওয়া। সৌভাগ্যক্রমে হোক কিংবা কাকতালীয়ভাবেই হোক, উপন্যাসের নায়ক অমলের মতো অনেকেই এ দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যায়। অমল ভীষণ অবাক হয় ঘটনার ঘনঘটায়, বুঝে ওঠার চেষ্টা করে আসলে কি হল। আমরা পাই একজন নিউরোসার্জন, যিনি ডাক্তার হলেও পদার্থবিদ্যায় উৎসাহী, ঘটনার কিছু কিছু কার্যকারণের ব্যাখ্যা দেন তিনি; দুর্ঘটনার হঠাৎ সুযোগ নিয়ে আগমন ঘটে একজন চোরের, যে পরবর্তীতে ঘটনার গুরুত্ব বুঝে যায় আর সবশেষে মহাকাশ থেকে বুদ্ধিমান প্রাণীর আগমন ঘটে; পৃথিবীর মানব প্রজাতির কাছে ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে, কারণ সচেতন-বুদ্ধিমান প্রাণী খোঁজা তাঁদের উদ্দেশ্য হলেও তাদের পাঠানো সন্ধানী তরঙ্গ যে এসব প্রাণীদের অদৃশ্য করে দেয়ার উদ্দেশ্য ছিলও না — তারা স্বীকার করে এটা তাদের ভুল ছিল। তারা ব্যাখ্যা করে তাদের নিজেদের সভ্যতার বিবর্তন, উন্নতির শিখরে পৌঁছানোর গল্প; নিজেদের দায় স্বীকার শেষ হলে তারা চলে যায় অন্য কোন গ্রহে, যেখান সন্ধানী তরঙ্গ অন্য বুদ্ধিমান প্রাণীদের হাওয়া করে দিচ্ছে। উপন্যাসের শেষে নায়ক বুঝতে পারে অজস্র শিশু সন্তান এ তরঙ্গ থেকে বেঁচে গেছে, কারণ শিশুদের নিওকর্টেক্স তেমন সুগঠিত নয়, তাদের সচেতন-ক্ষেত্রের স্তরও তাই উন্নত নয়; নায়ক উপলব্ধি করে তাদের হাতে এখন অনেক কাজ, পৃথিবীটাকে নতুন করে গড়তে হবে বেঁচে যাওয়া অন্যদের সাথে নিয়ে।
কিন্তু ভিনগ্রহের উন্নত প্রাণীরা কেন আরেকটি গ্রহ খুঁজতে বেরুলো যেখানে বুদ্ধিমান প্রাণী আছে? কাহিনী-অনুসারে ভিনগ্রহের প্রাণীরা আদিতে আমাদের মতো জৈব পদার্থে তৈরি হলেও তাদের প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে তারা নিজের দেহ এমনকি মস্তিষ্ককেও অজৈব বস্তু দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে যান্ত্রিক কিন্তু দীর্ঘ জীবন-যাপন করতে সমর্থ হয়। এ বিষয়টি অতিকল্পনা বলে মনে হয় না, কারণ এখনিই বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম অঙ্গ (প্রস্থেটিক লিম্ব) তৈরি করে ফেলেছেন পঙ্গুদের জন্য যাকে মস্তিষ্কের নির্দেশে পরিচালনা করা সম্ভব। অজৈব-দেহ-কাঠামো কিন্তু সচেতন ও বুদ্ধিমান – এরকম হাইব্রিড অস্তিত্বের ভিনগ্রহ-বাসীর একটি জটিল সংকটে পড়ে। তারা ব্ল্যাকহোলের শক্তি ব্যবহার করতে পারে, তারা বহু শতাব্দী বেঁচে থাকতে পারে, তারা এক সৌরজগত থেকে অন্য সৌরজগতে ভ্রমণ করতে পারে – কিন্তু তাদের কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তার ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে, এক সময় তাদের সমাজ এমন একটি অবস্থায় আসে যখন তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-প্রযুক্তি আর অগ্রসর হয় না। তখন তারা বুঝতে পারে তাদের হাইব্রিড অস্তিত্বের সংকট, তাদের যান্ত্রিক মস্তিষ্কের সীমাবদ্ধতা। এ অবস্থান থেকে তাদের বহির্বিশ্বে ভিন্ন বুদ্ধিমান অস্তিত্বের খোঁজ শুরু হয়, যা পৃথিবীতে তৈরি করে আরেক সংকট।
কিছু বৈশিষ্ট্য
এবার সংক্ষেপে আমার চোখে পড়া উপন্যাসটির কিছু ক্ষুদ্র কিন্তু উল্লেখযোগ্য দিকের কথা বলি।
- গদ্যশৈলী। প্রতিটা বাক্য অত্যন্ত যত্ন নিয়ে লেখা, সুগঠিত। শব্দের যথার্থ ব্যবহার। বাংলা ভাষা শব্দসম্ভারে অনেক সমৃদ্ধশালী, কিন্তু সচরাচর সেগুলো ব্যবহৃত হয় না। অনেক সময় কেউ ব্যবহার করলেও যথার্থ ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করাতে ভাষাটা প্রাচীন, মান্ধাতার আমলের কিংবা গুরুচণ্ডালী দোষে-দুষ্ট মনে হয়। কিন্তু লেখক সফলভাবে শব্দের বৈচিত্র্য নিয়ে খেলেছেন বইটিতে। শুধু শব্দ বা বাক্য-পর্যায় না – বিভিন্ন বর্ণনা লেখক সাবলীলভাবে বিস্তৃত করেছেন। পাঠকের মনে বর্ণনাগুলো বিস্তারিত ছবি ফুটিয়ে তোলে।
- সর্বত্র বাংলা ব্যবহারের প্রতি স্পষ্ট পক্ষপাত। বর্তমানে আমরা ভাষা আন্দোলন, একুশে ফেব্রুয়ারি ইত্যাদি নিয়ে অনেক অহংকার করলেও দোকানের নাম থেকে শুরু করে টেলিভিশন চ্যানেল কিংবা সংগঠন/সংস্থার নাম ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইংরেজি ব্যবহার করি। কিন্তু লেখক যেখানে যেখানে সম্ভব বাংলা ব্যবহার করেছেন। যেমন টেলিভিশন চ্যানেলের নাম ‘মহাবিশ্ব’ (পৃঃ ১৫)।
- উপন্যাসের প্লট নির্মানের খুঁটিনাটির ক্ষেত্রে লেখক যথাসম্ভব বাস্তব তথ্য ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসের একটি চরিত্র রামু মাসিক যে পত্রিকায় (মাসিক বসুমতী, পৃঃ ২১) লিখত, তা সত্যিই ছিলও! আমাদের বাসায় মাসিক বসুমতীর একটা সংকলন ছিলও – পত্রিকাটা চল্লিশের দশকের হলেও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে সেখানে বিজ্ঞানের একটা ছবিওয়ালা বিভাগ ছিল।
- উপন্যাসটা ভবিষ্যতের গল্প বলতে গিয়ে আকাশ-কুসুম কল্পনা করে নি, ভবিষ্যতের চিত্র আঁকতে গিয়ে লেখক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়কে মাথায় রেখেছেন। যেমন পরিবেশ বিপর্যয়। এটা পরিষ্কার সময়ের সাথে সাথে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়ছে, ঘনিয়ে আসছে পরিবেশ বিপর্যয়। নিকট ভবিষ্যতে গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ভাবনাটা তাই বারবার উঠে এসেছে উপন্যাসে, লেখক বলেছেন সুন্দরবনে জল উঠে যাওয়ার কথা (পৃঃ ৩৭)। উল্লেখ্য বাংলাদেশের উপর পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রভাব ঠিক কি হবে তা নিয়ে লেখকের কিছু গবেষণা আছে [২, ৩, ৪], তিনি অনুসন্ধিৎসু চক্রের আয়োজনে বিজ্ঞান সেমিনারেও গণ-বক্তৃতা দিয়েছেন এ বিষয়ে। এছাড়াও জনসংখ্যা বিস্ফোরণের প্রভাব ঢাকা শহরের উপর কিভাবে পড়বে তা নিয়েও লেখক কিছু চিন্তা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন এমন এক ঢাকা শহর, যেখানে জনসংখ্যার চাপ এতোটাই বেশি, যে অর্ধেক মানুষ দিনে কাজ করে আর বাকিরা রাত্রের শিফটে কাজ করে (পৃঃ ১৭, ১৮)।
- লেখক মূল গল্পের প্লট নির্মাণের জন্য বেশ কিছু ছোট ছোট বর্ণনা তৈরি করেছেন বিভিন্ন ব্যক্তি ও ঘটনা নিয়ে। যেমন উড়োজাহাজ বা রেলগাড়ি থেকে মানুষের উধাও হয়ে যাওয়া (পৃঃ ৭ – ১৬), চা-বিক্রেতা রামুর লেখক হয়ে ওঠা (পৃঃ ২০-২১)। এর পাশাপাশি কিছু বিচ্ছিন্ন অণু গল্পেরও সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন অমলের রংপুর-নিবাসী জমিদার প্রমাতামহী, যিনি এমন একটি তারা চিনতেন যা মানুষের কাছে অজানা ছিলও (পৃঃ ৪১)। আসলে বর্তমানের গতির মধ্যে দিন-যাপনের ফাঁকতালে বিভিন্ন স্মৃতি, ছোট ছোট উপলব্ধি, অনুভব আমাদের অন্যমনস্ক করে দেয়। এ অণু-কাহিনীগুলো পুরো উপন্যাসের মধ্যে সেরকম একটি আবহ তৈরি করেছে।
- উপন্যাসটির কাহিনীতে বেশ কিছু জায়গায় লেখক টানাপোড়নের একটা অনুভূতি তৈরি করতে পেরেছেন। যেমন অমলকে দেখে পোষা দেশি নেড়ি কুকুর কানুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠা, প্রতিবেশী ফারহানার দরজা না খোলা, ভিনগ্রহের প্রাণীর পৃথিবীতে নেমে আসা, কিংবা ঢাকার রাস্তায় আমলদের দলকে সামরিক ট্যাঙ্কের হঠাৎ আক্রমণ (পৃঃ ৩০, ৩৮, ৬৬, ৯৮)। যে অমল যখন অন্যমনস্ক ছিলও, তখন সন্ধানী তরঙ্গের বিক্রিয়ায় সে অদৃশ্য হতে শুরু করে ও ফলাফলে চেহারা বদলে যায়। তাই ফারহানা চিনতে না পেরে দরজা খুলে নি, কানুও প্রথমে ঘেউ ঘেউ করে উঠেছে। তবে আমরা জানি কুকুর তো দৃষ্টির চাইতে ঘ্রাণ শক্তির উপর বেশি নির্ভরশীল চারপাশের জগত চেনার জন্য। তাই খটকা লাগে কানু কেন ঘেউ ঘেউ করে উঠলো? নাকি অমলের গন্ধও বদলে গেছে সন্ধানী তরঙ্গের সাথে বিক্রিয়া করে? এই সব ছোটখাটো বাস্তবতার বিস্তার ঘটিয়েছেন লেখক অত্যন্ত যত্ন সহকারে। তাই উপন্যাসটি পাঠের অভিজ্ঞতা বেশ সমৃদ্ধ ও বহুমাত্রিক লাগে আমার কাছে।
- উপন্যাসের কয়েক জায়গায় লেখক আধুনিক বাংলা গান এনেছেন। ভাবতে ভালো লাগে ২০৪১ সালেও মানুষ হেমন্তের গান শুনবে। গানের কথাগুলো উপন্যাসের প্রেক্ষিতে দার্শনিক মনে হয়। যেমন: “পৃথিবীর গান আকাশ কি মনে রাখে?/ নীরব সুরের রামধনু শুধু দিগন্তে ছবি আঁকে।” ভাবনা জাগে, পৃথিবীর ছোট ভূখণ্ডে আমাদের এতো সাধ-আহ্লাদ, জীবিকার লড়াই, সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ – এতে মহাবিশ্বের কি এসে যায়?
মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব – রূপকথা না বাস্তবতা?
কল্পকাহিনীটির একটি প্রশ্ন হচ্ছে অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠতার ধারণা। মানুষই সৃষ্টির সেরা, তাদের সেরেব্রাল কর্টেক্স সুবিকশিত, তাই মানুষ বুদ্ধিমান, উন্নত চেতনার অধিকারী – আমরা এরকমটাই সচরাচর ভেবে অভ্যস্ত। তবে উপন্যাসে দেখা যায় মানুষের চেয়েও প্রযুক্তিতে উন্নত বুদ্ধিমান প্রাণীর আগমন। এখান থেকে একটি প্রশ্ন আরোপ করি, ‘মানুষ সৃষ্টির সেরা’ এ দৃষ্টিভঙ্গি কি সঠিক? এ দৃষ্টিভঙ্গির একটা সমস্যা হল এ অনুযায়ী সবাই ধরে নেয় মহাবিশ্বের শুরু থেকে শুরু করে সৌরজগত ও পৃথিবীর উৎপত্তি, পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ ও বিবর্তনের চূড়ান্ত ও পরম পরিণতি হল মানুষ। মানুষের মাঝেই প্রকৃতির চরম উৎকর্ষ সাধন হয়েছে। কিন্তু এটা অত্যন্ত ভুল একটি ভাবনা। আসলে আমরা মানুষ যেহেতু জ্ঞানচর্চা করি, তাই পৃথিবী ও প্রাণের ইতিহাসকে আমরা মানুষকে কেন্দ্রে রেখে বর্ণনা করি, তাই সবসময় একটি পক্ষপাত আমাদের মাঝে থাকে। কিন্তু এরকম দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নাও হতে পারে। আমরা আসলে প্রকৃতির একটি অংশ মাত্র। মানুষের বিবর্তন থেমে যায় নি, যেমন থেমে যায়নি অন্যান্য অজস্র জীবপ্রজাতির বিবর্তন। প্রাণ-বৃক্ষের একটি ডালের মাঝে একটি পাতায় অবস্থান আমাদের প্রজাতির। এরকম অজস্র পাতা রয়েছে এই জীবন-বৃক্ষে। আমরা যে এই বৃক্ষের মগডালে অবস্থান করছি এমন দাবীও আমরা করতে পারি না। মেরুদণ্ডী প্রাণী হয়ে স্তন্যপায়ী সেখান থেকে প্রাইমেট হয়ে মানুষ – এই বংশগতির ইতিহাস জীবন-বৃক্ষের যে শাখা-প্রশাখার পথ বেয়ে শিকড় পর্যন্ত পৌঁছেছে সে পথও সবচেয়ে মোটা নয় (মোটা বলতে যদি প্রজাতির বৈচিত্র্য অথবা জনসংখ্যা বোঝাই)। বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ সাময়িকী নেচার-এর দীর্ঘদিন জীবাশ্ম-বিদ্যার সম্পাদক থাকা হেনরি জি তাঁর দ্যা এক্সিডেন্টাল স্পিশিস (২০১৩) বইটিতে এই মানব-কেন্দ্রিক বয়ানের বিপক্ষে যুক্তি দিয়েছে, এ ধরনের মানবকেন্দ্রীক ভাবনা আসলে বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণার বহিঃপ্রকাশ। অন্যান্য প্রাণী থেকে আমরা নিজেদের আলাদাভাবে দেখি যে সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য, তা আসলে অজস্র বিবর্তনীয় সম্ভাবনার মধ্যে একটি পথ মাত্র। আয়না-পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা যায় এ প্রসঙ্গে। একটি মানব-শিশুকে আয়নার সামনে নিয়ে এলে সে নিজেকে চিনতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, অন্যান্য এপ-শাবকদের মধ্যেও এ বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায়। কিন্তু কুকুর-ছানারা আয়না-পরীক্ষায় তেমন কোন সাড়া দেয় না। যদি এধরনের পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে ‘স্ব-সচেতনতা’, কিংবা ‘আমিত্ব’ বিবর্তনের ফলে কেবলমাত্র এপ ও মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়েছে তাহলে সেটা ভুল হবে। কারণ অন্য গবেষণায় দেখা গেছে কুকুর-গোত্রীয় প্রাণীরা গন্ধের সাহায্য নেয় নিজেদের চিনতে। এমনকি তাঁরা নিজস্ব মল-মূত্র দিয়ে নিজেদের এলাকার সীমানাও ঠিক করে দেয়। তাদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। তাই তাদের মস্তিষ্কে বাস্তবতার-পুনর্নির্মাণ মানুষের পুনর্নির্মাণ থেকে ভিন্ন হবে। তারা চারপাশের পৃথিবীকে ঘ্রাণের যে বৈচিত্র্যের মাধ্যমে পুনর্নির্মাণ করে তা আমাদের কাছে শুধু অপরিচিতই নয়, হয়তো কখনোই আমরা সে বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবো না। একই ধরনের উপপত্তি টানা যায় অন্যান্য ইন্দ্রিয় কিংবা প্রাণীর-বাস্তবতার ক্ষেত্রে। মানব-কেন্দ্রিক জগত-বাস্তবতা আমরা সত্য বলে ধরে নিলেও ভিন্ন-বাস্তবতার অস্তিত্বের কথা মাথায় রাখতে পারি আমরা।
চিন্তক-যন্ত্রের উৎপত্তি
বইয়ের প্রচ্ছদে দেখা যায় একটি রোবটকে অগাস্ট রোদিন-এর ভাস্কর্য “দি থিংকার” এর আদলে ভাবনারত। সচেতন চিন্তক-যন্ত্রের উৎপত্তি এ কল্পকাহিনীর একটা আগ্রহের জায়গা। কাহিনীর শেষ পর্যায়ের দিকে সন্ধানী তরঙ্গ পাঠানো ভিনগ্রহের প্রাণী নিজেদের গল্প বলার সময় বর্ণনা করে কিভাবে তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে বুদ্ধিমান প্রাণী থেকে একধরনের চিন্তক যন্ত্রে রূপান্তরিত হল। এটা আসলেই এমন একটি বিষয় যা বহু চিন্তার খোরাক দিতে পারে। গণকযন্ত্র কম্পিউটারে সুনির্দিষ্টভাবে প্রোগ্রাম লিখে দিলে তা ঐ কাজ বারবার করে কোন ভুল-ত্রুটি ছাড়াই। তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণার এক পর্যায়ে মেশিন লার্নিং বা যন্ত্র-শিক্ষণের উৎপত্তি হওয়ার সাথে সাথে এমন প্রকারের প্রোগ্রাম লেখা সম্ভব হল যে গণক-যন্ত্রকে একগোছা পূর্বপ্রস্তুতি উপাত্তের সাহায্যে প্রশিক্ষণ দেয়া গেল; যার ফলে ঐ প্রোগ্রাম অন্য উপাত্তের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এখন মেশিন লার্নিং ব্যবহৃত হচ্ছে গুগলের পেজ র্যাঙ্ক অ্যালগরিদমের মাধ্যমে সার্চ ইঞ্জিন থেকে শুরু করে ফেসবুকের স্ব-শাসিত প্রক্রিয়ায় ছবি-চিনে ব্যবহারকারী দাগানো (ট্যাগিং) কিংবা স্মার্ট ফোনের বুদ্ধিমান সহচারী (আইফোনের সিরি, যার সাথে কথা বলা যায়)। কৃত্রিম আত্মসচেতন প্রোগ্রাম কিংবা রোবট তৈরি নিয়েও কাজ চলছে। ভাবনার বিষয় হল, মানুষের সভ্যতায় কি ইতিমধ্যে চিন্তক-যন্ত্রের উদ্ভব হয়ে গেছে? আমরা কি বলবো কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তা কিংবা যন্ত্র-শিক্ষন এলগরিদমগুলো গণকযন্ত্রকে ভাবতে শেখায়? বড় বড় ডাটা সেন্টারগুলো যখন অজস্র সার্ভার নোডের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে ইন্টারনেট গঠন করে, তখন কি তার মধ্যে অজস্র কম্পিউটার প্রোগ্রামের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে কোন সচেতনতা তৈরি হয়? এগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যা এই কল্পকাহিনী পড়ে মনের মাঝে উদয় হয়। এ কাহিনীতে বুদ্ধিমান প্রাণীরা নিজেদেরকে ক্রমেই বুদ্ধিমান যন্ত্রসত্ত্বায় পরিণত করে ফেলে। অজস্র গ্যাজেট ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে কি একই পথেই পরিচালিত করছি না?
সভ্যতার ধ্বংস-গল্প
কাহিনী অনুযায়ী নক্ষত্রের ঝড় ‘সভ্যতার ধ্বংস-গল্প’ গোত্রের মধ্যে পড়ে, কারণ বুদ্ধিমান ভিনগ্রহ-বাসীর পাঠানো সন্ধানী তরঙ্গে মানবজাতির অধিকাংশই হারিয়ে যায় – হয়তো ভিন্ন কোন মাত্রায় অথবা সমান্তরাল জগতে। নিজেদের তৈরি সভ্যতা কিভাবে ধ্বংস হবে তা নিয়ে মানুষ অনেক আগে থেকে ভেবে এসেছে, এ ধরনের গল্প বলা হয়েছে বহুবার – ধর্মে, লোককথায়, কল্পকাহিনীতে। হালের হলিউড-কাঁপানো নোলানের ইন্টারস্টেলার (২০১৪) চলচিত্রটিও এই ঘরানার – কিংবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে সভ্যতার ধ্বংস পরবর্তী টিকে থাকা মানুষের ভিন্ন কোন সৌরজগতে বেঁচে থাকার স্থান খোঁজার ছায়াছবি। এই বইটি পড়ে যখন ইন্টারস্টেলার ছবিটি দেখি – দুই অভিজ্ঞতাই আমার খুব কাছাকাছি ও তুলনীয় মনে হয়েছিলো। কারণ সম্ভবত বই ও ছায়াছবিটির অন্তর্নিহিত সৌষ্ঠব; কল্পনাকে বাস্তব করে তুলে ও পাঠক/দর্শককে ধরে রাখার গুণ। বইয়ে বলা কিংবা চলচ্চিত্রে দেখানো কাহিনী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সহজপাচ্য বিনোদন দিতে গিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে না। আর সহজপাচ্য বিনোদনের গন্ডীর বাইরে আসতে চাইলেও জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো ও দ্বন্দ্ব-টানাপোড়নের সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যের অভাবে অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে যায়। এটাই সম্ভবত বড় শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য – আরেকটি কল্পনার জগতে মানুষের দ্বন্দ্ব, সীমাবদ্ধতা, দায়বোধ ইত্যাদি টানাপোড়ন নিটোল-বাস্তব করে তোলার জাদুকরী ক্ষমতা।
সূত্র:
[১] Dipen Bhattacharya’s Blog. http://randomworldtravel.com/
[২] The Response of Bangladesh and Ganges-Brahmaputra Delta to Sea Level Rise. D Bhattacharya and W. Fraczek http://randomworldtravel.com/?page_id=179
[৩] Climate Change Effects in the Deltaic Environment of Bangladesh. D. Bhattacharya. Climate Change and the Tasks for Bangladesh. 2009. http://randomworldtravel.com/?page_id=151
[৪] বিশ্ব উষ্ণায়ন ও বাংলাদেশ। দীপেন ভট্টাচার্য। পড়শী, মে-জুন ২০০৯। http://www.porshi.com/_arc_news_details.php?nid=77&rd=y&did=4
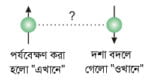
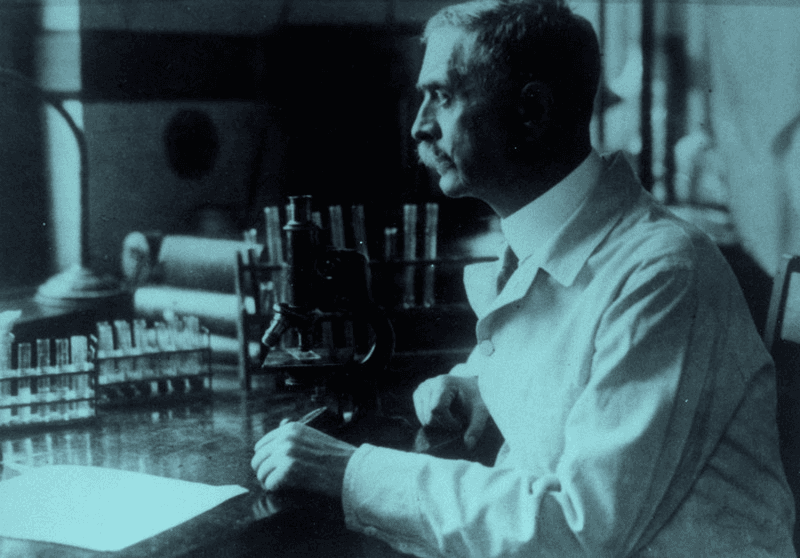


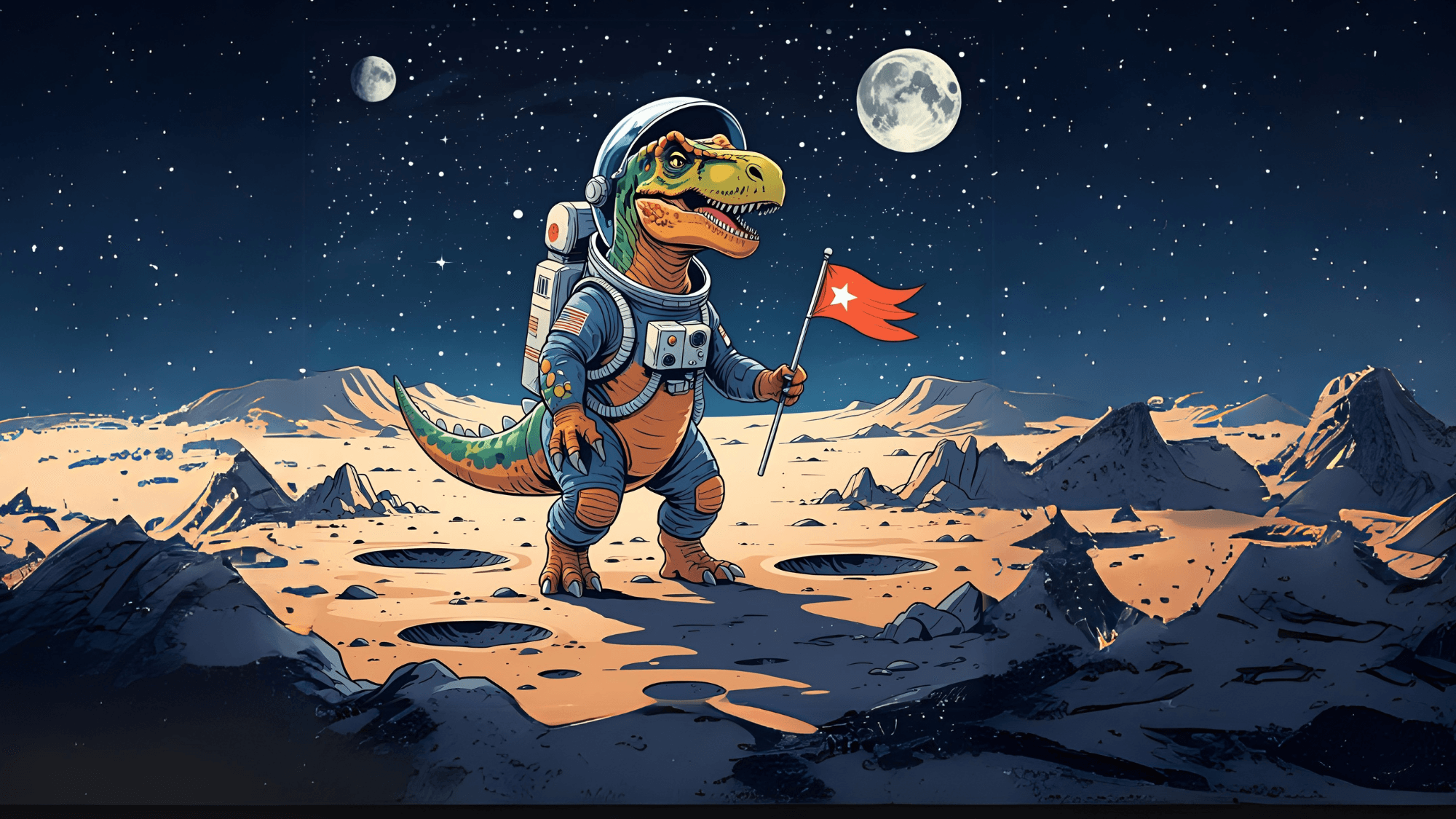
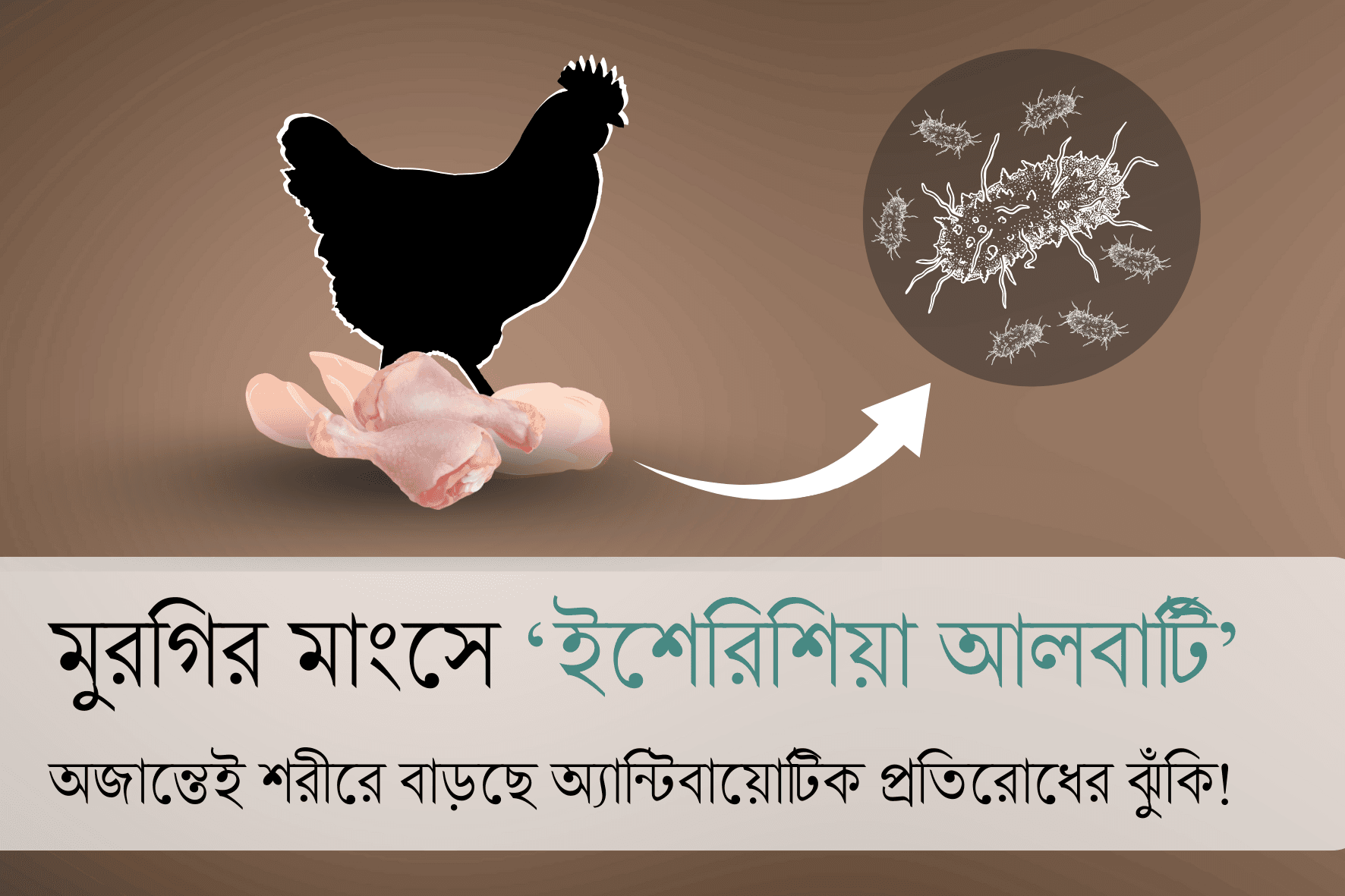


Leave a Reply