বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের কোন এক গরুর খামারের তিনটি গরুর (ডাংকি, মংকি এবং চাংকি) মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল-
ডাংকিঃ কিরে মংকি উপরে তাকায়ে কি দেখিস?
মংকিঃ দেখ, আজকে আকাশে কত তাঁরা উঠছে। কত সুন্দর তাই না?
ডাংকিঃ আ্যহ! এই দিনের বেলা তুই তাঁরা পাইলি কই? তোর উপর কি পাগলা গরুর ভুত ভর করলো নাকি!
চাংকিঃ ঐ ডাংকি দেখ, ঐখানে একটা গরু নিজের মাথা নিজেই দেয়ালে ঠুকতেছে। আমারও কেমন জানি ওর মতো করতে ইচ্ছা করতেছে।
ডাংকিঃ কি জানি ভাই, তোগোর কাহিনি তো আমার কিছুই ভালো লাগতাছে না। আমি শুনছি পাগলা গরু নামের কি এক ভুত নাকি আসছে, সুযোগ পাইলেই নাকি গরুর উপর ভর করতেছে। এখন তো দেখি ঘটনা আসলেই সত্যি।
চাংকিঃ কি যে কইতাছস ব্যাট্টা, আরে আমাগো ভয় কিসের, আমরা কি গরু নাকি যে ঐ গরুর ভুত আমাগো ধরবো। আমরা তো ভাল্লুক, ভাল্লুকের আবার গরুর ভুতে ধরে নাকি?
ডাংকিঃ আ্যহ! সব গুলারেই তো ধরছে দেখি। ভালোয় ভালোয় কেটে পরি। পালাও, পালাও…..ভুত, ভুত, পাগলা গরুর ভুত আসছে।
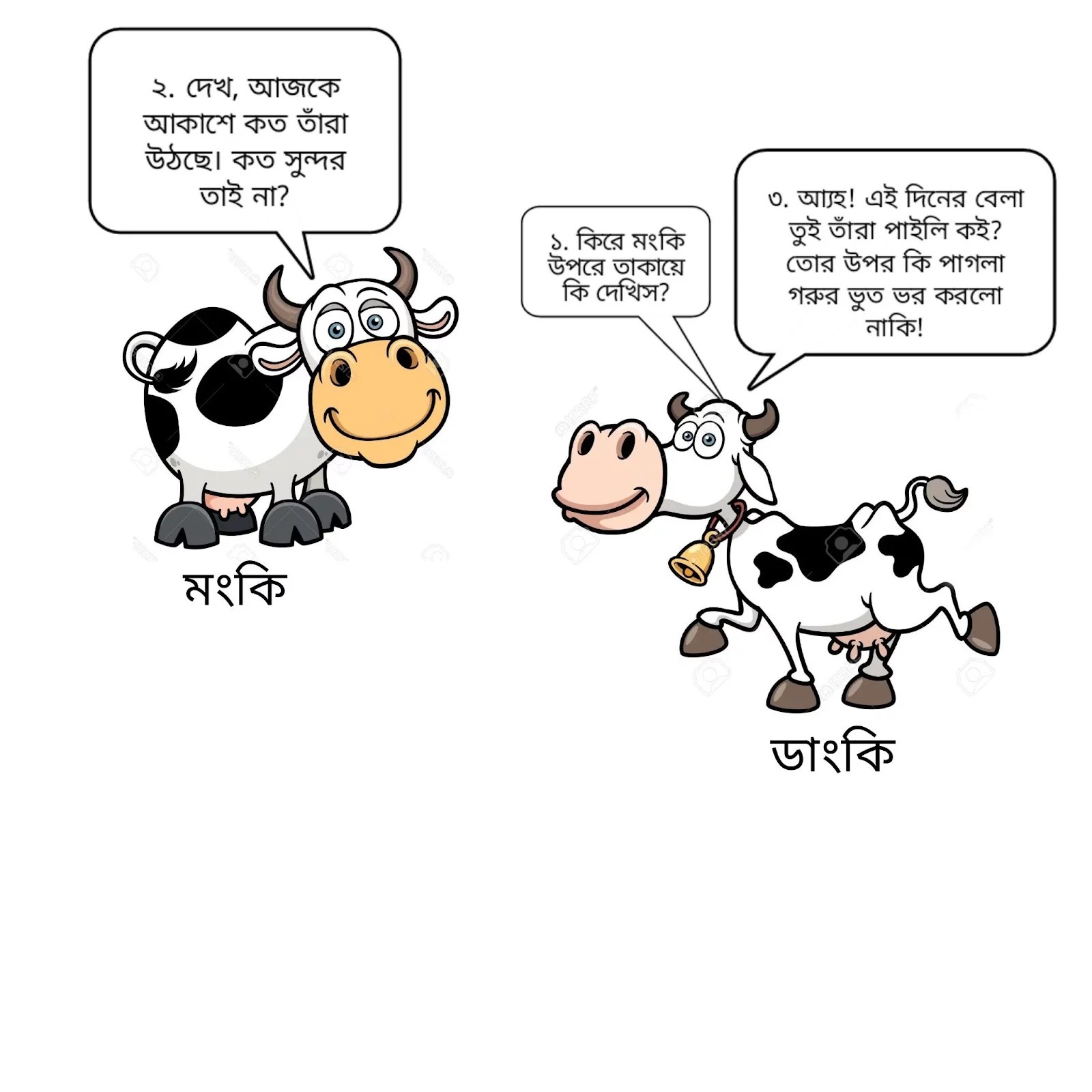
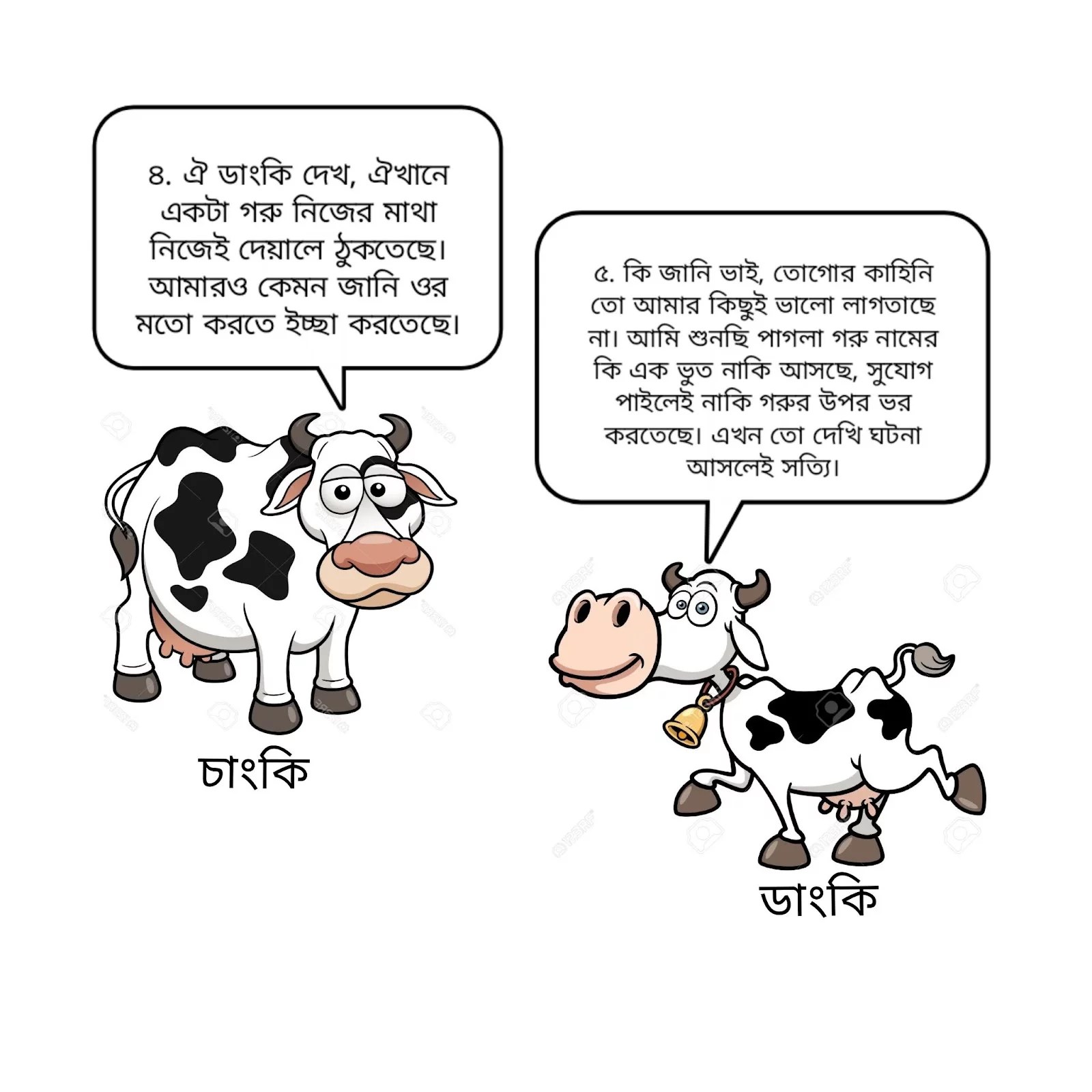
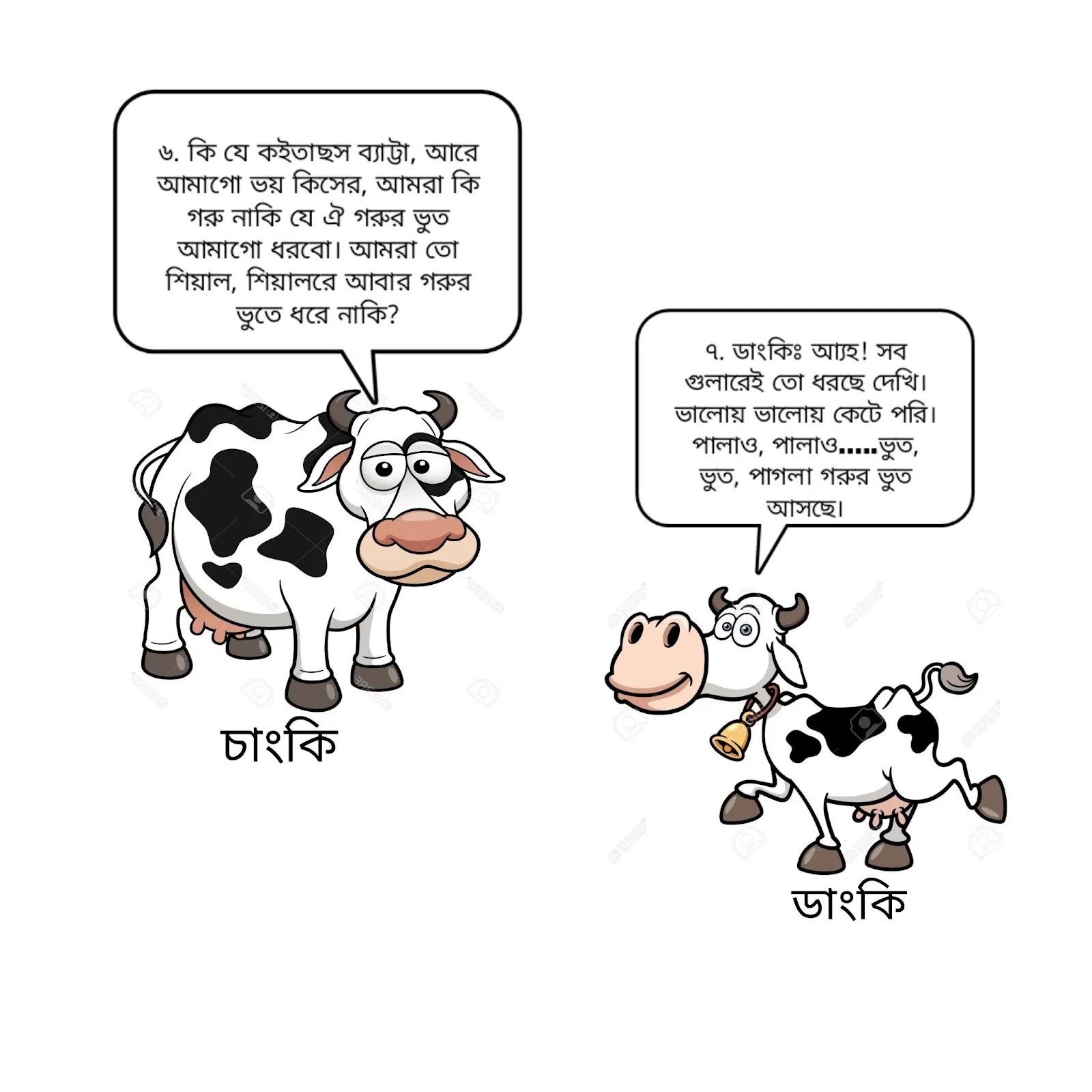
উপরের কথোপকথনটি কাল্পনিক হলেও বিংশ শতাব্দীর শেষের দশকে যুক্তরাষ্ট্রের গরুর খামার গুলোতে আজানা কারনে গরুর মধ্যে অস্বাভাবিক, পাগলের ন্যায় আচরণ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে আমেরিকান নিউরোলজিস্ট এবং প্রানরসায়নবিদ স্ট্যানলি বেনজামিন প্রোসিনার প্রিয়ন নামক সংক্রমণকারী একধরনের প্রোটিনের কথা উল্লেখ করেন যা এই ধরনের রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। এই রোগকে ম্যাড কাউ ডিজিজ বা পাগলা গরু রোগ নামে অবিহিত করা হয়। এবার আমরা প্রিয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো।
প্রিয়ন হচ্ছে একপ্রকার সংক্রমণকারী প্রোটিন কনা যা মস্তিষ্কের ক্ষয় জনিত স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতার জন্য দায়ী। প্রিয়ন কোনো ডিএনএ বা আরএনএ বহন করে না, কিন্তু এরা নিজেদের প্রতিরূপ তৈরি করতে সক্ষম [1]। সংক্রমণকারী এই প্রিয়ন প্রোটিন সমূহ স্নায়ুকোষের ভিতর জমা হয়ে স্বাভাবিক প্রোটিনগুলোকে এমাইলয়েড তন্তুতে পরিণত করে। এমাইলয়েড তন্তু কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষয় করতে সাহায্য করে। যার ফলে পুরো টিস্যুটি স্পঞ্জের ন্যায় বিকৃত রূপ নেয় এবং স্নায়ুকোষে ছোট ছোট গহ্বর তৈরি হয়। এ রোগটির সুপ্তাবস্থায় প্রায় পাঁচ থেকে দশ বছর থাকতে পারে। যদিও একবার রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে তা খুব দ্রুত মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে [2]।

একটা সময় বিজ্ঞান মহল এ বিষয়ে সন্দিহান ছিল যে কিভাবে বংশগতির বৈশিষ্ট্যগত তথ্য বংশধরদের মধ্যে প্রবাহিত হয়। ১৯২৮ সালে ব্রিটিশ ব্যাকটেরিওলজিস্ট (ব্যাকটেরিয়াবিদ) ফ্রেডরিক গ্রিফ্থ তার গবেষণার মাধ্যমে দেখান যে ব্যাকটেরিয়া নিজেদের মধ্যে বংশগতির তথ্য স্থানান্তর করতে পারে [3]। তখন সবাই এটা বিশ্বাস করতো যে দেহের প্রোটিনসমূহ বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করে। কিন্তু ১৯৪৪ সালে এ ধারনা ভুল প্রমাণ করেন কয়েকজন বিজ্ঞানী তাদের সম্মিলিত গবেষণার মাধ্যমে। আর তারা হলেন ওসওয়াল্ড অ্যাভেরী, কোলিন ম্যাকলিড এবং ম্যাকলিন ম্যাককার্ট। তারা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখান যে প্রোটিন নয় বরং ডিএনএ বংশগতির তথ্য বহন করে [4]।
এ থেকে বিজ্ঞানমহলে এধারনা বদ্ধমূল হয় যে, যেকোনো রোগসংক্রমণকারী বস্তু বা কনা (ভাইরাস বা ব্যক্টেরিয়া) অবশ্যই ডিএনএ বা আরএনএ বহন করবে। কিন্তু পরবর্তীতে সবাইকে অবাক করে দিয়ে ১৯৮২ সালে স্টেন্ডলি বেনজামিন প্রোসিনার একধরনের সংক্রমণকারী প্রোটিনের কথা উল্লেখ করেন।এই প্রোটিন কোনো প্রকার ডিএনএ অথবা আরএনএ বহন করে না, তবুও এরা নিজের প্রতিরুপ তৈরি করতে সক্ষম। এই সংক্রামনকারী প্রোটিনের নাম দেয়া হয় প্রিয়ন, যা সাধারণত স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা বা রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। যেমনঃ গবাদি পশুর ম্যাড কাউ রোগ, স্ক্রেপি, এবং মানুষের জার্সটম্যান স্ট্রাউসলার স্কেইনকার সিন্ড্রোম, কুরু, ক্রিউট্জফিল্ড জেকব ইত্যাদি [5-8]। এর জন্য স্ট্যানলি বেনজামিন প্রোসিনার ১৯৯৭ সালে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন।

প্রিয়নের উৎপত্তি
এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোথায় থাকে এই প্রিয়ন বা কোথায় এর উৎপত্তি?
সাধারণত প্রিয়ন প্রোটিন প্রানীর দেহে প্রাকৃতিকভাবেই থাকে। পিআরএন(Prn) জিন থেকে ট্রান্সলেশন এর মাধ্যমে প্রিয়ন প্রোটিন (Prnp) তৈরি হয়ে থাকে। যে সকল প্রিয়ন প্রোটিন আমাদের দেহে স্বাভাবিকভাবেই থাকে তাদেরকে পিআরএনসি (Prnc) বলা হয়। অন্যদিকে যেসকল প্রিয়ন প্রোটিন আমাদের দেহে সংক্রমক রোগ সৃষ্টি করে, তাদেরকে পিআরএনএসসি (Prnsc) বলা হয়। পিআরএনএসসি (Prnsc) প্রোটিন গুলো তৈরি হয় মূলত কোষের স্বাভাবিক পিআরএনসি (Prnc) প্রোটিন তৈরি হওয়ার সয়মভাঁজগত ত্রুটির (Misfold) কারনে। অর্থাৎ পিআরএন (Prn) জিন থেকে ট্রান্সলেশনের পর যে অ্যামাইনো এসিডের চেইন তৈরি হয়, তা স্বাভাবিক ভাবে ভাঁজ হয়ে যেইরুপ কুন্ডলী পাকায়, তা না করে ভিন্ন ধরনের কুন্ডলী তৈরি করে। সাধারণত পিআরএনসি (Prnc) প্রোটিন গুলোতে আলফা হেলিক্স এর অংশ বেশি থাকে এবং বিটা শিট এর পরিমাণ কম থাকে। কিন্তু তখন পিআরএনএসসি (Prnsc) প্রোটিন এ আলফা হেলিক্স এর অংশ কম থাকে এবং বিটা শিট এর পরিমাণ বেশি থাকে [9]।

চিত্রঃ স্বাভাবিক পিআরএনসি (Prnc) এবং সংক্রামক পিআরএনএসসি (Prnsc) প্রোটিন।
স্বাভাবিক ভাবে আমাদের আরও একটি চিন্তা মাথায় চলে আসে যে, দেহের স্বাভাবিক প্রিয়ন প্রোটিন ভাজগত ত্রুটির কারনে সংক্রমক প্রিয়ন প্রোটিন এ পরিনিত হয়, তা ঠিক আছে, কিন্তু দেহে স্বাভাবিক প্রিয়ন প্রোটিনই বা কেন তৈরি হলো?
কোষস্থ স্বাভাবিক পিআরএনসি (Prnc) প্রোটিন এর কিছু কাজ রয়েছে যেমন-
১. একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, স্বাভাবিক কোষীয় প্রিয়ন প্রোটিন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে ভেংগে যাওয়া ‘সোয়ান কোষ- Schwann Cell’ এর মায়েলিন বা চর্বির আবরণের পুনর্গঠনে সাহায্য করে।
২. অন্য একটি গবেষণায় পাওয়া যায়, প্রিয়ন অস্থিমজ্জার রক্তকোষ তৈরিকারী প্রাথমিক কোষ গুলোতে থাকে, যেসব প্রাথমিক কোষ সমূহে প্রিয়ন থাকেনা সেগুলো খুব সহজেই কার্যকারীতা হারিয়ে ফেলে [10]।
৩. প্রিয়ন প্রোটিন এর অ্যামাইলয়েড তন্তু মৃত কোষ কে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নতুন কোষ কে ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে [11]।
৪. কিছু প্রিয়নের এন্টিভাইরাল (ভাইরাস বিনাশকারী) ক্ষমতা রয়েছে যা প্রানী দেহে সহজাত প্রতিরক্ষা প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্য যে এরা এইচআইভি (HIV) ভাইরাসের বিরুদ্ধেও প্রতিরক্ষা প্রদান করে থাকে [12]।
আমরা পূর্বেই জেনেছি প্রিয়ন তার প্রতিরুপ তৈরি করতে পারে। এখন আমরা দেখবো কিভাবে প্রিয়ন তার প্রতিরুপ তৈরি করে। অনুমান করা হয়, প্রিয়নের বংশ বিস্তার দুই উপায়ে হতে পারে। সেগুলো হলো-
- হেটেরো-ডাইমার মডেল এই ধারনা অনুযায়ী পিআরএনএসসি (Prnsc) প্রোটিন গুলো বাহিত হয়ে পিআরএনসি (Prnc) প্রোটিন এর নিকট যায়। এরা পরস্পর মিলিত হয় এবং এনজাইম এর কার্যকরীতায় নতুন পিআরএনএসসি (Prnsc) প্রোটিন তৈরি করে [13, 14]। ব্যাপারটা অনেকটা হাসানের ঐ গানের মতো – “আমি হাত দিয়ে যা ছুঁই তাই দুঃখ হয়ে যায়”।
- ফিবরিল মডেল পিআরএনএসসি (Prnsc) সাধারণ তন্তু ন্যায় অবস্থান করে। এই ধারনা অনুসারে পিআরএনএসসি(Prnsc) প্রোটিনের শেষ প্রান্তে এসে পিআরএনসি (Prnc) ব্ন্ধন তৈরি করে এবং পিআরএনসি(Prnc) প্রোটিন, পিআরএনএসসি(Prnsc) প্রোটিনে রুপান্তরিত হয়। এরা পর্যায়ক্রমে বড় তন্তুর ন্যায় গঠন তেরি করে, যা অ্যামাইলয়েড তন্তু নামে পরিচিত [15-17]।

কিভাবে প্রিয়ন সংক্রামিত হয়?
আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, মানবদেহে অবস্থিত স্বাভাবিক কোষীয় প্রিয়ন প্রোটিন এর অস্বাভাবিক আচরণগত কারণে প্রিয়ন সংক্রান্ত রোগ সৃষ্টি হয় [1]। এছাড়াও পোষক দেহের বাইরে থেকে খাবারের সাথে দেহে প্রবেশ করতে পারে। যেসব শষ্যক্ষেতে পশুর মল সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেসব ক্ষেতের ফসলের মাধ্যমে এ সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা অনেক বেশি [18, 19]। এছাড়াও রোগাক্রান্ত পশুর মাংস, মগজ এবং অন্যান্য অংশ ভক্ষণ করলে এ রোগ ছড়াতে পারে। রক্ত ও অঙ্গ প্রতিস্থাপন (যেমনঃ কিডনি, লিভার ইত্যাদি) এবং মস্তিষ্কের সার্জারির কারনে এ প্রোটিন ছড়াতে পারে। মজার ব্যাপার হলো মহিলাদের বন্ধ্যাত্ব দূর করতে ব্যবহৃত ‘হিউম্যান মেনোপোজাল গোনাডোট্রপিন-Human menopausal gonadotropin’ (একধরনের হরমোন যা মূত্র থেকে সংশ্লেষ করা হয়) থেকেও এই ভয়ানক প্রোটিনটি ছড়াতে পারে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে, উদ্ভিদও প্রিয়ন প্রোটিন এর বাহক হিসাবে কাজ করতে পারে।

২০১৫ সালে, আমেরিকার টেক্সাস ইউনিভার্সিটির স্বাস্থ্যবিজ্ঞান কেন্দ্রের একদল গবেষক তাদের একটি গবেষণা কাজের জন্য হ্যামস্টার নামক ইঁদুর ন্যায় একধরনের প্রানীকে মাঠে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়। তার কিছু দিন পূর্বে একই মাঠে একটা প্রিয়ন সম্বলিত রোগাক্রান্ত হরিণ মারা যায়। ঐ মাঠের ঘাস খাওয়ার ফলে হ্যামস্টার গুলোও প্রিয়ন সংগঠিত রোগে আক্রান্ত হয়। পরবর্তীতে গবেষকরা আবিষ্কার করেন যে উক্ত মাঠের ঘাসের মধ্য সংক্রামক প্রিয়ন প্রোটিন পিআরএনএসসি (Prnsc) এর অস্তিত্ব রয়েছে [20, 21]। কিছু বিচ্ছিন্ন গবেষনায় দেখা গেছে বায়ু ও মাটির মাধ্যমেও এই সংক্রমণ ছড়াতে পারে [18, 22]।
যাই হোক, একটি অনুসন্ধানে দেখা গেছে প্রিয়ন সংগঠিত রোগের ১০-১৫ শতাংশ হয়ে থাকে বংশগত ভাবে। ১ শতাংশ হয়ে থাকে বাইরে থেকে আসা সংক্রমক প্রিয়ন প্রোটিন এর কারনে (যেমনঃ রোগাক্রান্ত পশুর মাংশ বা মগজ খেলে, বা অন্য মাধ্যম দ্বারা) এবং বাকি ৮৫-৯০ শতাংশ ক্ষেত্রেই কি কারণে রোগটি হয়েছে তার কারন জানা যায় না।
প্রিয়ন কিভাবে রোগ সৃষ্টি করে?
আমরা পূর্বেই জেনেছি যে সংক্রমক প্রিয়ন প্রোটিন আমাদের দেহেই তৈরি হয় এবং দেহের অন্যান্য কোষের ন্যায় এগুলো মস্তিষ্কের কোষে ও তৈরি হতে পারে। ফলাফল স্বরূপ এরা কোষের স্বাভাবিক প্রিয়ন প্রোটিন কে সংক্রমক প্রিয়ন প্রোটিনে রুপান্তর করে এবং কোষের বাইরে এসে অ্যামাইলয়েড তন্তু তৈরি করে [1]।
এছাড়াও সংক্রমক প্রিয়ন প্রোটিন সরাসরি আমাদের দেহে প্রবেশ করতে পারে নানা উপায়ে যেমনঃ আক্রান্ত পশুর মাংশ বা মগজ খেলে, অন্য যে কোন খাবারের সাথে, বিশেষ ক্ষেত্রে বায়ু ও মাটির মাধ্যমে ও ছড়ায়। খাওয়ার পর এই সংক্রমক প্রিয়ন প্রোটিন গুলো পাকস্থলীতে পৌঁছায়। এর পর ক্ষুদ্রান্ত্রের দেয়াল সংশ্লিষ্ট লসিকা নালিতে প্রবেশ করে। লসিকা নালিতে অবস্থিত ডেনড্রিক (ফ্যাগোসাইটিক) কোষ এবং ম্যাক্রোফেজ দ্বারা ভক্ষিত হয়। এই ফ্যাগোসাইটিক কোষ গুলো ভক্ষিত সংক্রামক প্রিয়ন প্রোটিন গুলোর ক্ষতি করতে পারে না, কারন এদের গঠনের সময় আলফা হেলিক্স কম এবং বিটা সীট বেশি তৈরি হয়। যা এই প্রোটিন গুলোকে প্রতিরোধী (Resistance) করে তোলে। ফলে ফ্যাগোসাইটিস এর লাইসোজাইম এনজাইম ও এর কোন ক্ষতি করতে পারে না। এমন কি অধিক তাপেও এদের নষ্ট করা সম্ভব নয়। এজন্য সংক্রমিত পশুর মাংশ অধিক তাপে রান্না করে খেলে ও প্রিয়ন সংগঠিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।
যাই হোক, উক্ত ডেনড্রিক কোষের সাথে বাহিত হয়ে এরা রক্তনালিতে চলে আসে। যা পরবর্তীতে ব্লাড ব্রেইন বেরিয়ার (Blood Brain Barrier) কেও ছাপিয়ে মস্তিস্কে চলে যায়। ব্লাড ব্রেইন বেরিয়ার রক্তে অবস্থিত ক্ষতিকারক পদার্থকে ছেঁকে মস্তিষ্ককে রক্ষা করে। যেহেতু এই সংক্রমক প্রিয়ন প্রোটিন গুলো রক্ত কণিকা (ডেনড্রিক কোষ) এর ভিতরে অবস্থান করে, তাই ব্লাড ব্রেইন বেরিয়ার এদের আক্রমণ ঠেকাতে পারে না। একই কারনে আমাদের দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও এর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হয়। মস্তিষ্কে প্রবেশের পর এরা কোষের বাইরে এসে বিভিন্ন স্থানে জড়ো হতে থাকে এবং অ্যামাইলয়েড তন্তু সৃষ্টি করে যা স্নায়ুর সংকেত প্রদানে বাঁধা প্রদান করে এবং স্নায়ু কোষগুলো কে মেরে ফেলতে থাকে [23]।

স্নায়ুতন্ত্রে মাইক্রোগ্লিয়া নামক একধরনে প্রতিরক্ষা কোষ থাকে। এরা মৃত স্নায়ুকোষ গুলো কে অপ্রত্যাশিত অংশ মনে করে ধ্বংস করে দেয়। ফলে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত দেখা যায়। এটিকে ‘ট্রান্সমিসেবল স্পঞ্জিফর্ম এনসেফালোপেথি (transmissible spongiform encephalopathies) নামক স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা বা রোগ বলা হয়ে থাকে।
আমরা জানি যে, মস্তিষ্ক প্রাণীর সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। হাঁটা-চলা থেকে শুরু করে চিন্তা-ভাবনা সবই নিয়ন্ত্রিত হয় মস্তিষ্কের নির্দেশনায়। যেহেতু এই রোগ এর কারনে মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু তন্ত্রের ক্ষয় হয়, সেহেতু এই রোগে আক্রান্ত প্রাণী পক্ষাঘাতগ্রস্থ এবং পাগলের ন্যায় আচরন করে। প্রথম দিকে আমরা যেই ডাংকি, মংকি ও চাংকির যে পাগলামি দেখেছিলাম তা কোন ভৌতিক ঘটনা ছিল না। তা মুলত তাদের মস্তিষ্কে প্রিয়ন সংক্রমণের কারনেই হয়েছিল।
সবই বুঝলাম, কিন্তু এ রোগ হলে বুঝবো কিভাবে?
প্রিয়ন সংগঠিত রোগের সাধারণ লক্ষণ গুলো হলো [24, 25] –
- চিন্তাভাবনা, স্মৃতিশক্তি এবং বিচারে অসুবিধা
- ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন যেমন উদাসীনতা, আন্দোলন এবং বিষন্নতা
- বিভ্রান্তি
- অনিচ্ছাকৃত পেশীর খিঁচুনি (মায়োক্লোনাস)
- সমন্বয়ের ক্ষতি (অ্যাটাক্সিয়া)
- ঘুমের সমস্যা (অনিদ্রা)
- প্রতিবন্ধী দৃষ্টি বা অন্ধত্ব
আমরা কিভাবে নিশ্চিত হবো যে আসলেই প্রিয়ন সংগঠিত রোগ হয়েছে?
মস্তিষ্কের এমআরআই (MRI), ইইজি (EEG) করার মাধ্যমে এই রোগ নির্ণয় করা যায়। এছাড়াও সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড এবং কিছু ক্ষেত্রে রক্ত পরীক্ষা করার মাধ্যমে ও এই রোগ নির্ণয় করা সম্ভব [24]।
প্রিয়ন সংগঠিত রোগের চিকিৎসা কি?
প্রিয়ন সংগঠিত রোগের সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা বা ঔষুধ এখনও আবিষ্কার হয়নি। তবে ‘Antiprion antibodies’ নামক এন্টিবডি আবিষ্কৃত হয়েছে যা ‘blood-brain-barrier’ কে অতিক্রম করে প্রিয়ন প্রোটিনকে ধ্বংশ করতে সক্ষম। Polythiophenes এবং Astemizole-এই দুটি ঔষুধও প্রিয়নের বিরুদ্ধে কাজ করে বলে জানা গিয়েছে। তবে ওষুধ তৈরির কিছু ধারণা বিজ্ঞানীরা অনুমান করতে পেরেছেন। যেমনঃ পিআরএনসি(Prnc) প্রোটিন কে পিআরএনএসসি(Prnsc) প্রোটিনে রূপান্তরিত হতে বাঁধা প্রদান করা, অ্যামাইলয়েড তন্তু তৈরি হওয়ার সময় তার শেষ প্রান্ত কে কোন ড্রাগ দিয়ে ব্লক করে দেওয়া। বর্তমানে ‘কম্পিউটার ভিত্তিক ড্রাগ ডিজাইন (computer aided drag design, CADD) ওষুধ তৈরিকে খুব সহজলভ্য করেছে। আশা করছি শীগ্রই এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞান আমাদের প্রিয়ন সংগঠিত রোগর প্রতিকার প্রদান করবে [26-28]।
প্রিয়ন-রোগ প্রতিরোধের উপায় কি?
বংশগত বা অজানা কারনবশত প্রিয়ন সংগঠিত রোগের প্রতিরোধ করা অসম্ভব। কিন্তু অর্জিত প্রিয়ন রোগের সংক্রমণ রোধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। যেমনঃ
- গরুর মস্তিষ্ক এবং মেরুদন্ডের মতো অংশগুলিকে মানুষ বা প্রাণীর খাবারে ব্যবহার করা থেকে নিষিদ্ধ করা।
- যাদের প্রিয়ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার পারিবারিক ইতিহাস আছে তাদের রক্ত বা অন্যান্য টিস্যু দান করা থেকে বিরত থাকা।
- সন্দেহভাজন প্রিয়ন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির স্নায়বিক টিস্যুর সংস্পর্শে আসা চিকিৎসা যন্ত্রগুলিতে শক্তিশালী ‘নির্বীজন (sterilize) ব্যবস্থা ব্যবহার করা।
- ‘নিষ্পত্তিযোগ্য (disposable) চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ধ্বংস করা।
- বর্তমানে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বা বিক্ষিপ্ত ধরনের প্রিয়ন রোগ প্রতিরোধ করার কোনো উপায় নেই। যদি আপনার পরিবারের কারোর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রিয়ন রোগ থাকে, তাহলে আপনি এই রোগটি হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করার জন্য জেনেটিক কাউন্সেলরের সাথে পরামর্শ করার কথা বিবেচনা করতে পারেন [29, 30]।
জৈব অস্ত্র হিসাবে প্রিয়ন এর ব্যবহার
বলা হচ্ছে প্রিয়ন কে খুবই শক্তিশালী জৈব অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে [31]। জৈব অস্ত্র হলো মানুষ হত্যা কিংবা বিকলাঙ্গ করার উদ্দেশ্যে সামরিক যুদ্ধে কোন জৈবিক বিষাক্ত পদার্থ কিংবা সংক্রামক অণুজীব যেমন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং ছত্রাকের ব্যবহার করা। বর্তমান সময়ে যা অনেক বড় আতংকের নাম। তবে প্রচলিত আন্তর্জাতিক মানবকল্যাণ আইন এবং নানান আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে জৈব-অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সশস্ত্রযুদ্ধে জৈব-পদার্থের ব্যবহার একপ্রকার যুদ্ধাপরাধ।

তথ্যসূত্র:
Colby, D.W. and S.B.J.C.S.H.p.i.b. Prusiner, Prions. 2011. 3(1): p. a006833.
Lloyd, S., S. Mead, and J.J.P.P. Collinge, Genetics of prion disease. 2011: p. 1-22.
Griffith, F.J.E. and Infection, The significance of pneumococcal types. 1928. 27(2): p. 113-159.
Prusiner, S.B.J.N.E.J.o.M., Neurodegenerative diseases and prions. 2001. 344(20): p. 1516-1526.
Cohen, F.E., et al., Structural clues to prion replication. 1994. 264(5158): p. 530-531.
Eigen, M.J.B.c., Prionics or the kinetic basis of prion diseases. 1996. 63(1): p. A1-A18.
Abdelaziz, D.H., et al., Autophagy pathways in the treatment of prion diseases. 2019. 44: p. 46-52.
Boddie, C., et al., Assessing the bioweapons threat. 2015. 349(6250): p. 792-793.
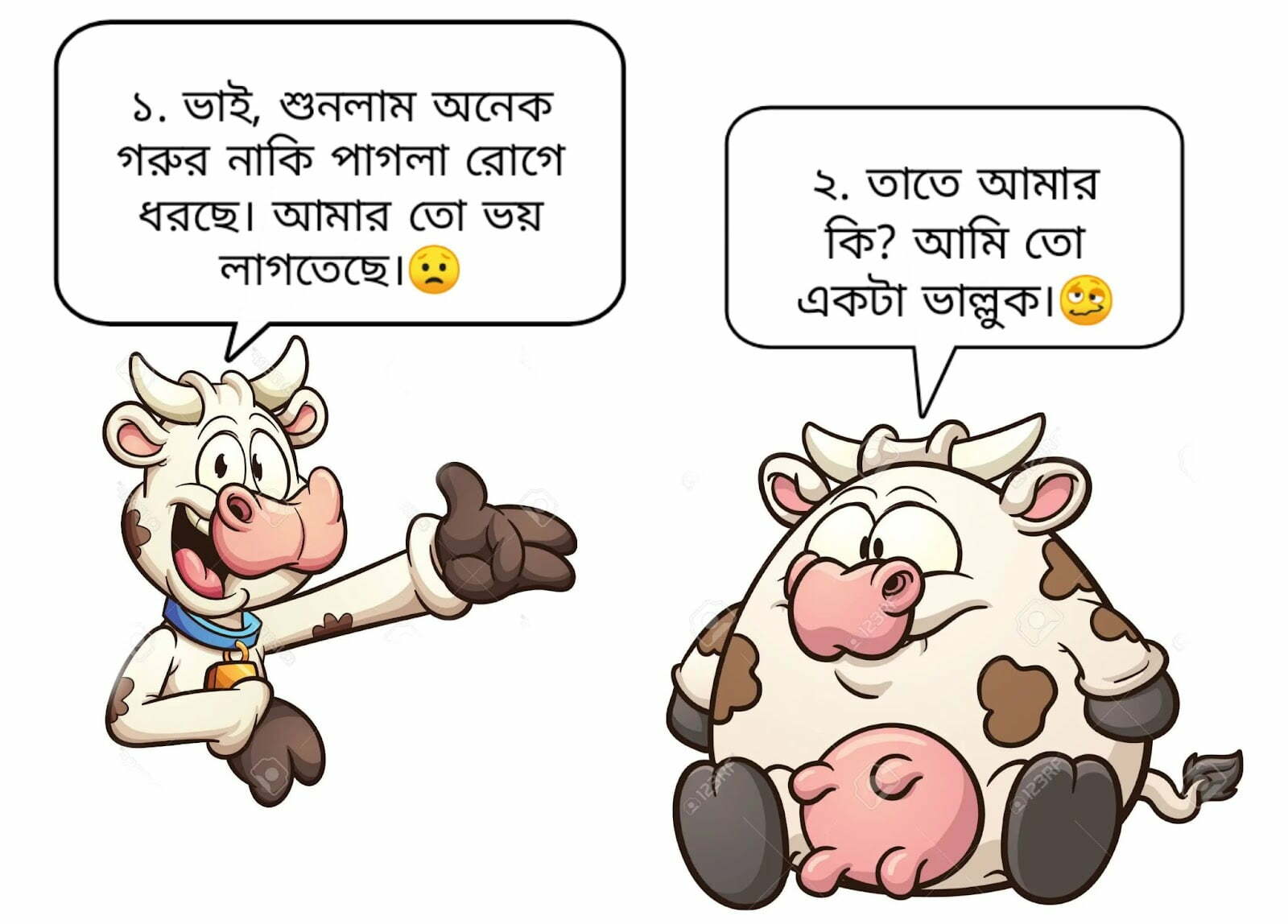





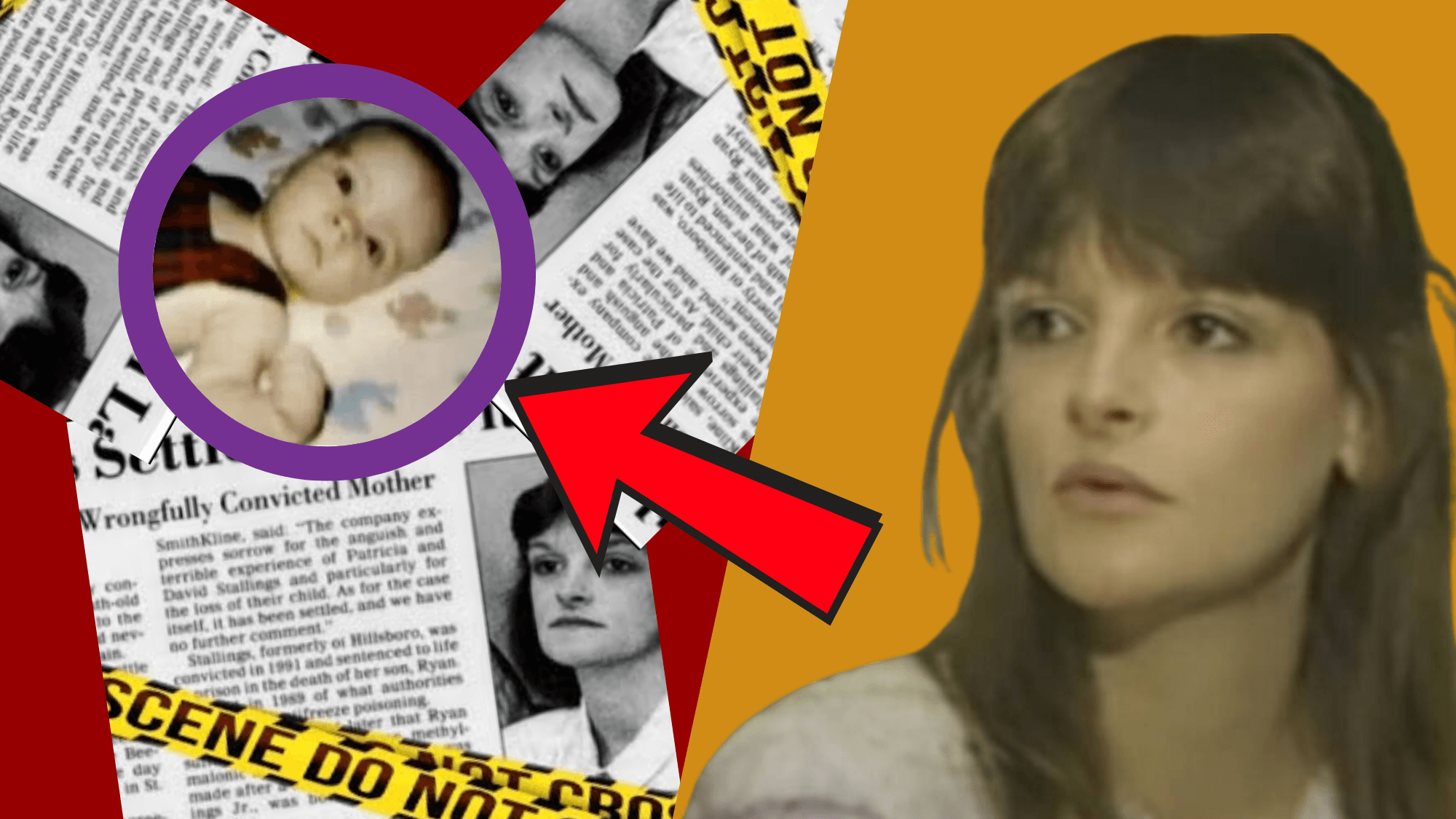

Leave a Reply