“হাত দিয়ে কেন কাজ করবো যদি মেশিন সেটা করে দিতে পারে?” – এই ধারণাই সূত্রপাত করে শিল্পবিপ্লবের। বিজ্ঞানীরা আজও নিশ্চিত নন যে ঠিক কবে এই বিপ্লবের শুরু এবং কবে এর শেষ। তবে ধারণা করা হয় যে ১৭৬০ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে এই গণজোয়ার শুরু হয়েছিলো। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই বিপ্লবের রেশ শুরু হওয়ার পর থেকেই পৃথিবীতে বেশ কয়েকটি বড় ধরনের পরিবর্তন শুরু হয়ে যায় যা পৃথিবী তার গত কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে কখনো দেখেনি।
কলকারখানা নির্গত প্রচুর পরিমাণ ধোঁয়া, নিয়ন্ত্রণহীন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন, বিপুল পরিমাণ ফ্রিয়ন গ্যাসের উপস্থিতি ইত্যাদি গ্রিন হাউজ ইফেক্টের সূত্র ধরে বিগত একশ বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এই অতিরিক্ত তাপমাত্রার বড় একটি অংশ শোষণ করেছে পৃথিবীর সমুদ্র। পানির উপরিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা যার ফলে অনেকাংশে বেড়ে গিয়েছে।
বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সত্য। পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন আসেঃ এর ফলে সমুদ্রের লবণাক্ততার তারতম্য কেন হবে? প্রবাহী এবং তাপগতিবিদ্যা সম্পর্কে যারা ভালো জানেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেলবেন ব্যাপারটি। লবণাক্ততা তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, কোনো তরল কতখানি লবণাক্ততা প্রদর্শন করবে তা নির্ভর করে তরলটি কতখানি গরম বা ঠান্ডা।
সহজ সূত্র হলো, অধিক তাপ অধিক লবণ ধরে রাখে। অতিরিক্ত গরমে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানি বাষ্পীভূত হয়ে উবে চলে যায় এবং নিচে পড়ে থাকে লবণ। যার ফলে একবিংশ শতাব্দীর নিরক্ষরেখার কাছাকাছি থাকা সমুদ্রগুলো (প্রশান্ত, মধ্য-আটলান্টিক, ভারত) হবে আরও বেশি লবণাক্ত। পানির পিএইচ (pH) বেড়ে যাবে বিপদসীমার বাইরে। এর একটি সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য হলো, অতিবৃষ্টি (বন্যা) অনেক বেড়ে যাবে এবং একই সাথে শুষ্ক অঞ্চলে নেমে আসবে অধিক মাত্রায় খরা এবং দুর্ভিক্ষ। ধারণা করা হয় সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, উচ্চতা, এবং বায়ুপ্রবাহ, এই তিনটি বিষয় ভবিষ্যতে সামুদ্রিক পানির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা রাখবে।
এই লেখায় কয়েকটি ছোট পয়েন্টের মাধ্যমে সমুদ্রের পানির লবণাক্ততার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করবো। তবে আমার প্রধান লক্ষ্য হলো বাংলাদেশ এর প্রসঙ্গে এই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা।
বাংলাদেশকে আর্কটিকের উপহার?
আমি একজন বাংলাদেশি গবেষক এবং আমি আর্কটিক মহাসাগরের গতিবিদ্যা নিয়ে পিএইচডি করছি। স্বভাবতই, আমার লেখায় এই দুই অঞ্চলের ভৌগোলিক মেলবন্ধন নিয়ে আসার একটা সুপ্ত প্রচেষ্টা থাকবে। তবে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমার অতিরিক্ত কোনো জোরাজুরির প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১১,৫৮০ কিলোমিটার দূরে বরফে ঢাকা মহাসাগরে যা ঘটছে তার একটি শক্তিশালী প্রভাব দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চল (উত্তর ও দক্ষিণ) প্রায় সারাবছর বরফে ঢাকা থাকে। গ্রীষ্মকালে যা খানিকটা (বা অনেকটা!) গলে যায়। শীতকালে আবার তারা জুটি বাঁধে। তবে, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে প্রতি বছর বিশেষত গ্রীষ্মে (এমনকি শরতেও) মেরু অঞ্চলের বরফ দ্রুত গলছে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায়, এই অতিরিক্ত গরম প্রতি বছর প্রায় ৭৫০ বিলিয়ন টন ওজন সমপরিমাণ বরফকে গলিয়ে দেয়। এই গলিত বরফ কোথায় যায়? তারা সব পানি হয়ে পৃথিবীর অন্যান্য মহাসমুদ্রের সাথে মিশে যায়।
বঙ্গোপসাগরও এই অতিরিক্ত পানির একটা শেয়ার পায়। যার ফলে প্রতি বছর কিছুটা হলেও বেড়ে যায় বঙ্গোপসাগরের উচ্চতা। এই অতিরিক্ত লোনা পানি উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোর (ভোলা, নোয়াখালী, ফেনী, কক্সবাজার) জন্য কোন সুসংবাদ নিয়ে আসে না। বরফগলা পানি এবং সাধারণ সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা এক নয়। ভবিষ্যতে এই ভিন্নতা সমুদ্রের কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে মিশে গিয়ে লবণাক্ততা মাত্রাকে আরও ভারসাম্যহীন করে তুলবে।
সমুদ্র দেবতার আক্রোশ
পৃথিবীর তাপমাত্রা বৈশ্বিক বায়ুপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই বায়ুর ঝাপটা সমুদ্রের স্রোতকে বয়ে নিয়ে যায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। এখানে একটি সহজ বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে কথা বলে রাখা ভালো। আমরা জানি গরম বায়ু হালকা, এবং ঠান্ডা বায়ু ভারী। কোনো অঞ্চলে যদি তাপমাত্রা বেড়ে যায় তাহলে সেই জায়গায় বায়ু হালকা হয়ে যায়। হালকা বায়ু তো ততখানি চাপও সৃষ্টি করতে পারে না, তাই না? তাই কোনো অঞ্চল অতিরিক্ত গরম হয়ে গেলে সেখানে নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। এই নিম্নচাপই উপকূলবর্তী অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাস বা ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বাড়িয়ে দেয়।
তবে ঝড়ঝাপটা নিয়ে লেখার উদ্দেশ্য নেই এই ব্লগে। বরং এটা জেনে রাখতে হবে যে ঘূর্ণিঝড়ের বায়ুপ্রবাহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ত পানিকে মিশ্রিত করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, গালফ স্ট্রিম নামক প্রবাহ উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলে লবণ ও তাপ পরিবহণ করে। যদি এই প্রবাহের তীব্রতা ও দিক পরিবর্তিত হয়, তবে উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলে লবণাক্ততার মাত্রা পরিবর্তিত হবে এবং জলবায়ুতে প্রভাব ফেলতে পারে। একইভাবে, ভারত মহাসাগরের লবণাক্ততার মান বঙ্গোপসাগরের থেকে কিছুটা বেশি। তাই এই মিশ্রণও উপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণাক্ততার ভিন্নতা নিয়ে আসতে সক্ষম।
বৃষ্টি বিভ্রান্তি
বাংলাদেশ বর্ষার দেশ। বৃষ্টিপাতের হার জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মৌসুমি জলবায়ুর বৃষ্টিপাতের একটি নির্দিষ্ট রুটিনমাফিক সিস্টেম আছে। তবে প্রথম প্রশ্ন হলোঃ মৌসুমি জলবায়ু কী? সহজ উত্তর হলোঃ সারাবছর ধরে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বায়ুপ্রবাহ একই থাকে না, বরং তা পরিবর্তিত হয়। ঠিক একারণেই আমরা “দক্ষিণা বাতাস” সারা বছর ধরে অনুভব করিনা। প্রধানত শীতকালে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। এই প্রতিনিয়ত অথচ শৃঙ্খলিত পরিবর্তন হাজার বছর ধরে বাংলার বুকে বৃষ্টিপাতের ধারাকে অনুমেয় রেখেছিল।
তবে আমরা বাস্তবিক অর্থেই একটি জটিল সময় পার করছি যেখানে অনুমেয় ঘটনাগুলোই অনেকাংশে অনিশ্চিত হয়ে যেতে সময় লাগছেনা। জলবায়ু যদি এভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে তাহলে যে-সব অঞ্চলে সাধারণত কম বৃষ্টি হয়, সেখানে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। বিপরীতে, যে-সব অঞ্চলে অধিক বৃষ্টি হয়, সেখানে খরা দেখা দিতে পারে। যখন বৃষ্টি বেশি হয়, তখন সেই পানির একটা বড় অংশ সমুদ্রে গিয়ে মিশে লবণাক্ততা হ্রাস করে। বিপরীতে, খরা হলে লবণাক্ততা বাড়ে, কারণ পানি বাষ্পীভূত হলেও লবণ থেকে যায়। ফলে, জলবায়ুর দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন হলে সমুদ্রের লবণাক্ততাও স্থিতিশীল থাকবে না।
খাবারে ও টাকায় টান
আমরা মাছে-ভাতে বাঙালি। দেশের বেশিরভাগ মানুষের খাবার প্লেটে এখনো ভাতের সাথে কিছু সবজি বা পুকুর-নদীর মাছ থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে, লবণাক্ততার তারতম্য ফসলের পাশাপাশি মাছের প্রজনন ও স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করে। দক্ষিণাঞ্চলের নদী এবং জলাশয়গুলি এখনো আমাদের মাছের বড় একটি উৎস। সমুদ্রের নির্দিষ্ট অংশে লবণাক্ততা পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন মাছের প্রজাতি হ্রাস পেতে পারে। সত্যি বলতে এই হ্রাসের একটি ধারা আমরা আমাদের প্রজন্মেই পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করছি (যদিও তার বড় একটি কারণ জলাশয় ভরাট, ভূমি দখল, ইউট্রোফিকেশন, এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দূষণ তবে লবণাক্ততার হেরফেরেও একটি ঋতুভিত্তিক প্রভাব আছে)।
উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রের লবণাক্ততার তারতম্য তাই অর্থনৈতিকভাবে অনেক জেলেদেরকে বিপদে ফেলার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যারও সৃষ্টি করতে পারে। সমুদ্রের লবণাক্ত পানি জমি ও মিঠা পানির উৎসে অনুপ্রবেশ করলে কৃষিজমি ও মিঠা পানির জন্য হুমকি তৈরি হয়। এর ফলে গুদামে খাদ্য মজুদ কমে যাবে। শহর পর্যন্ত হয়ত অনেক খাবার পৌঁছাবেই না। খাদ্য উৎপাদনের সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক শৃঙ্খল ব্যাহত হবে। পাশাপাশি, জরুরি পরিস্থিতিতে বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকটও দেখা দিতে পারে। এটি গ্রাম্য ও উপকূলীয় সমাজের জন্য বড় ধরনের আর্থসামাজিক চ্যালেঞ্জের কারণ হয়ে উঠতে পারে। আমরা আবেগপ্রবণ জাতি। যেকোনো সমস্যার সামাজিক প্রতিক্রিয়াগুলো তাই অতিরিক্ত রকম সংবেদনশীল হয়ে উঠার আগে আমাদেরকে এই ব্যাপারগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরি।
বাংলাদেশ এর উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে সাম্প্রতিক লবনাক্ততা বেড়ে যাওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনেকটা এরকম- আমরা জানি উত্তরে হিমালয় প্রদেশ থেকে বরফগলা সুমিষ্ট পানি বাংলাদেশে বিভিন্ন নদী হয়ে প্রবেশ করে। পাহাড়ের চূড়া, আঁকাবাঁকা দীর্ঘ রাস্তা, বন-জঙ্গল, গ্রাম, সভ্যতা পেড়িয়ে তাদের অন্তিম গন্তব্য হয় বঙ্গোপসাগর। বঙ্গোপসাগরের দৈনিক জোয়ার উপকূলবর্তী জেলাগুলোতে লবণাক্ত সমুদ্রের পানি নিয়ে আসে। প্রায় কয়েকশত কিলোমিটার এলাকা জুড়ে দিনে দুইবার ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা বেড়ে যায়। উত্তরের সুমিষ্ট পানি এবং দক্ষিণের লবণাক্ত পানি যুগ যুগ ধরে প্রতিদিন একে অন্যের স্পর্শে আসে।
বাংলার জেলে এবং কৃষকরা (এমনকি সাধারণ মানুষরাও) এই ঘটনার সাথে আজীবন পরিচিত। এখানে এতদিন নতুনত্বের কিছু ছিল না। তবে এখন আসছে। সামুদ্রিক জোয়ারের শক্তি এবং নদীর স্রোতের বাঁধার মাঝে এক মেলবন্ধন ছিল, এক ভারসাম্য ছিল। তবে যখনি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যায়, স্বভাবতই জোয়ারের ধাক্কা নদীর স্রোতকে কাবু করে দেয়। উপকূলে ওঠে আসে আরও বেশি সমুদ্রের পানি। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে লবণাক্ততা। বাটারফ্লাই ইফেক্ট বলে, কোনো এক প্রজাপতি আমেরিকাতে ডানা ঝাঁপটালে সুদূর আমাজন জঙ্গলে তা এক ঘূর্ণিঝড় তৈরি করবে। ঠিক তেমনি সমষ্টিগতভাবে পৃথিবীর কোণায় কোণায় ঘটে যাওয়া প্রকৃতির উপর অত্যাচার যেন হতাশা এবং দুঃসহ বাস্তবতা হয়ে ফিরে আসে তার কাছেই, অন্য এক রূপে।
পরিশিষ্ট
ভবিষ্যতে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কেবল তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা বরফ গলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং এই প্রভাব আরও ব্যাপকভাবে সমুদ্রের লবণাক্ততা ও বাস্তুসংস্থানের উপর পড়বে। সঠিক গবেষণা, সামাজিক সচেতনতা, এবং সরকারের বিশেষ মনোযোগ অবশ্যই সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান ও উপকূলীয় এলাকাগুলোর সুরক্ষা অনেকাংশে নিশ্চিত করতে পারবে। একটি প্রচলিত উপায় হলো, উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ তৈরি করা, যা লবণাক্ত পানি অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রিত প্রতিরোধ করে। পাশাপাশি, বিভিন্ন অঞ্চলে খরা ও বন্যার মোকাবিলায় আধুনিক উপায়ে পানি জমিয়ে রাখা (পানির সঞ্চয়ন) ও পানির পুনর্ব্যবহার প্রক্রিয়া উন্নত করা প্রয়োজন। সমুদ্রের তাপমাত্রা ও লবণাক্ততার পরিবর্তনের ওপর নজরদারি করতে নতুন ধরনের উপগ্রহ প্রযুক্তির ব্যবহার হতে পারে, যা ইতোমধ্যেই পৃথিবীর অনেক দেশ শুরু করে দিয়েছে। সবশেষে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি আমাদের মৌলিক জ্ঞান এবং সচেতনতা থাকে, আমি বিশ্বাস করি, পরবর্তী প্রজন্ম এগিয়ে আসবে সমুদ্রের লবণাক্ততা ও সামুদ্রিক পরিবেশের স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে।
তথ্যসূত্রঃ
- Modeling the Relationship of Groundwater Salinity to Neonatal and Infant Mortality From the Bangladesh Demographic Health Survey 2000 to 2014
- Living on the Frontier: Laypeople’s Perceptions and Communication of Climate Change in the Coastal Region of Bangladesh
- EFFECTS OF CLIMATE AND SEA·LEVEL CHANGES ON THE NATURAL RESOURCES OF BANGLADESH
- Current and Future Salinity Intrusion in the South-Western Coastal Region of Bangladesh

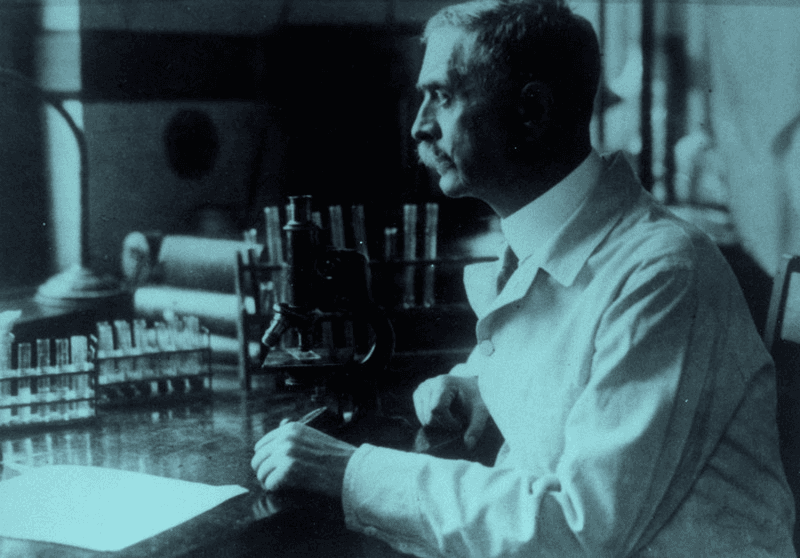






Leave a Reply