আমাদের মানবদেহ এক চলমান বিস্ময়। সূক্ষ্ম স্তরে, মাইক্রোস্কোপিক স্কেলে এটি আশ্চর্য জটিলতায় ভরা। সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গিতে দেহের শৈল্পিক স্থাপত্যের কিছু নিদর্শন নিচের ছবিগুলো। সবগুলো ছবি Science is Beautiful বই থেকে সংগৃহীত এবং তথ্যগুলো ডিসকভার ম্যাগাজিন থেকে ভাবানুবাদকৃত।
মেদকলা বা চর্বির কোষগুচ্ছ

বিশেষ ধরনের রঞ্জকে রঞ্জিত ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে দৃশ্যমান ছবি এটি। মেদ কোষের বেশিরভাগ অংশ শুকনো থাকে, সাইটোপ্লাজম থাকে না বললেই চলে। তাই ছবিতে এদের এমন মধুপোকার বাসার কুঠুরির মতো দেখাচ্ছে। ত্বকের নিচের তুলতুলে অংশে থাকা এই মেদকলা আমাদের সহ সকল প্রাণীর দেহের শক্তির সংগ্রহশালা।
পেনিসিলিয়াম ছত্রাক

দেখতে অনেকটা ফুলের মতো যেন। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দৃশ্যমান পেনিসিলিয়াম ছত্রাকের গুচ্ছ এরা। হালকা গোলাপী রঙে দেখানো সুতার মতো অংশগুলোকে বলে ‘কনিডিওফোর’ আর কিছুটা হলদেটে গুচ্ছগুলো ‘কনিডিয়া’। গুচ্ছের শেষের অংশটা হচ্ছে এদের বংশবিস্তারের অঙ্গ। জনজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এন্টিবায়োটিক ‘পেনিসিলিন’ আসে এই ছত্রাক থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই পেনিসিলিন গুলি খাওয়া ক্ষত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গ সাড়াতে সফল হয়েছিল। পেনিসিলিনের এন্টিবায়োটিকের জন্য আলেকজেন্ডার ফ্লেমিং ১৯৪৫ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পান।
মস্তিষ্কের কোষ

ফ্লোরোসেন্ট বাতির মতো দেখতে এরা হচ্ছে মস্তিষ্কের দুই ধরনের কোষ। এরা মানব মস্তিষ্কের খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সবুজ রঙে রঞ্জিত কোষটা হচ্ছে মাইক্রোগ্লিয়াল কোষ আর কমলা রঙের ও একটু বড় আকৃতিরটা হচ্ছে অলিগোডেন্ড্রোসাইট। সবুজ কোষগুলো কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সাড়া প্রদান করে। এ ধরনের কোষগুলো শরীরের আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলোকে শনাক্ত করে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে সংকেত প্রেরণ করে।
কমলা রঙের অলিগোডেন্ড্রোসাইটের অসমতল কিছু এলাকা নিউরনকে অধিক পরিমাণ মায়েলিন সরবরাহ করতে পারে। যার ফলে নিউরনগুলো একে অপরের সাথে বেশি পরিমাণ বৈদ্যুতিক সংকেত আদান-প্রদান করতে পারে। যার অর্থ হচ্ছে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।
যকৃতের কোষ

লিভার বা যকৃত বা কলিজার যেকোনো স্থানের কর্তিত অংশের আণুবীক্ষণিক চিত্র এটি। অঙ্গাণুগুলো বিশেষ রঙে রঞ্জিত বলে এমন সুন্দর দেখাচ্ছে। বড় বড় নীল স্পটগুলো মাইটোকন্ড্রিয়া, মাইটোকন্ড্রিয়াগুলো কোষের ভেতরে থেকে শক্তি উৎপাদন করে এবং সে শক্তি কোষে সরবরাহ করে। তন্তুর মতো দেখতে সবুজ রেখাগুলো গলগি বস্তু। এরা প্রোটিন তৈরি করে। ফিকে হলুদ অংশগুলো চর্বির ক্ষুদ্র অংশ। বাদামী অংশগুলো হচ্ছে শক্তি সংগ্রাহক গ্লাইকোজেন।
ইনসুলিন কেলাস

এ অষ্টতলকীয় বস্তুগুলো মানুষের হরমোন ইনসুলিন। ইনসুলিন তৈরি হয় অগ্নাশয়ে। এদের কাজ রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ঠিক রাখা। দেহে এই ইনসুলিনের সরবরাহ অপর্যাপ্ত হয়ে গেলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়, যা ডায়বেটিসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।
ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস

এরা ইনফ্লুয়েঞ্জা A H1N1 ভাইরাস। এগুলো মানুষ, শূকর, পাখি, ও ঘোড়াকে আক্রান্ত করতে পারে। ২০০৯ সালে মহামারী আকারে সোয়াইন ফ্লু ছড়িয়েছিল এ ভাইরাসগুলোই। মাঝের অংশের গোলাপি রঙে রঞ্জিত অংশগুলো বংশগত তথ্যভাণ্ডার। এদের DNA থাকে না, তাই এমনভাবে বংশগত তথ্য বহন করতে হয়। এই তথ্যগুলো প্রোটিন দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। ঘিরে রাখা হলুদ রঙের অংশগুলো হচ্ছে প্রোটিনের আবরণ। H1N1 এর H ও N এসেছে Haemagglutinin ও Neuraminidase থেকে। এরা হচ্ছে একধরনের প্রোটিন। চিত্রে বাইরের দিকে সবুজ রঙে এদের চিহ্নিত করা হয়েছে।
ব্যাকটেরিওফাজ

ব্যাকটেরিওফাজ হচ্ছে একধরনের বিশেষ ভাইরাস। এরা ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করতে পারে এবং ব্যাকটেরিয়ার দেহে নিজেদের বংশবিস্তার করে। চিত্রে দৃশ্যমান ভাইরাসটি হচ্ছে T4 ব্যাকটেরিওফাজ। এটি এইমাত্র তার ভাইরাল DNA একটি E. coli ব্যাকটেরিয়ার ভেতর প্রবেশ করালো। এ ধরনের ভাইরাস তাদের তন্তু দিয়ে ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে নোঙর করে। ফাজ ভাইরাসের মাঝ বরাবর দণ্ডসদৃশ অংশটা অনেকটা সিরিঞ্জের মতো। ব্যাকটেরিয়ার কোষ পর্দাকে ছিদ্র করে মাথার মতো দেখতে মূল অংশ থেকে DNA প্রবেশ করিয়ে দেয়। অনেকটা ইনজেকশনের মতো। ভেতরে T4 এর ফাজ বৃদ্ধি পায়, তারপর ব্যাকটেরিয়াকে মেরে বেরিয়ে আসে। পুরো কাজটা সম্পন্ন হয় মাত্র ৩০ মিনিটে।
জমাট রক্ত

চিত্রে রক্তের লোহিত কণিকাগুলো সাদা ও হলুদাভ ফাইব্রিনে আটকা পড়ে গেছে। শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে এই রক্ত জমাট প্রক্রিয়া কাজ করে। এ প্রক্রিয়া সাধারণত ত্বকের অংশে হয়।
Featured Photo Credit: Science is Beautiful
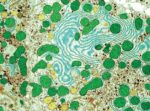
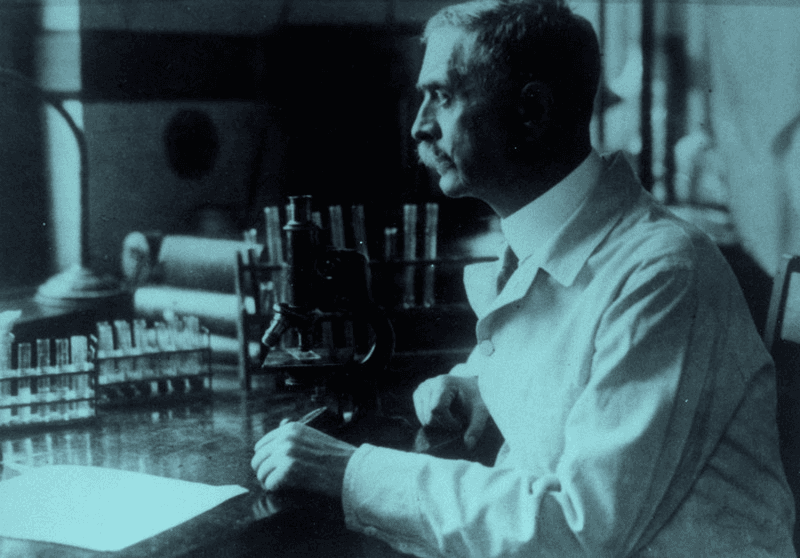






Leave a Reply to খান ওসমানCancel reply