খ্রিস্টের জন্মের ৪০০ বছর আগে হিপোক্রেটস বলেছিলেন আমাদের দের চার ধরনের তরলে গঠিত। এই চার ধরনের তরলের মধ্যে সব সময় ভারসাম্য বজায় থাকে, যা নষ্ট হলেই নানা বিধ ব্যামোর আবির্ভাব হয়। এর মধ্যে ব্ল্যাক বাইল নামক তরলের পরিমান বেড়ে গেলে যেটা হয় তাকে কার্সিনোস এবং কার্সিনোমা বলে বলে ডাকতেন তিনি, যার উৎপত্তি গ্রীক ‘Karkinos’ থেকে, এর অর্থ হচ্ছে কাঁকড়া আক্রান্ত টিস্যু হতে চারপাশে রক্তনালীগুলোর ছড়িয়ে পড়া দেখতে অনেকটা কাঁকড়ার থাবার মত, তাই এই নামকরন। ধীরে ধীরে এর ক্যান্সার নামটি প্রচলিত হয়।
এখন ২০১৫ সালে এসে এত এত বছরের গবেষনা, এত এত মলাট বদ্ধ প্রকাশনা, এত এত পরীক্ষা নীরিক্ষা, এত এত বস্তা টাকা ঢালার পরেও কেন ক্যান্সারের কোন প্রতিষ্ঠিত নিরাময় নেই? কারন ক্যান্সারকে কোন সূত্রে বাধা সম্ভব নয়। সকাল বিকাল আমরা এক নামে একে ডাকলেও প্রতিটা ক্যান্সার আলাদা, প্রতিটা ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর গল্প আলাদা। ক্যান্সার এতটাই রহস্যময় যে, প্রায়ই দেখা যায় যেই চিকিৎসায় একজন রোগী সুস্থ হয়ে গেছেন, সেই একই ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত আরেকজনের ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থা আর কাজ করেনা। দেহের যেকোন টিস্যুকে আক্রান্ত করতে সক্ষম এই ক্যান্সারের কারন হিসেবে ভূপৃষ্ঠ থেকে সূর্য রশ্মি পর্যন্ত হাজার হাজার এজেন্ট ছড়িয়ে আছে।

আগেই বলেছি ক্যান্সারকে যেহেতু আমরা এক নামে চিনি, সে কারনে একে একক কিছু ভাবলে ভুল হবে। ক্যান্সার আসলে অনেক গুলো ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি যাদের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্যে মিল রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন, যা শুরু হয় কিছু জিনের মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তনের কারনে। আমাদের দেহের গঠন ও অন্যান্য কারিগরিতে জড়িত থাকে নানা ধরনের প্রোটিন। প্রতিনিয়ত এইসব প্রোটিন তৈরি হচ্ছে, আবার কাজ শেষে নষ্টও হয়ে যাচ্ছে। কোন প্রোটিন কেমন হবে এইসব তথ্য থাকে আমাদের জিনগুলোতে। তাই, জিনের পরিবর্তন প্রোটিনকেও প্রভাবিত করে। এই পরিবর্তনের ফলে যে বাটারফ্লাই ইফেক্ট শুরু হয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত তার ফলাফল মোটামুটি একই। লাগামছাড়া ভাবে কিছু কোষ বিভাজিত হচ্ছে, দেহের বিভিন্ন প্রান্তে দুষ্ট কোষগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে,অন্যান্য টিস্যুকে আক্রমন করছে, এবং হ্যা ব্যাপারটা খুবই ভয়ংকর।

জিনের এই পরিবর্তনকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে মিউটেশন। দুই ধরনের জিনে মিউটেশনের কারনে ক্যান্সার হয়, একটাকে বলে অনকোজিন, আরেকটাকে বলে টিউমার সাপ্রেসর জিন।
তবে আসলে মিউটেশন হবার পরে একে অনকোজিন বলে, এর আগে এর নাম প্রোটো-অনকোজিন। প্রোটোঅনকোজিন থাকা অবস্থায় এরা স্বাভাবিক জিনের মতই আচরন করে যার কাজ হচ্ছে এমন প্রোটিন তৈরি করা যা কোষের বিকাশ এবং বিভাজনে সাহায্য করে। কিন্তু একটা মিউটেশন, এদেরকে পাগল করে দেয় যে আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানো যায়না। কোষের মধ্যে এরা ক্রমাগত চেচামেচি করতে থাকে ‘বড় হ-বিভাজিত হ!, বড় হ-বিভাজিত হ!’।

আর মিউটেশনের ফলে এই জিন যে প্রোটিন তৈরি করার কথা তার আকৃতি যায় বদলে, আর সে এমন একটা অবস্থায় আটকে যায় যে ক্রমাগত কোষে বড় হবার সংকেত দিতে থাকে। এই নতুন আকৃতির কারনে, অন্যান্য যেসব প্রোটিনের কথা ছিল কাজ শেষ হলে এদের আটকানোর- তারাও চিনতে পারেনা। তাই কোষগুলো ক্রমগত বড় হয়ে বিভাজিত হতে হতে একটি টিউমারে পরিতন হয়।
‘টিউমার সাপ্রেসর’ নাম থেকেই বুঝা যায় এর কাজ হলো বিপথে যাওয়া কোষগুলোকে রুখে দেওয়া। সকল জিনের মত আমাদের প্রতিটা কোষেও দুই কপি করে টিউমার সাপ্রেসর জিন থাকে। যদি এক কপিতে কোন কারনে মিউটেশন হয়ে কাজ করা বন্ধ করে দেয় তখনো অন্য কপি ঠিকই কাজ করতে থাকে। দেখা গেছে যে একই লোকাসে অবস্থিত দুটি টিউমার সাপ্রেসরের যেটিতে মিউটেশন হয় সেটি প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, কিন্তু একই লোকাসে অবস্থিত অনকোজিনে মিউটেশন হলে সেটি হয়ে যায় প্রকট, এবং অন্য কপিকে আর সুস্থভাবে কাজ করতে দেয়না। যাই হোক, ক্যান্সারের প্রবৃত্তিই হল সব রকম প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থার ফাঁক গলে বের হয়ে যাওয়া। কখনো এমনও হতে পারে যে দুটো কপিতেই মিউটেশন হলো, কিংবা একটি কপিতে মিউটেশন হলেও অন্য সুস্থয় কপিটা কোন কারনে হারিয়ে গেল। তখন আর টিউমারকে আটকানোর মত কেউ থাকেনা।
এখানেই শেষ নয়, একটা দুটো মিউটেশন হলেই তা ক্যান্সার হয়ে যায়না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোষের নিজস্ব মেরামত ব্যাবস্থা ডিএনএ এর ছোটোখাটো মিউটেশনগুলোকে ঠিক করে নিতে পারে, কিংবা খারাপ অবস্থায় চলে গেলে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা আক্রান্ত কোষটিকে ধ্বংস করে ফেলে। একটা সুস্থ কোষকে ক্যান্সারে পরিনত হবার জন্য কমপক্ষে ৫ থেকে ৬ টা মিউটেশনের শিকার হতে হয়। সাম্প্রতিক একটি গবেষয়নায় দেখা গেছে ‘মিউটেশন অর্ডার’ অর্থাৎ কোন জিনের মিউটেশন আগে কোন জিনের মিউটেশন পড়ে হলো সেটাও ক্যান্সারের তীব্রতাকে প্রভাবিত করে। আমাদের দেহের স্বাভাবিক কোষগুলো প্রতিবার বিভাজিত হবার সময় এর ক্রোমোজোমের এক প্রান্ত ছোট হতে থাকে। একসময় কোষটি মরে যায়, এবং নতুন সুস্থ কোষ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। কিন্তু, ক্যান্সার কোষ এই ব্যাবস্থাকে ঠকিয়ে নিজের ক্রোমোজোমকে খুব করে আগলে রাখে। যার কারনে, ক্যান্সার কোষগুলো বলা যায় অমর হয়ে যায়।
যেহেতু প্রতিটা টিউমার ভিন্ন পথ অবলম্মন করে বিকশিত হয়, এটা চিকিৎসক এবং গবেষকদের জন্য কঠিন যে কোন পথকে আসলে টার্গেট করতে হবে। তাহলে কোন কোন উচ্ছন্নে যাওয়া জিনের কারনে টিউমার হয়েছে সেটাকে না জেনে কিভাবে এর বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেবেন?
একটা উপায় হতে পারে ছুরি নিয়ে টিউমারটি ঘ্যাঁচ করে ফেলা। কিন্তু সেটা তো সব সময় সম্ভব হয়না, আবার অনেক ক্ষেত্রে কেটে ফেলার পরেও টিউমার ফিরে আসে।
অনেক দিন ধরে ক্যান্সার চিকিৎসার সবচেয়ে ভালো সমাধান ছিল, দেহে কিছু একটা প্রয়োগ করা যা সমস্ত দ্রুত বিভাজনশীল কোষকে আক্রমন করবে। যেমন কেমোথেরাপী কিংবা রেডিওথেরাপী। রেডিওথেরাপীতে এমন ধরনের তেজস্ক্রিয়তা প্রয়োগ করা হয় যা কোষের ডিএনএ কে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। কিন্তু, সমস্যা হলো এই তেজস্ক্রিয়তা আশেপাশে সুস্থ কোষেরও ক্ষতি করে। তাই চিকিৎসকরা প্রয়োগ করার সময় খুব চেষ্টা করেন যাতে যথাসম্ভব কম ক্ষতি হয়। কেমোথেরাপী রয়েছে একাধিক ধরনের। তবে এরা যেহেতু রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়, এদের কারনে সারা দেহ প্রভাবিত হতে পারে। কিছু কিছু কেমো ডিএনএর গাঠনিক এককের ছদ্মবেশে থাকে। ক্যান্সার কোষ বিভাজিত হবার সময় তা নতুন ডিএনএ সূত্রক তৈরি করে এবং এদেরকে নতুন ডিএনএ তে যুক্ত করে ফেলে, কিন্তু সেই ডিএনএ আর সঠিক কার্যক্ষম থাকেনা। অনেকটা বিষটোপ দিয়ে শত্রুনাশের মত ব্যাপার। কিছু কিছু কেমো আবার কোষের অন্তঃকংকালকে নষ্ট করে দেয়। এর ফলে কোষটি আর বিভাজিত হতে পারেনা।
কেমো থেরাপী ক্যান্সারের বৃদ্ধি দমাতে পারলেও আমাদের দেহে প্রচুর সুস্থ কোষও আছে যাদের বিভাজিত হওয়া প্রয়োজন। যেমন চুলের ফলিকল বিভাজিত না হলে চুলের বৃদ্ধি হবেনা, আবার হজমের সময় নিঃসৃত এসিডের কারনে অন্ত্রের আস্তরনের যে ক্ষয় হয় সেটাও পুরন দরকার। এই কারনেই কেমো থেরাপীর ফলে চুল পড়ে যায়, হজমে সমস্যা দেখা যায়। এরকম হাজারো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াকে সাথে নিয়ে কেমো থেরাপী কাজ করে। ক্যান্সার রোগীর শারীরিক কষ্টের পাশাপাশি প্রচন্ড মানসিক চাপেরও সৃষ্টি করে, তাই ন্যাড়া মাথার কাউকে দেখে মজা করার আগে সবসময় খেয়াল করবেন তার চোখে ভ্রু আছে কিনা।


ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে অস্ত্রটিকে বিজ্ঞানীরা কয়েক বছর ধরে উন্নত করার চেষ্টা করে আসছেন তা হল জিনোম সিকোয়েন্সিং। এই প্রকৃয়াটি এখন এতটাই দ্রুত আর সস্তা যা দশ বছর আগেও শুধু স্বপ্নেই সম্ভব ছিলো। আর এখন এটা সরাসরি রোগীদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।
বর্তমানে কয়েক দিনের ব্যাবধানে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার কোষের জিনোম সিকোয়েন্স করে তার কোথায় এবং কিভাবে মিউটেশন ঘটেছে তা বের করা সম্ভব। এই তথ্য ব্যাবহারের মাধ্যমে কোন সর্বগ্রাসী ব্যাবস্থা গ্রহন ছাড়াই, পার্সোনালাইজড মেডিসিন দিয়ে নির্দিষ্ট ব্যাক্তির, নির্দিষ্ট ক্যান্সারের জন্য চিকিৎসা সম্ভব।
যে দুটো বড় প্রজেক্ট এই পদ্ধতি নিয়ে গবেষনায় নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা হল ১। ক্যান্সার জিনোম প্রজেক্ট, ২। ক্যান্সার সেল লাইন এনসাইক্লোপিডিয়া।
তারা নানা ধরনের ক্যান্সার কোষের বিপরীতে বিভিন্ন ধরনের ওষুধের প্রভাব পরীক্ষা করেছে। গবেষকরা দেখেছেন যে কিছু কিছু ওষুধ বিশেষ বিশেষ ক্যান্সার কোষের বিপরীতে ভালো কাজ করে। তারা মিউটেশনের ধরনের উপর ভিত্তি করে কোন ওষুধের কার্যকারীতা সম্পর্কে অনুমান করতে পারেন। তাই, ক্যান্সারের জন্য ওষুধ নির্বাচন এখন আর অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মত নয়, অন্তঃত তত্ব সেটাই বলে।
ক্যান্সার প্রতিরোধে আরেকটি কার্যকর অস্ত্র হতে পারে ন্যানোটেকনোলজি। আমরা সবাই জানি ন্যানোটেকনোলজি কি। ১ থেকে ১০০ ন্যানোমিটার স্কেলে যেই টেকনোলজি কাজ করে সেটাই অল্প কথায় ন্যানোটেকনোলজি। বেশির ভাগ সূক্ষ জৈবিক প্রকৃয়া এবং যেসব প্রকৃয়া ক্যান্সারের কারন হতে পারে সেগুলোও ন্যানোস্কেলে সংঘটিত হয়। তাই ন্যানোটেকনোলজির মাধ্যমে ক্যান্সার শনাক্তকরন থেকে শুরু করে নিরাময় পর্যন্ত সকল পর্যায়ই বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের সুবিধা পাওয়ার কথা।
ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য বায়োপসি করার আগে সাধারনত ইমেজিং কিংবা স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে প্রাথমিক ধারনা নেওয়া হয়। ন্যানোটেকনোলজি দুটো পদ্ধতিকেই আরো দক্ষ করে তুলতে পারে। যেমন ইমেজিং এর কথা যদি বলে, এর মাধ্যমে তাৎক্ষনিক ভাবে তখনই ক্যান্সার নির্ণয় করা যায় যদি কিনা বিপুল সংখ্যক কোষের ক্যান্সারে রূপান্তরের কারনে টিস্যুতে দৃষ্টিগ্রাহ্য কোন পরিবর্তন আসে। তবে ততক্ষনে হয়তো হাজার হাজার ক্যান্সার কোষ এদিক ওদিকে ছড়িয়ে গেছে। আবার দেখা গেলেও সেটা কতটা মারাত্নক সেটা বুঝার জন্য বায়োপসি ছাড়া উপায় নাই। তো ইমেজিং কে কার্যকর করার জন্য দুটি জিনিস দরকার, এমন কিছু যেটা একদন খাপে খাপ ক্যান্সার কোষকে চিনে নিতে পারবে এবং স্ক্যানিং ডিভাইসকে চেনাতে সাহায্য করবে। দুটোই ন্যানোটেকনোলজির দ্বারা অর্জন করা সম্ভব। যেমন যেসব অ্যান্টিবডি ক্যান্সার কোষের রিসেপ্টরের সাথে যুক্ত হতে পারে তাদেরকে ন্যানো আকারের ধাতব অক্সাইডের গায়ে লেপে দিলে তারা MRI কিংবা CT Scan এ স্পষ্টতর সংকেত তৈরি করতে পারে।
ন্যানোটেকনোলজির ভিত্তিতে যেসব ওষুধ তৈরি করা হচ্ছে সেগুলো সাধারনের তুলনায় বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ভালো কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ছে। যেমন এসবের অর্ধায়ু, স্থায়ীত্ব, আক্রান্ত কোষ চেনার ক্ষমতা অধিক এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ন্যানোপার্টিকেল ব্যাবহার করে মাল্টিড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেম তৈরির চেষ্টা করছেন, যেগুলা দ্রুত পরিবর্তনশীল ক্যান্সারের বিপক্ষে শক্তিশালী ব্যাবস্থা নিত সক্ষম।
যাই হোক, ক্যান্সার নিয়ে আসলেই অনেক কাজ হচ্ছে সারা বিশ্বে। গুগল ট্রেন্ডে গিয়ে যদি ক্যান্সার এবং এইডস এই দুটি রোগের নাম সার্চ আইটেম হিসেব দেন তাহলে এরকম একটি গ্রাফ পাবেনঃ

না, এটা কিন্ত এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নয় বরং ইন্টার্নেটে এদের জনপ্রিয়তার একটা তুলনা। যদিও এইডস রোগটি কম ভয়ানক নয়, ইন্টার্নেটে এর জনপ্রিয়তা যে কারনেই হ্রাস পাক- ক্যান্সার কিন্তু বিগত কয়েক বছরে স্থিতিশীল অবস্থায় আছে। তো আমরা ধরে নিতেই পারি সামাজিক নেটোয়ার্ক, ব্লগ ও নিউজপোর্টাল গুলো ছাড়াও বৈজ্ঞানিক জার্নালগুলোতেও ক্রমাগত এই শব্দটি বারবার এসেছে। তবে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো যে ধরনের অগ্রগতি সাধন করেছে, আমরা তার কতটা আমদানী করতে পেরেছি, আমাদের ক্যান্সার আক্রান্তরা কেমন সেবা পাচ্ছের সেটা ভাবার বিষয়। ২০১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের মধ্যে ক্যান্সার আক্রান্ত প্রায় ১৫ লক্ষ, যেখানে আমেরিকাতে এখন প্রতি ৩ জনে মাত্র ১ জন ক্যান্সারে আক্রান্ত! এত বিশাল সংখ্যক আক্রান্ত জনগোষ্ঠী মানেই বিশাল একটা ব্যবসা। তাই রথী-মহারথীদের ক্যান্সারে আক্রান্ত মানুষের জন্য নতুন নতুন চিকিৎসা উদ্ভাবন ও প্রদানের মাধ্যমে সংবাদপত্রের হেডলাইন হতে ও টাকা কামাতে যতটা উৎসাহ, ততটা কি পুরোপুরি নিরাময় লক্ষ্যে কাজ করাতে আছে?
তথ্যসূত্রঃ
১। Mutation order reveals what cancer will do next by Andy Coghlan, New Scientist Magazine.
২। nano.cancer.gov.
৩। Fighting Cancer with Nanomedicine by Dean Ho, The Scientist Magazine.
৪। Syed Md Akram Hussain, Comprehensive update on cancer scenario of Bangladesh, South Asian Journal of Cancer.
৫। The Cancer Industry is Too Prosperous to Allow a Cure By John P. Thomas, The Health impact News.

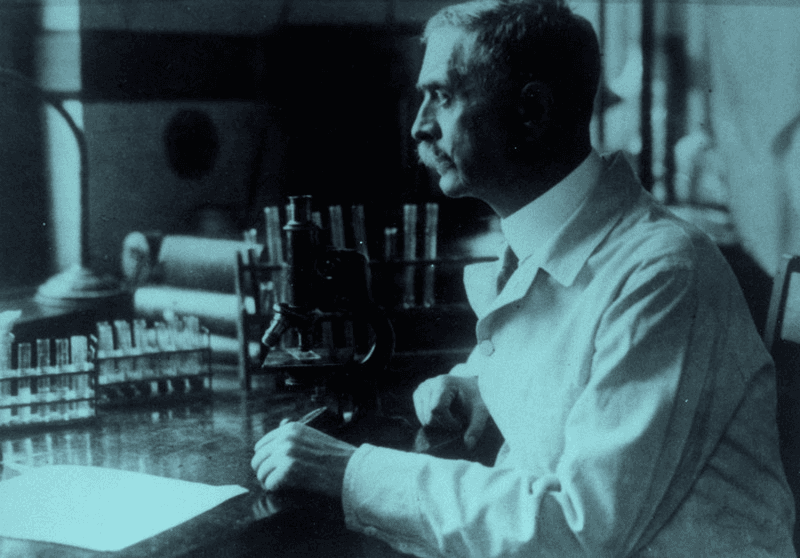


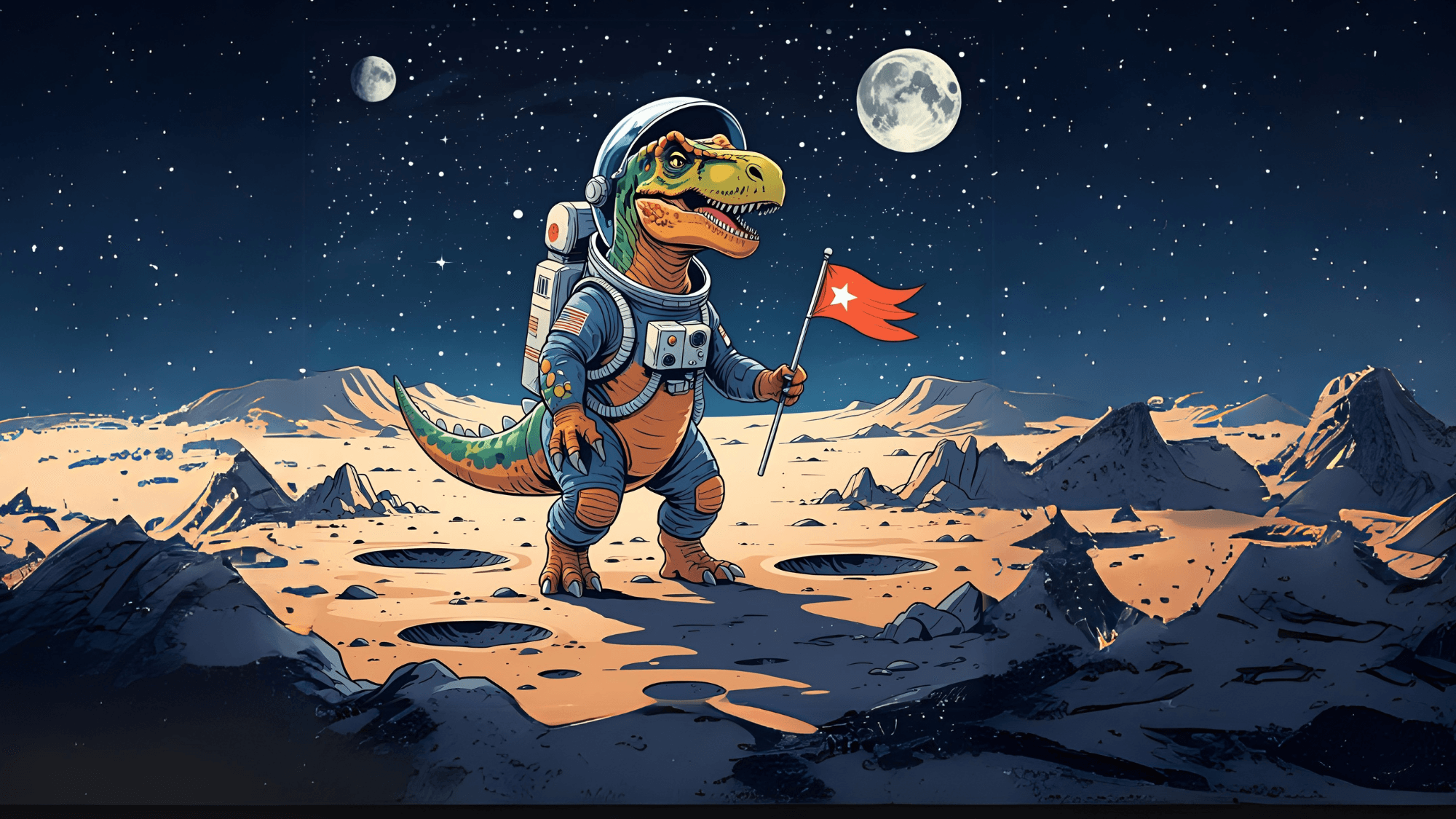
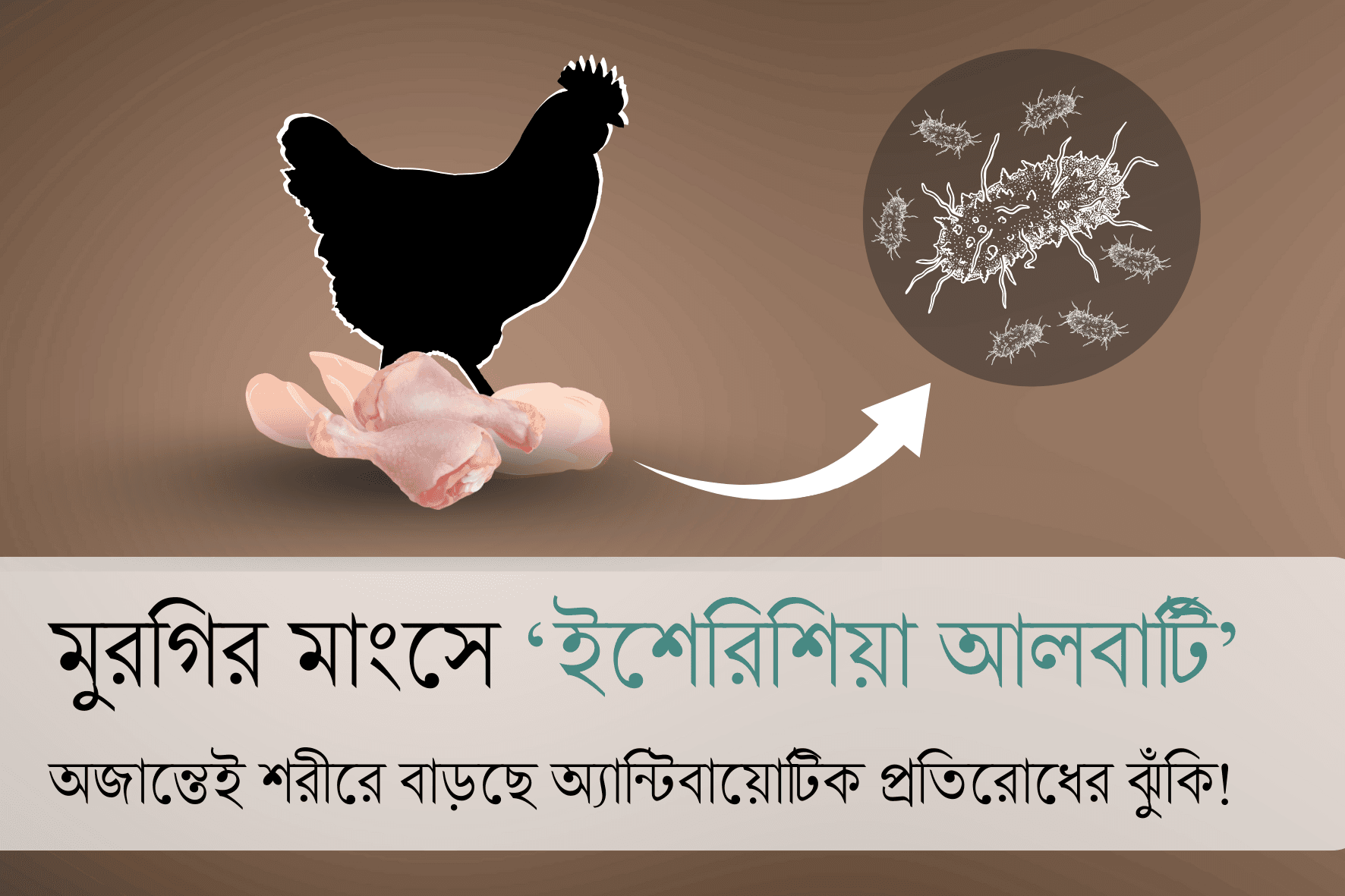


Leave a Reply