জীবনের উদ্ভব কিভাবে হলো বুঝতে হলে আমাদের প্রচলিত ধারণা বদলিয়ে প্রাণকে আণবিক শক্তির প্যাটার্ন হিসেবে দেখার দরকার হতে পারে
১.
১৯৮৩ সালে গ্লাসগোতে এক উষ্ণ বসন্তের বিকেলে যখন তার এগার বছর বয়সী ছেলে একটি খেলনা ভেঙে ফেলে, তখন মাইক রাসেল তাঁর অনুপ্রেরণার মুহূর্তটি খুঁজে পান। ওই খেলনাটি ছিলো একরকমের রাসায়নিক বাগান। জিনিসটা মূলত প্লাস্টিকের একটি ছোট ট্যাঙ্ক। সেখানে একটি খনিজ দ্রবণে স্ফটিক-বীজ রাখা হলে স্টেলেগমাইট[১]-সদৃশ লতানো টেনড্রিল[২] বেড়িয়ে আসে। বাইরে থেকে এসব টেন্ড্রিল দেখতে নিরেট মনে হয়। তবে খেলনটি ভেঙে যাওয়ার পর এরা তাদের প্রকৃত গঠন উদ্ঘাটন করলো: প্রতিটি টেন্ড্রিইল আসলে অজস্র ফাঁপা নলের জালিকার সমাহার। অনেকটা পানীয় খাওয়ার স্ট্র-এর বান্ডিলের মতো।
রাসেল ছিলেন একজন ভূবিজ্ঞানী। সে সময় তিনি সম্প্রতি আবিষ্কৃত অন্যরকমের শিলার গঠন বোঝার চেষ্টা করছিলেন। শিলাটি বাইরের দিকে নিরেট হলেও ভেতরে ফাঁপা নল দিয়ে ভর্তি। তাদের পাতলা দেয়াল আণুবীক্ষণিক কুঠরি দিয়ে ঝাঁঝরা করা। রাসেলের মনে হলো এই অদ্ভূত শিলা অবশ্যই কোন বিরল তরলের দ্রবণে তার ছেলের খেলনা টেন্ড্রিলের অনুরূপ কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। এ থেকে তিনি এক নতুন ভূতাত্ত্বিক প্রপঞ্চের অবতারণা করেন। তা হলো: সাগরতলে উষ্ণতরলের হটস্পট রয়েছে যেখানে খনিজ-সমৃদ্ধ পানি পৃথিবীর ভেতর থেকে বের হয় এসে চারপাশের ঠান্ডা পানিতে গিয়ে থিতিয়ে পড়ে। এ প্রক্রিযায় তৈরি হয় সুউচ্চ রাসায়নিক বাগান, যেখানে ফাঁপা শিলা সাগরতল হতে উপরের দিকে লম্বা হতে থাকে।
অন্তর্দৃষ্টির উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত এ প্রপঞ্চটি তখন বিশাল একটি উল্লফন ছিলো। এটি খুব শীঘ্রই রাসেলকে এর চেয়েও বিদঘূটে চিন্তার দিকে নিয়ে যায়। রাসেল বলেন, ‘হঠাৎ করে আমার মনে হলো এসব শিলা থেকেই প্রাণের উদ্ভূত হয়েছে। বহু বছর পর অন্যরা আমাকে বলা শুরু করলো যে ভাবনাটা অদ্ভুত ছিলো। তবে আমার কাছে ভাবনাটা বিস্ময়কর ছিলো না। আমি আসলে ভূতত্ত্ববিদ হিসেবে যা জানি তার আলোকে অন্য একটি বিষয় নিয়ে ভাবছিলাম। প্রাণের উদ্ভব নিয়ে গবেষণা করার জন্য আমি চিন্তাটা শুরু করি নি, কিন্তু ধারণাটি আমার কাছে সংশয়ের উর্ধে বলে মনে হয়েছিলো।‘
প্রাণ-উদ্ভবের গভীরতম ধাঁধাটি হলো হলো শক্তি সমস্যা। রাসেল সংশায়তীত ছিলেন যে তাঁর অনুকল্পিত রাসায়নিক বাগান এই ধাঁধার সমাধান করতে পারবে। এখনকার মতো সে সময়েও প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কিত অনেকগুলো তত্ত্বের শেকড় ছিলো চার্লস ডারউইনের ‘উষ্ণ ক্ষুদ্র পুকুর’ বিষয়ক ধারণায়। উষ্ণ পুকুরের ধারণাটি ছিলো এমন – আদিম পৃথিবীর জলাশয়ে উত্তাপ, সূর্যালোক বা বিদ্যুৎ চমকের শক্তিতে অজৈব বস্তু সক্রিয় হয়ে জটিল অণু তৈরি করে। পরবর্তীতে ঘটনাপরম্পরায় এরা নিজেদের প্রতিলিপি তৈরি করা শুরু করে। দশকের পর দশক ধরে প্রাণের-উদ্ভব বিষয়ক অধিকাংশ গবেষণার মূল কেন্দ্র ছিলো কিভাবে এ রকমের স্বপ্রতিলিপিকারী রসায়নের উদ্ভব হতে পারে। তবে এসব গবেষণা অন্যান্য মৌলিক প্রশ্নের দিকে ভ্রুক্ষেপ করে নি – যেমন প্রথম প্রাণ বৃদ্ধি, প্রজনন ও অধিকতর জটিলতার দিকে বিবর্তিত হওয়ার জন্য কিভাবে শক্তি সংগ্রহ করতো।
তবে রাসেলের মনে হয়েছিলো প্রাণের উদ্ভব ও এর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস এ দুইটি আসলে একই বিষয়। এরা একে অপরের সাথে অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। বর্তমানে নাসা-র জেট প্রপালশন পরীক্ষাগারে কর্মরত এই ভূবিদ তাঁর জীববিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত সহকর্মীদের বিপরীতে একেবারে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে প্রাণের উদ্ভব সমস্যাটি নিয়ে ভাবলেন। রাসেল বুঝতে পারলেন যে সাগরতলে রাসায়নিক বাগান এক জায়গায় একই সাথে শক্তি ও পদার্থের অনর্গল প্রবাহ সরবরাহ করবে। এরকম পরিবেশ যে শুধু স্ব-প্রতিলিপিকারী বিক্রিয়া সংঘটনের জন্য সহায়ক তাই নয়। একই সাথে নতুন উদ্ভূত জীবের জন্য খাবারের উৎস সরবরাহকারীও বটে। প্রাণের উদ্ভব পর পর ঘটে যাওয়া অনেকগুলো রাসায়নিক ঘটনার উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল। এ ঘটনাগুলো ধাপে ধাপে উদ্ভূত প্রাণকে অধিকতর জটিলতার দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু পর পর ঘটবার ক্ষীণ সম্ভাবনা নিয়ে গবেষকরা দীর্ঘদিন ধরে অস্বস্তিতে ছিলে। তবে শুরুতেই শক্তির সমস্যাটি বিবেচনা করে রাসেল ভাবলেন তিনি এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারবেন। তাঁর মতে, জটিল প্রাণের উত্থান অসম্ভব নয়, বরং অবশ্যম্ভাবী।
রাসেলের ‘শক্তিই-প্রথম’ পরিপ্রেক্ষিতটি প্রায় তিন দশক ধরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। বর্তমানে এ দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে: ভূবিজ্ঞান, জিনোমিকস ও আণবিক জীববিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার তাঁর এই অনুকল্পকে নতুন প্রত্যয় এনে দিয়েছে। এই পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাণ আসলে কি – এ সংজ্ঞায় নতুন পরিপ্রেক্ষিতের আবির্ভাব হয়েছে, যা একে সমগ্র বিশ্বজগতের পরিসরে একটি উন্নত অবস্থানে নিয়ে গেছে। রাসেল প্রাণের উদ্ভবের ভিত্তি দেখছেন সেই সব মূলনীতির মধ্যে যা গ্যালাক্সি, গ্রহসমূহ ও টর্নেডোর সৃষ্টি পরিচালনা করে। তিনি যুক্তি দেন যে জীবন কোন খাপছাড়া খামখেয়ালী ঘটনা নয়। বরং সুদূরপ্রসারিত একটি ভৌত আখ্যানের মধ্যে সমন্বিত অংশ। তিনি বলেন, ‘(প্রাণ হলো) সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বে শক্তির নিরবচ্ছিন্ন ধারার একটি অংশ মাত্র‘।
ভিডিও: রয়েস সোসাইটিতে ‘Vital Question’ বইয়ের লেখক ও গবেষক নিক লেনের বক্তৃতা। তিনি এখানে প্রাণের উদ্ভব ও বিবর্তনে শক্তির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন।
২.
পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম উদয় কিভাবে হলো তার প্রত্যক্ষ কোন নজির না থাকলেও আমাদের জিন ও জৈবরসায়নের মধ্যেই লুকায়িত আছে আমাদের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার আলামত। ১৯৫৩ সালে ডিএনএ-র গঠন আবিষ্কার ও পরবর্তীতে অণুপ্রাণবিজ্ঞানের উত্থান বিজ্ঞানীদের একটি আতস কাঁচ দেয় যার মাধ্যমে তারা সে মহাসৃষ্টির কাহিনীটি পড়তে পারেন। সকল তথ্য-সাবুদ একটি সাধারণ পূর্বপুরুষকে নির্দেশ করে। এ পূর্বপুরুষ ছিলো এমন একটি জীব যা সেই আদিম নরকসম পৃথিবীতে সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগে বেঁচে থেকে নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে সফল হয়েছিলো। এ সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকেই জীবন-বৃক্ষের কান্ড ও ডালপালা অঙ্কুরিত হয়।
ডিএনএ কেন্দ্রিক মনোযোগের সাথে সাথে সমসাময়িক গবেষণায় স্বপ্রতিলিপিকারী অণুদের রসায়ন বিষয়ক একধরণের জড়তা চলে আসে। এর ফলে সেসব স্বপ্রতিলিপকারী অণু তৈরি করতে যে শক্তি দরকার ছিলো সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করা হয় নি। তাই প্রাণের উদ্ভব বিষয়ক গবেষণা মূলত হয়ে পড়ে ডিএনএ যেসব প্রাচীন-অণু থেকে পরিবর্তিত হয়েছে তাদের অনুসন্ধান অভিযান। ১৯৬০-এর দশকে গবেষকরা আরএনএ-বিশ্বের ব্যাখ্যায় মোটামুটি ঐক্যমতে আসে। এ মতানুসারে, প্রাণের শুরু হয়েছিলো একটি আরএনএ-বিশ্বে। আরএনএ-কে বলা যায় ডিএনএ-র রাসায়নিক চাচাতো ভাই। সেই আরএনএ-বিশ্বে আরএনএ অণুসমূহ বংশগতির তথ্য ধারণ করার সাথে সাথে জীবনের বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটনের জন্য সাহায্য করতো। আরএনএ যে বংশগতির তথ্য ধারণ করতে পারে, এ বিষয়টি তখনই বিজ্ঞানীরা জানতেন। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে একটি আবিষ্কারের মাধ্যমে এই আরএনএ-বিশ্বের অনুকল্প বেশ জোরদার হয়। এ আবিষ্কারে দেখা যায় আরএনএ অন্য কোন কোন প্রোটিন বা অণুর সহায়তা ছাড়া নিজেই বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া পরিচালিত করতে পারে। বিজ্ঞানীদের মনে হচ্ছিলো যে আরএনএ অণু দিয়ে একটি রাসায়নিক ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব বলে যা নিজেকে তৈরি করে স্বঅণুলিপি করতে পারে।
বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, আদিম পৃথিবীতে আরএনএ কোনভাবে লিপিডের বুদবুদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। লিপিড হলো তৈলাক্ত অণু যা আধুনিক কোষের কোষপর্দায় থাকে। লিপিডের বুদবুদ নিজে নিজেই বাড়তে থাকে ও একসময় বিভক্ত হয়ে একাধিক বুদবুদ তৈরি করতে পারে। ফলে এর মধ্যে কেবল সেরা আরএনএ অণুলিপিকারকরা টিকে থাকে ও সংখ্যাবৃদ্ধি করতে থাকে। এক সময় এই আদিম সত্ত্বাগুলো মধ্যে কোন কোনটি সাংকেতিকভাবে সরল প্রোটিন নির্মাণের সামর্থ্য লাভ করে। এ সামর্থ্য থেকে পরবর্তীতে বিভিন্ন বিপাকীয় (মেটাবলিক) পথ তৈরি হয় যা পরিবেশ থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে পারে। তারপর বংশগতীর তথ্য সংরক্ষণের দায়িত্বটি আরএনএ থেকে ডিএনএ-র ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। এভাবে জীবন হিসেবে আমরা যা বুঝি তার উদ্ভব হয়।
তবে প্রাণের উদ্ভব রহস্য সমাধানে আধুনিক জীবের মধ্যে আরো একটি নজির বর্তমান। এটি ডিএনএ-র চেয়ে অস্পষ্ট, কিন্তু বিশ্বজনীন। তা হলো, তড়িৎ-আধান দিয়ে আহিত অণু অদল-বদল করে কোষ যেভাবে শক্তি উৎপাদন করে সে পদ্ধতি। এ জটিল পদ্ধতির নাম হলো কেমি-অসমোসিস বা রাসায়নিক অভিস্রবণ। খামখেয়ালি ব্রিটিশ বায়োকেমিস্ট পিটার মিশেল ১৯৬১ সালে এ পদ্ধতির প্রস্তাব করেন। রাসায়নিক অভিস্রবণে ডিএনএ জেনেটিক কোডের মতো সাংকেতিক যথার্থতা অনুপস্থিত হলেও এর মাঝে আদিম বিশৃঙ্খলা বর্তমান – যে বৈশিষ্ট্য একে রহস্য উন্মোচনের উপযোগী করে তোলে।
রাসেলের মতে ডিএনএ- বা আরএনএ-র মতো কোন কিছুর আসার আগে অবশ্যই শক্তির পূর্ববর্তী ভূমিকা থাকবে। তাই রাসায়নিক-অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার উদ্ভব কিভাবে হলো তা প্রাণের আবির্ভাব রহস্যের সমাধানে আমাদের সাহায্য করতে পারে। আমাদের কোষের গভীরে মাইটোকন্ড্রিয়া নামক অঙ্গাণুর মধ্যে রাসায়নিক-অভিস্রবণ সংঘটিত হয়। অধিকাংশ কোষে শত শত বা হাজার হাজার সংখ্যায় এই আণুবীক্ষণিক অঙ্গাণুটি বিরাজ করে। মাইটোকন্ড্রিয়া খাদ্য থেকে রাসায়নিক শক্তি নিষ্কাশিত করে। তারপর আমরা যে অক্সিজেন শ্বাস-গ্রহণ করি, তার সাহায্যে এডিনোসিন ট্রাইফসফেট বা এটিপি (ATP) নামের এক অণুতে এ শক্তি সংরক্ষণ করে। ডিএনএ-র মতো এটিপিও প্রাণের জন্য অতিজরুরী অণু। এটিপি হলো কোষীয় শক্তি-মুদ্রা যা খরচ করে আমরা বড়ো হই, নড়াচড়া বা চিন্তাভাবনা করি। আমাদের দেহভরের একাংশ প্রতিদিনই এ মুদ্রায় রূপান্তরিত হয়।
মাইটোকন্ড্রিয়ার ঝিল্লীতে শক্তির ধারা এক ধরনের বিদঘুটে আণবিক কল দিয়ে ভ্রমণ করে। এ আণবিক যন্ত্রটি এতোটাই বিস্তারিত যে তার খুঁটিনাটি বোঝাটা বেশ কঠিন। হাজারখানেক পরমাণু দিয়ে তৈরি অনেকগুলো প্রোটিন ধাপে ধাপে খাদ্য অণু থেকে পাওয়া উচ্চ-শক্তির ইলেকট্রনকে (e–) ফাঁদে ফেলে পরবর্তী প্রোটিনের কাছে হস্তান্তর করে। প্রোটিনের এ লম্বা শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের চলাচল একটি তড়িৎ-প্রবাহ তৈরি করে। এর মাধ্যমে মাইটোকন্ট্রিয়ার ঝিল্লির মাঝে অজস্র সংখ্যক চার্জিত প্রোটন (H+) জমা হয়। এখান থেকে প্রোটনের বের হয়ে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা হলো অন্য একটি অসাধারণ প্রোটিনের মধ্য দিয়ে, যার নাম এটিপি সিন্থেস। এটি অসাধারণ প্রকৌশলের ন্যানোমেশিন, যার রয়েছে আণবিক রোটার (চক্র), স্ট্যাটর (ধারক) ও শ্যাফট (অক্ষদন্ড)। এর মধ্য দিয়ে যখন প্রোটন ঝিল্লীর ভেতরে যেতে থাকে তখন তা জলচক্রের মতো ঘুরতে থাকে, সেকেন্ডে শতশতবার গতিতে, আর তৈরি হতে থাকে এটিপি।

প্রাণ-উদ্ভবের অণুলিপিকেন্দ্রীক তত্ত্ব এখনো রাসায়নিক-অভিস্রবণের সমান্তরাল উদ্ভবের কোন ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারে নি। কিন্তু রাসেল যুক্তি হলো তাঁর রাসায়নিক বাগান একটি প্রাকৃতিক পরিবেশ দেয়, যেখানে প্রাকৃতিকভাবে বিরাজমান প্রোটন-তারতম্য ব্যবহার করে শক্তি তৈরি করতে পারে এরকম অণুর উদ্ভব হওয়া সম্ভব। পৃথিবীর প্রাচীন সাগর সম্ভবত অম্লধর্মী ছিলো, তার মানে সেখানে উচ্চ ঘনত্বে প্রোটন থাকতো। অন্যদিকে সাগরতলের ফাঁটল থেকে বের হয়ে আসা উষ্ণতরল পানি সাধারণ ক্ষারীয় বৈশিষ্ট্যের, অর্থাৎ সেখানে প্রোটনের ঘনত্ব কম। প্রোটন-ঘনত্বের এই পার্থক্য সাগর থেকে শিলার মধ্যে একটি প্রাকৃতিক প্রোটন প্রবাহ তৈরি করতে পারে – যেখানে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রোটন শিলা-খনিজের গোলকধাঁধার মধ্যে চুঁইয়ে পরতে থাকে।
রাসেল মনে করেন, প্রোটন-তারতম্যে (proton gradient) ইলেকট্রন স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত শক্তি থেকেই সরল ধরনের বিক্রিয়া সংঘটন সম্ভবপর হয়েছিলো। প্রোটিনরা বিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে সাথে কোন কোষ আদিম এটিপি সিন্থেসের মাধ্যমে এই এই প্রোটন-ধারা ব্যবহার করা শুরু করে। সম্প্রতি পাওয়া জিনোমিক উপাত্ত এই ঘটনাক্রমকে সমর্থন করে। পৃথিবীর সকল জীবের এটিপি সিন্থেস অণুটি একই রকমের। কিন্তু যেসব প্রোটিন-শৃঙ্খল ব্যবহার করে প্রোটনকে ফাঁদে ফেলা হয় তারা এক রকমের নয়। এর মানে হলো, প্রথম দিকের কোষেরা কোষঝিল্লীতে প্রোটন-তারতম্য তৈরি করার ক্ষমতা অর্জনের আগেই পরিবেশে উপস্থিত প্রোটন-তারতম্য থেকে শক্তি সংগ্রহের জন্য বিবর্তিত হয়েছিলো। রাসেলের রাসায়নিক বাগান এ রকম প্রোটন-তারতম্যের যোগান দিতে পারে। পরবর্তীতে জীবকোষে নতুন ধরনের প্রোটিন বিবর্তিত হয় যারা নিজেরাই প্রোটন-তারতম্য তৈরি করতে সক্ষম। প্রক্রিয়াটি এমনই যা প্রাণের উদ্ভব কোথায় হয়েছিলো তার প্রমাণ মুছে ফেলে।
প্রাণের উদ্ভব গবেষণার মূলধারার বাইরে রাসেলের তত্ত্ব অবহেলিত হয়ে পড়ে ছিলো। তবে এ তত্ত্ব প্রথিতযশা জীববিজ্ঞানী বিল মার্টিনকে আকৃষ্ট করে। রাসায়নিক-অভিস্রবণ যে আরএনএ-র পূর্বে এসেছিলো এ বিষয়টি মার্টিনের বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যথার্থ মনে হয়। তিনি বলেন, ‘যখন আপনি একদল জীবকে নিরীক্ষা করেন – এক্ষেত্রে যা হলো আমাদের জানা সকল জীব – তাদের সকলের বর্তমান রূপের মধ্যে একটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। আপনি এই বৈশিষ্ট্যকে এদের সাধারণ পূর্বপুরুষের মধ্যে আরোপিত করেন। আর এই সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যটি হলো (প্রোটন) আয়ন–গ্রেডিয়েন্ট।‘
২০০৩ সালে কয়েকটি ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে রাসেল ও মার্টিন একসাথে রাসায়নিক-বাগান পটভূমির জীববৃত্তিক-প্রভাব খুঁজতে থাকেন। তাঁদের অনুকল্পের মূল কথা হলো প্রাণের আবির্ভাব মুক্তজীবি স্বত্ত্বা হিসেবে শুরু হয় নি যারা প্রাকৃতিক জৈবঅণু খেয়েদেয়ে সাগরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতো। বরং প্রাণের শুরু অনেকটা সাগরতলের শিলার খনিজ কুঠুরীতে জেঁকে বসা অধিবাসীর মতো ছিলো যারা নিজেদের খাবার নিজেরাই তৈরি করতো। শুরুর দিকে সাগরতলের ফাটল ছিলো ভুতত্ত্বের সরল স্থান যেখান থেকে গ্যাস ও দ্রবীভূত খনিজ বুদ্বুদের মতো বের হয়ে এসে ক্ষুদ্র কুঠুরিযুক্ত শিলা তৈরি করতো। তবে এসব শিলার ক্ষুদ্রকুঠুরীতে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটা শুরু করলো। সাগরের কার্বন ডাই-অক্সাইড এসব ফাটলের হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করা শুরু করলো। সাধারণ পরিস্থিতিতে এ বিক্রিয়া ঘটবে না। কিন্তু লোহা ও সালফারে সমৃদ্ধ শিলার প্রভাবক-ভূমিকায় ক্ষুদ্রকুঠুরীতে এই কুন্ঠিত-সহযোগীতা সম্ভব হলো। এই বিক্রিয়াগুলোর ফলে তৈরি হলো প্রাচীন বিপাকীয় পথের অন্যতম সদস্য এসিটাইল-কোএ-র (Acetyl-CoA) মতো বিভিন্ন জৈবঅণু।
রাসায়নিক বাগানের এই ‘বিস্তারিত’ অনুকল্প জীবনের উদ্ভব বিষয়ে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেয়। তা হলো কিভাবে আণবিক জৈব-এককগুলো যথেষ্ট ঘনীভূত হয়ে একে অন্যের সাথে বিক্রিয়া করে যুক্ত হয়। রাসেল বললেন যে সাগরতলের ফাটলের চারপাশে একটি তাপীয় তারতম্য (thermal gradient) তৈরি হয় যার বাহিরে ঠান্ডা ও কেন্দ্রে উষ্ণ। এই তাপীয় তারতম্য থার্মোফোরেসিস নামক একটি তাপীয়-পরিচলন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। থার্মোফোরেসিস বৃহৎ জৈব-অণুকে কুঠুরীতে আটকে ফেলে সুগার, অ্যামিনো এসিড, লিপিড ও নিউক্লিয়োটাইডের মতো জীবনের জৈব-ইট তৈরিতে উদ্দীপনা দিতে পারে। গভীর সাগরতলের ভীষণ চাপ ও ফাটল থেকে বের হওয়া উষ্ণ প্রস্রবণের উচ্চতাপে এধরনের জৈব-ইট একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে বৃহত্তর ও জটিল অণু গঠন করে।
রাসেল ও মার্টিনের অনুকল্প অনুসারে, এর পরপরেই বংশগতির উপাদান নির্মিত হওয়া শুরু করলো। এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন জটিল জৈব-অণুর ঘন সরবরাহের সুযোগ নিয়েছিলো নবনির্মিত বংশগতির উপাদান। স্বপ্রতিলিপিকারী রাসায়নিক ব্যবস্থা শিলার এক কুঠুরী থেকে অন্যটিতে ছিদ্র দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করলো। এসব ছিদ্রাকার-শিলা সমান তালে নতুন নতুন কুঠুরি বানাতে থাকলো আর নব্য-প্রাণের উপনিবেশ তৈরির অঞ্চলের আওতাও বাড়তে থাকলো। এখান থেকেই প্রথম কোষের উদয় ঘটে। রাসেলের মতে একমাত্র যৌক্তিক ব্যাখ্যা হলো: “প্রাণের উদ্ভব আসলে একটা ভূতাত্ত্বীক ঘটনা। এভাবে যদি আপনি বিষয়টা না দেখেন তাহলে আপনি একটি মনগড়া প্রাথমিক শর্ত তৈরি করে ফেলবেন।”
৩.
রাসেলের এই কুশলী ব্যাখ্যার সবচেয়ে বড় সমস্যাটা ছিলো তাঁর অনুমিত রাসায়নিক বাগানের অস্তিত্বের খোঁজ কেবল তাঁর কল্পনাতেই ছিলো। ১৯৭৭ সালে সাগরতলে এ ধরনের খনিজ কাঠামো আবিষ্কৃত হয়। এ ধরনের কাঠামো যে প্রাণের উদ্ভবের জন্য সাম্ভাব্য স্থান হতে পারে এমন আলোচনা তখন আরম্ভ হয়। তবে এ কাঠামোগুলোর ভীষণ আগ্নেয়গিরি-ধর্ম ও স্বল্পস্থায়িত্বের কারণে এ ভাবনা দ্রুতই মিইয়ে পড়ে। ১৯৯২ সালে বিখ্যাত প্রাণ-উদ্ভব গবেষক স্ট্যানলি মিলার ডিসকভার পত্রিকাকে বলেন যে এ ধরণে উষ্ণপ্রস্রবণ উদগরণকারী হইড্রোথার্মাল-ফাটল তত্ত্ব হলো পরাজিত, অভাগা। তিনি মন্তব্য করেন যে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার কোন কারণই খুঁজে পান না।
তারপর ২০০০ সালের এক শীতের সন্ধ্যায় একদল ভূতত্ত্ববিদ আর্গো-২ নামের একটি রিমোট-কন্ট্রোলড সাবমার্সিবল (এক ধরনের ডুবজাহাজ) নিয়ে শান্ত আটলান্টিক মহাসাগরের তলে নিমজ্জিত পাহাড়-এলাকা জরিপ করতে নামেন। সাবমার্সিবলটি সর্পিল কোরাল পেরিয়ে, সাগরের ফোটিক অঞ্চল পেরিয়ে, যেখানে সূর্যালোক ঝাপসা হতে হতে নিকষ কালো অন্ধকার শুরু হয়, তার তলে নেমে যায়। হঠাৎ সাবমার্সিবলের আলো খুব অপ্রত্যাশিত কোনকিছুকে আলোকিত করে: সাগরের মেঝে থেকে উপরের দিকে বাড়তে থাকা বহির্জাগতিক শৃঙ্গের গুচ্ছ, যাদের একেকটির উচ্চতা বিশ-তলা ভবনের মতো। এদের চূড়া থেকে চিমনী থেকে বের হওয়া ধোঁয়ার মতো উষ্ণ জলের চকচকে ধারা বের হয়ে আসছে। এই অদ্ভূতুড়ে জায়গায় এক কিম্ভূতকিমাকার বাস্তুসংস্থানের খোঁজ পাওয়া গেল। এখানে শামুক, কাঁকড়া ও খোলওয়ালা মাছ কিছু অণুজীবের উপর নির্ভর করে টিকে থাকে। দেখা গেলো সেসব অণুজীব সূর্যালোকের সাহায্য ছাড়াই ভূগর্ভের কাঁচামালকে প্রাণে পরিণত করে। রাসেলের ১৯৮৩ সালের ভাবনার সাথে মিলে যাওয়া এই উষ্ণপ্রস্রবণ-ফাটলে সমৃদ্ধ স্থানের নাম দেয়া হলো লস্ট সিটি। অবশেষে তাঁর রাসায়নিক বাগানের খোঁজ পাওয়া গেলো।
প্রাণের উদ্ভব যে রাসায়নিক বাগানে হয়েছে এ তত্ত্বের পক্ষে পরবর্তী পনের বছর ধরে আরো উপাত্ত জড়ো হতে লাগলো। অধিকাংশ জীববিজ্ঞানী মনে করেন যে বিশ্বজনীন প্রাণের সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিলো একটি অটোট্রফ (autotroph)। অর্থাৎ সেটি অজৈব পদার্থ থেকে নিজের খাবার নিজেই তৈরি করতে পারতো – যেমনটা বলেছিলেন রাসেল ও মার্টিন। এ বিষয়ে ২০১৫ সালের একটি জিনোমিক গবেষণা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে প্রত্যয়জনক প্রমাণ উপস্থাপন করে। প্রায় চল্লিশটি জিন নিয়ে করা এই গবেষণাটি জোড়গলায় প্রস্তাব দেয় যে প্রাচীনতম অণুজীবরা কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO2) ও হাইড্রোজেন (H) থেকে মিথেন (CH4) তৈরি করতো। এটি অন্য একটি ভূতাত্ত্বিক গবেষণার সাথে খাঁজে খাঁজে মিলে যায়, যেখানে প্রাচীন শিলায় প্রাপ্ত জৈব পদার্থে যে মিথেন দেখা যায় তা জৈব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে বলে প্রমাণিত।
প্রথম প্রাণের উষ্ণ ও পাথুরে উদ্ভবের কথা অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সমর্থিত। দশকের পর দশক অধিকাংশ জীববিজ্ঞানী ভাবতেন যে প্রাণ পৃথিবীর উপরিত্বকে তাপমাত্রার সীমিত গন্ডীর মধ্যেই বাঁচতে পারে। তবে প্রাণবৃক্ষের প্রাচীনতম কান্ডে যে প্রজাতি পাওয়া যায়, তাদের অধিকাংশই উষ্ণতা পছন্দ করতো এ ধরণের তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যেতে থাকে ২০০০-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। উচ্চ-তাপমাত্রার জীবেরা যে পৃথিবীতে প্রথম এসেছিলো, আর পরবর্তীতে ভূত্বকে বসবাসকারী জীবেরা মাঝারী তাপমাত্রায় বসবাসে বিবর্তিত হয়েছিলো – এ বিষয়টি এখন সম্ভব বলে মনে হয়। এছাড়া অণুজীব থেকে শুরু করে স্তন্যপায়ী প্রাণী সকলের মাঝেই কিছু কিছু প্রোটিন পাওয়া যায়। এসব প্রোটিনের কেন্দ্রে ক্ষুদ্র খনিজ-অণুর গুচ্ছ থাকে। এ বিষয়টি নির্দেশ করে যে আদিম জীবনের সাথে পাথরের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। শক্তি-চালিত প্রাণ খনিজ-গুটি থেকে উদিত হচ্ছে – রাসেলের এই ধারণাটা এখন আর অবিশ্বাস্য কিছু মনে হয় না।

৪.
প্রাণের উদ্ভব যে সাগরতলের রাসায়নিক বাগানে হয়েছে – এমন ভাবার পেছনে আরো গভীর কিছু কারণ আছে। প্রথম দেখায় মনে হবে প্রাণ পদার্থবিদ্যার নিয়ম অমান্য করছে। মহাবিশ্বের প্রবণতা হলো ক্রমাগত শৃঙ্খলা থেকে বিশৃঙ্খলার দিকে যাওয়া। গোছানো ঘর এলোমেলো হয়ে যায়, দূর্গ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়। এই বিশৃঙ্খলা এনট্রপি নামে পরিচিত যাকে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ সূত্র অনুযায়ী যে কোন প্রক্রিয়াতে মহাবিশ্বের সামগ্রিক এনট্রপি বাড়াবে। পরিবর্তন এমনভাবে বদলে দেবে যেন পূর্বের অবস্থায় পুনরায় ফেরত যাবে না – এমনটাই লিখেছিলেন জন আপডাইক তাঁর ‘অড্ টু এনট্রপি‘ কবিতায়। এর যৌক্তিক উপসংহার হল বস্তু ও শক্তি যখন সর্বত্র সমানভাবে বন্টিত হয় তখন আর কোন কিছুই ঘটতে পারে না – আপডাইক যাকে বলেছেন বিলুপ্তির সীলমোহর।
তবে প্রাণ এনট্রপির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অস্ট্রিয়ার পদার্থবিদ আরউইন স্রডিঞ্জার তাঁর একসেট সুদূরদৃষ্টি লেকচার-নোটকে What is Life? (১৯৪৪) নামের প্রভাবশালী বইয়ে রূপ দেন। এ বইয়ে তিনি প্রাণ কর্তৃক তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের আপাত-লঙ্ঘনের একটি ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন যে প্রাণ শক্তিকে কাজে লাগানোর একটি উপায় পেয়েছে যার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে এনট্রপি বাড়লেও স্থানীয়ভাবে এনট্রপি কমে যায়। এনট্রপির এই স্থানীয় অবনমনকে রেফ্রিজারেটরের সাথে তুলনা করা যায়। রেফ্রিজারেটর তড়িৎশক্তি ব্যবহার করে নিজেকে ঠান্ডা লাখলেও এর পেছনের কয়েল থেকে পরিবেশে অধিকতর তাপ ত্যাগ করে (ফ্রিজ কেন একটি এপার্টমেন্টকে ঠান্ডা করতে পারে না তার মূল কারণ এটাই)। প্রাণও একই রকম। প্রাণ শক্তি ব্যবহার করে নিজেকে স্থানীয়ভাবে সংগঠিত করে, কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর পরিমাণ তাপ বর্জ্য হিসেবে চারপাশে ত্যাগ করে। স্রডিঞ্জার উল্লেখ করেন প্রাণ ‘চারপাশ থেকে ক্রমাগত শৃঙ্খলতা চুষে নিয়ে বেঁচে থাকে‘।
বিশৃঙ্খলা থেকে এভাবে শৃঙ্খলার উদয়ের কথা চিন্তা করলে তা মূলত অসম্ভব বলে মনে হয়। প্রাণ কি বিশ্বসৃষ্টির কোন আকষ্মিক ঘটনা, নাকি প্রকৃতির নিয়মে খোদাই করা কোন বিষয়, জ্যোতির্জীববিদ্যার অন্যতম প্রধান প্রশ্ন। ব্রিটিশ জ্যোর্তিবিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আবির্ভাবকে তুলনা করেছেন কোন আস্তাকুঁড়ে সংঘটিত টর্নেডোয় অণুপরমাণু পুনঃসজ্জিত হয়ে বোয়িং ৭৪৭ উড়োজাহাজ তৈরির সাথে।
রাসেল এখানেও ভিন্নভাবে দেখেন। তিনি মনে করেন প্রাণের উদ্ভব বিশৃঙ্খলা–থেকে–শৃঙ্খলার উদয় বা এরকমের কোন সমস্যা নয়। বরং এটি মূলত শৃঙ্খলা–থেকে–শৃঙ্খলার উদ্ভব। তিনি বলেন, ‘আপনার কাছে শুরুতেই যদি সুসংগঠিত প্রারম্ভিক অবস্থা থাকে তাহলে সেখান থেকে অন্য যে কোন সংগঠিত অবস্থা পাওয়া সম্ভব‘। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রাণের আগে ভূতাত্ত্বিক শৃঙ্খলা এসেছে। প্রশ্ন হলো, একটি জটিল ভূতাত্বিক ব্যবস্থা থেকে কিভাবে জৈবিক জটিলতার উদয় হতে পারে। কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিজ্ঞানী রবার্ট হ্যাজেন মনে করেন এই অন্তর্দৃষ্টিটি বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানে রাসেলের অন্যতম মৌলিক অবদান। তিনি বলেন, ‘জীবনের উদ্ভব – যা হলো জটিলতার উদ্ভব – তা এর তুলনায় (অধিক) জটিল পরিবেশ ছাড়া ঘটতে পারে না।‘
জটিলতা ঠিক কোত্থেকে এলো তা বোঝার জন্য জন্য রাসেলের শক্তি-পরিচালিত মডেল সাহায্য করে। প্রায় এক শতাব্দী আগে বিজ্ঞানীরা বুঝতে আরম্ভ করলেন যে একটি অজৈব ব্যবস্থাও স্ববিন্যস্তকারী হিসেবে কাজ করতে পারে। এরকম স্ববিন্যস্তকারী ব্যবস্থা চারপাশ থেকে ‘শৃঙ্খলতা চুষে খায়‘। এই ধারণাটি ১৯৬০ সালে রুশ রসায়নবিদ ইলিয়া প্রিগগাইন বিধিবদ্ধ করেন। তিনি এসব স্ববিন্যস্তকারী ব্যবস্থাদের অপচয়কারী সংগঠন বলে ডাকতেন (dissipative structures)। এরকমের গঠন খুঁজে পাওয়া সহজ: বাথটাবের প্লাগ খুলে দিন আর দেখুন একটি ঘূর্ণি তৈরি হয়েছে। অভিকর্ষের টানে পানির অণু নিজেরাই একটি ছাঁদে মোচড় খেয়ে ঘূর্ণি তৈরি করেছে, যা তাদের পূর্বের অবস্থার এলোমেলো গতিবিধির তুলনায় সুবিন্যস্ত। যেহেতু এর ফলে পানি খুব দ্রুত নিষ্কাষিত হয়ে যায়, তাই এই ঘূর্ণি স্থানীয় এনট্রপির গঠন তৈরির মাধ্যমে সামগ্রিক এনট্রপি বাড়িয়ে তোলে। যদি বাথটাবটি শাওয়ার বা ট্যাপ খোলা রেখে ক্রমাগত পানি দিয়ে ভর্তি করা হয়, তাহলে এই ঘূর্ণিটি অসীম সময় ধরে টিকে থাকবে। অর্থাৎ যখন কোন ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে ক্রমাগত শক্তি প্রবাহিত থাকে, তখন এরকম আগ্রহোদ্দীপক ব্যাপারস্যাপার ঘটতে শুরু করে।
রাসেল মন্তব্য করেন, প্রাণ এধরণের ব্যবস্থার দলে পড়ে যারা শক্তিপ্রবাহের প্রতি উন্মুক্ত। এভাবে চিন্তা করলে তা প্রাণকে নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত করে।
বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে শক্তির বিপরীতে রসায়নকে গুরুত্ব দেয়া বিজ্ঞানীরা প্রভাব রেখেছেন। ১৯৫৩ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থী স্ট্যানলি মিলারের বিখ্যাত পরীক্ষা এই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতের জন্য অংশতঃ দায়ী। তিনি দুইটি গোলাকার ফ্লাস্ককে যুক্ত করেন যার একটিতে ছিলো পানি। এ পানি পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রকে অনুকরণ করে। অন্যটিতে কিছু সরল গ্যাসের মিশ্রণ ছিলো যা আদিম পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে থাকতো বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। মিলার তারপর গ্লাসের মধ্যদিয়ে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ প্রেরণ করেন – যাকে বজ্রপাতের ছোট সংস্করণ বলে ভাবা যায়। এক সপ্তাহের মধ্যে তরল হলুদ রঙে পরিণত হলো, তারপর গোলাপি, সব শেষে কড়া লাল রঙ ধারণ করলো। মিলার দেখলেন ফ্লাস্কের মধ্যে বিভিন্ন জৈব পদার্থের মিশ্রণ তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে অ্যামিনো এসিডও ছিলো। এ পরীক্ষায় তিনি বাতাস থেকে প্রাণের অন্যতম একক-ইট তৈরি করে ফেললেন।
খুব দ্রুতই মিলারকে টাইম পত্রিকার প্রচ্ছদে দেখা গেল। বিভিন্ন ট্যাবলয়েড পত্রিকা ল্যাব থেকে কৃত্রিম প্রাণ হামাগুঁড়ি দিয়ে বেরোচ্ছে এরকম গালগল্প ছাপতে লাগলো। অনেক রসায়নবিদ প্রাণ তৈরির জন্য প্রতিযোগীতা শুরু করলেন, অন্তত প্রাণ না হলেও জীবনের জরুরী রাসায়নিক পদার্থ তৈরির চেষ্টা করলেন। শুরুতে কিছু মনোমুগ্ধকর সাফল্য থাকলেও যেসব গবেষক জটিল ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেন তারা একটা ঐক্যমতে পৌঁছালেন যে এসকল পরীক্ষায় শক্তির প্রাথমিক উৎস হিসেবে যে বজ্রপাত কিংবা অতিবেগুণী বিকিরণ ব্যবহার করা হয়, তা জটিলতর জৈব অণু তৈরি করার ক্ষেত্রে ভীষণ অনিশ্চিত কিংবা ধ্বংসাত্মক। অন্যদিকে রাসায়নিক বাগানে যে তাপীয়-গ্রাডিয়েন্ট দেখা যায় তা জটিলতর জৈব অণু তৈরির উপযোগী বলেই মনে হয়।
জার্মানির হাইডেলবার্গে ইউরোপিয়ান মলিকুলার বায়োলজি ল্যাবরেটরিতে জৈবব্যবস্থায় স্বপ্রতিলিপিকারী সংগঠন নিয়ে গবেষণা করা বিজ্ঞানী এরিক কারসেন্টি তাই বলেন, “আমি এজন্যেই উষ্ণপ্রস্রবণ উদগরণকারী ফাটলের চিন্তাটা পছন্দ করি: আপনি খুব পরিস্কার শক্তি–তারতম্য বিভব ও রাসায়নিক–তারতম্য লাভ করছেন। আর তারতম্য থেকে জটিলতা তৈরি হয়”। আরএনএ-পৃথিবী তৈরির জন্য যদি দরকারী সব কাঁচামাল সঠিক জায়গায় রাখাও হয়, শক্তির তারতম্য ছাড়া প্রাণ হঠাৎ করে আবির্ভূত হতে পারে না। অর্থাৎ, প্রাণের প্রতিলিপি করার জন্য দরকারী জৈব তথ্য ব্যবস্থা হঠাৎ করে উদ্ভূত হতে পারে না। কারসেন্টি বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন যে, “জৈবব্যবস্থা তৈরির জন্য মূল বিষয়টা হলো শক্তি সংরক্ষণ ব্যবস্থা গঠন। তারপর একই শক্তি ব্যবস্থা ব্যবহার করে ডিএনএ– ও আরএনএ–র মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা নির্মাণ। আমি বলবো শক্তির বিষয়টি প্রথমে এসেছে।”
রাসেল এই ভাবনাটাকে আরো পরিচিত কথা দিয়ে ব্যাখ্যা করেন: ‘আমার প্রিয়াস গাড়িটি এর কম্পিউটার ছাড়া চলতে পারলেও ইঞ্জিন ছাড়া কিন্তু চলবে না।‘
৫.
কোন প্রাণের-উদ্ভব সম্পর্কিত যে কোন তত্ত্বের প্রকৃত সত্য শত-কোটি বছরের ইতিহাসের অন্তরালে লুকানো আছে। তবে শক্তি-ধারা নিয়ে রাসেলের ভাবনা সময়ের এই বাঁধাকে অস্পষ্ট, কিন্তু কাব্যিক কোন অস্ফুট কিছুতে বদলে দেয়। তিনি বলেন, ‘আমি উৎপত্তি (origin) শব্দটা পছন্দ করি না। আমরা একে বলতে চাই ‘আবির্ভাব‘ (emergence)।’ আপনি যদি শক্তি দিয়ে প্রাণের আবির্ভাবের কথা ভাবেন, তাহলে প্রাণের উদ্ভবকে আসলে শক্তিধারার বিশ্বজনীন উৎস বিগব্যাঙের সাথে সম্পর্কিত করা যায়। বিগব্যাঙের মুহূর্তে মহাবিশ্ব এক ‘প্রায় অসীম তাপগতীয় চাপ’-এর মধ্যে ছিলো বলে ২০১৩ সালের এক গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেন রাসেল। স্ববিরোধী মনে হলেও এটা সত্যি যে এরকম চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য – শৃঙ্খলা থেকে বিশৃঙ্খলার দিকে ধাবমান হওয়ার জন্য – সবচেয়ে কর্মদক্ষ পথ হল অস্থায়ী কিন্তু শৃঙ্খলিত ব্যবস্থার নির্মান। একে তুলনা করা যায় বাথটাবের হঠাৎ পানি যাওয়ার প্লাগ খুলে দিলে উৎপন্ন হওয়া ঘূর্ণিস্রোত কিংবা ঝড়ের সময় টর্নেডো তৈরি হওযার সাথে। ঐ গবেষণা প্রবন্ধে রাসেল ও তার সহলেখকরা উল্লেখ করেন মহাবিশ্বের সকল শৃঙ্খলা সম্ভবত এই স্ববিরোধী বৈপিরত্য থেকেই জন্মলাভ করেছে।
জীবন এরকম শৃঙ্খলার একটি মরুদ্যান। তাত্ত্বিকভাবে, বিগব্যাঙের পর মহাবিশ্ব সকল দিকে সমভাবে শক্তি ও বস্তু ছড়িয়ে দিয়ে সম্প্রসারিত হতে পারতো। যদি তাই হতো, তাহলে কোন কিছুই ঘটনো না। প্রাণ সহ কোন কিছুই তৈরি হতো না। তবে এটা না হয়ে অন্য ঘটনা ঘটেছে। কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন সম্ভবত স্থানের গঠনের মধ্যে শক্তি ও বস্তুর ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়ে বিশ্বসৃষ্টির গঠন ও সংগঠনকে একটি গতিপথ দিয়েছে। বিভিন্ন কণা যুক্ত হয়; মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্যে অন্যান্য কণাদের আকৃষ্ট করে; দ্রুত বিভিন্ন অঞ্চল তৈরি হয়েছে যেখানে মহাকর্ষ বল দিয়ে বস্তু নিচয় যুক্ত থাকে, আর থাকে বৃহৎ প্রসারিত শূন্যতা।
কিছু কিছু বস্তু জড়ো হয়ে নক্ষত্র তৈরি করে। সেসব নক্ষত্রের চারপাশে গ্যাস ও ধূলিকণার চাকতি থেকে তৈরি হয় গ্রহ যাদের উত্তপ্ত কেন্দ্র গলিত; যেখানে চলতে থাকে বিরামহীন টেকটনিক নড়াচড়া আর আগ্নেয়গিরির উদ্গিড়ন। এ অস্থিরতা থেকে তাপীয়-তরল পরিচলন প্রক্রিয়ার শুরু হয়, যা উস্কে দেয় সার্পেন্টিনাইজেশন (serpentinisation) প্রক্রিয়া; যার ফলে সমুদ্রতলে উষ্ণপ্রস্রবণ নিঃসরণকারী ফাটল তৈরি হয় – ফলাফল রাসেলের রাসায়নিক বাগান। অন্ততঃ একটি গ্রহে এসব খনিজ-মিনার গ্রহ-ভূতত্ত্বের ভারসাম্যহীনতাকে ভিন্ন রসায়নের পথে পরিচালিত করে, তৈরি হয় জটিল প্রাক-বিপাকীয় ব্যবস্থা যা অবশেষে প্রাণের উদ্ভব ঘটায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে প্রাণের উদ্ভব আসলে কোন ‘উৎপত্তি‘ নয়, বরং বিগব্যাঙের কারণে একের পর এক ঘটতে থাকা অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি ধাপ মাত্র।
প্রাণকে শক্তির ভাষায় চিন্তা করতে গেলে তা প্রাণের সংজ্ঞাকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। রাসেল বলেন, “প্রাণ কি এটা কোন কথা নয়। কথা হলো প্রাণ কি করে।” যত যাই হোক, আপনি আপনার দেহের সকল পরমাণু কয়েক বছরের মধ্যেই স্থানান্তরিত করে ফেলেন। এভাবে ভাবলে প্রাণ আসলে কোন বস্তু নয়, বরং অস্তিত্বশীলতার একটি প্রক্রিয়া, সৃষ্টি ও ধ্বংসের এক বিরামহীন ভারসাম্য। যদি প্রাণকে সংজ্ঞায়িত করতেই হয়, তহলে এরকম বলা যায়: প্রাণ হলো নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য সুসংগঠিত প্রবাহধারা, কিছু নির্দিষ্ট শর্তের মধ্যে বস্তু- ও শক্তির নিজেকে প্রকাশ করার একটি প্রাকৃতিক উপায়।
রাসেলের ভাবনা অনুযায়ী অন্যান্য জীবনের পাশাপাশি আমাদের মানব প্রজাতিকে শক্তির এক রকম ছাঁদ বা প্যাটার্ন – মহাবিশ্বের বাউণ্ডুলে শৈশবের উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে যার আবির্ভাব – এভাবে দেখলে আমাদের অহংবোধে একটু আঘাত লাগে। তবে এটা হয়তো আমাদেরকে উপলদ্ধি করতে শেখায় যে আমরা বিশাল মহাবিশ্বে নিঃসঙ্গ নই। আমরা সময়ের সুপ্রভাত থেকে প্রবাহিত শক্তিধারার বংশধর। পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যার মধ্যে এরকম গভীর একটি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতে পারে তা ডারউইন আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, তিনি ভেবেছিলেন যে, “এমন হয়তো সম্ভব যে প্রাণের মূলনীতিকে পরবর্তীতে কোন সাধারণ নিয়মের অংশ, বা পরিণাম হিসেবে দেখানো যাবে।” তিনি হয়তো এও যোগ করতেন যে প্রাণ বিষয়ক এই দৃষ্টিভঙ্গিতে একধরণে জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বর রয়েছে।
টিম রেকার্থ একজন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক। তাঁর লেখা সায়েন্টিফক আমেরিকান, নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন, ফরেন পলিসি সহ অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিউ ইয়র্ক শহরে বসবাস করেন। মূল লেখা Our Chemical Eden, অনলাইন পত্রিকাAeon-এ প্রকাশিত। অনুবাদটি আমার বই প্রাণের বিজ্ঞান: সাম্প্রতিক জীববিজ্ঞানের ভাবনা ভাষান্তর (২০১৭) থেকে নেয়া।
টীকা
[১] গুহার মেঝেতে তৈরি হওয়া এক ধরনের পাথর, যা গুহার ছাদ থেকে ঝরে পড়া তরল থেকে তৈরি হয়[২] লতানো তন্ত্রী বা আঁকড়
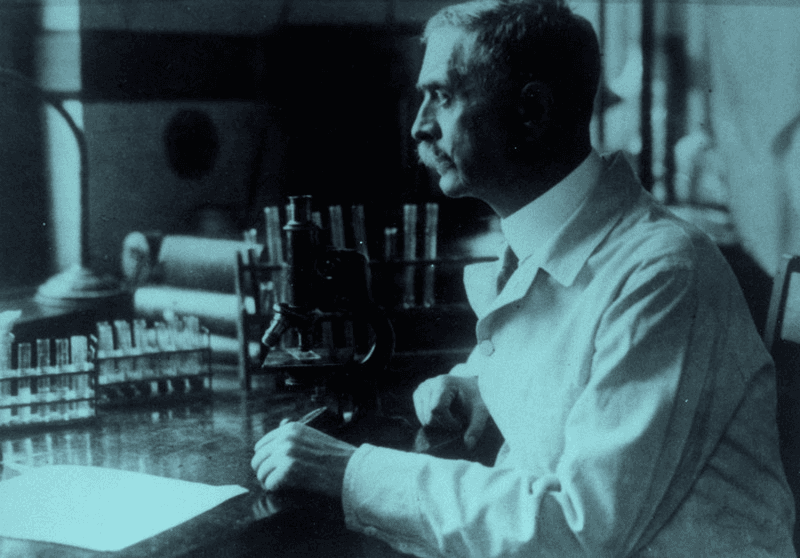


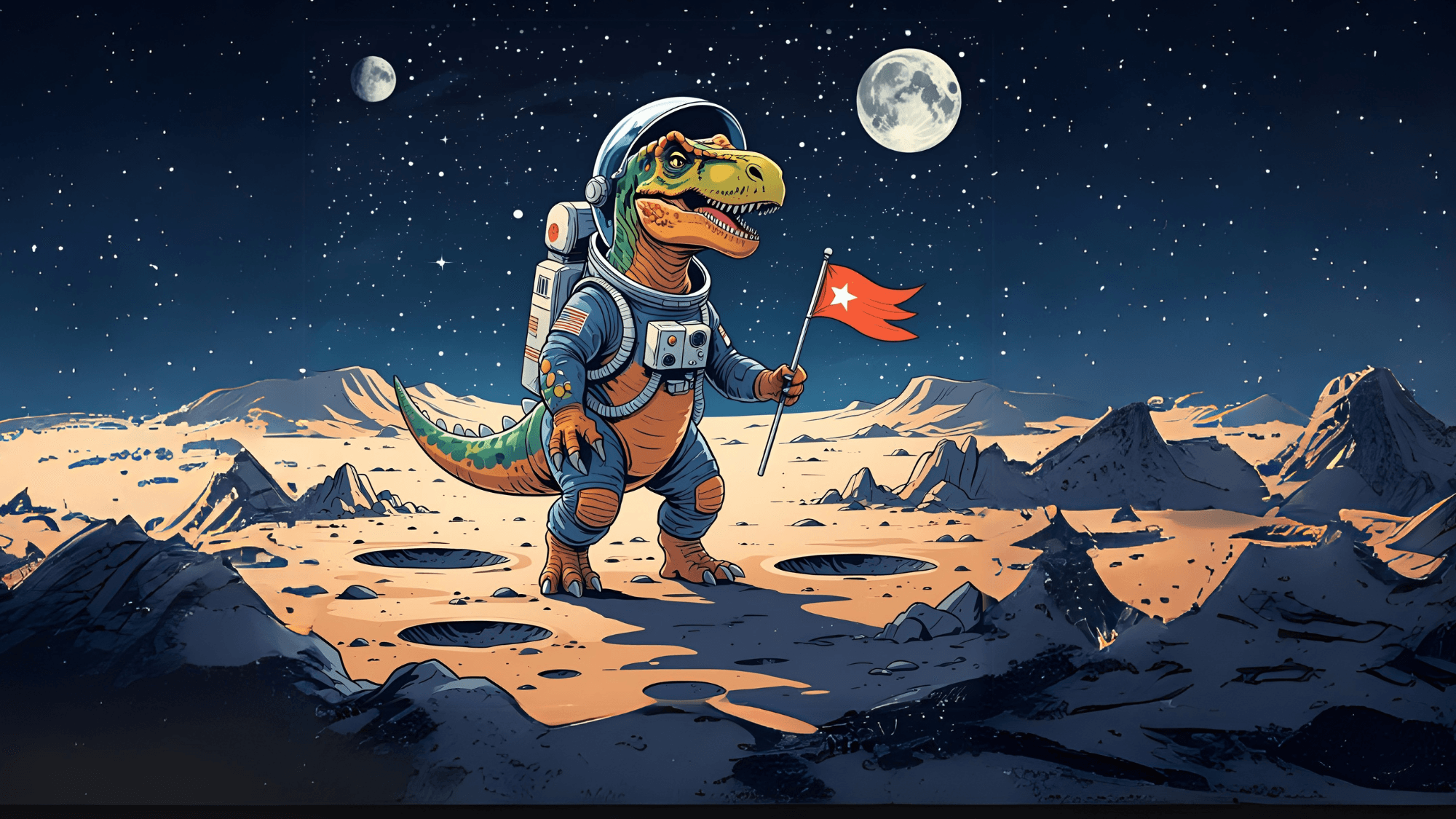
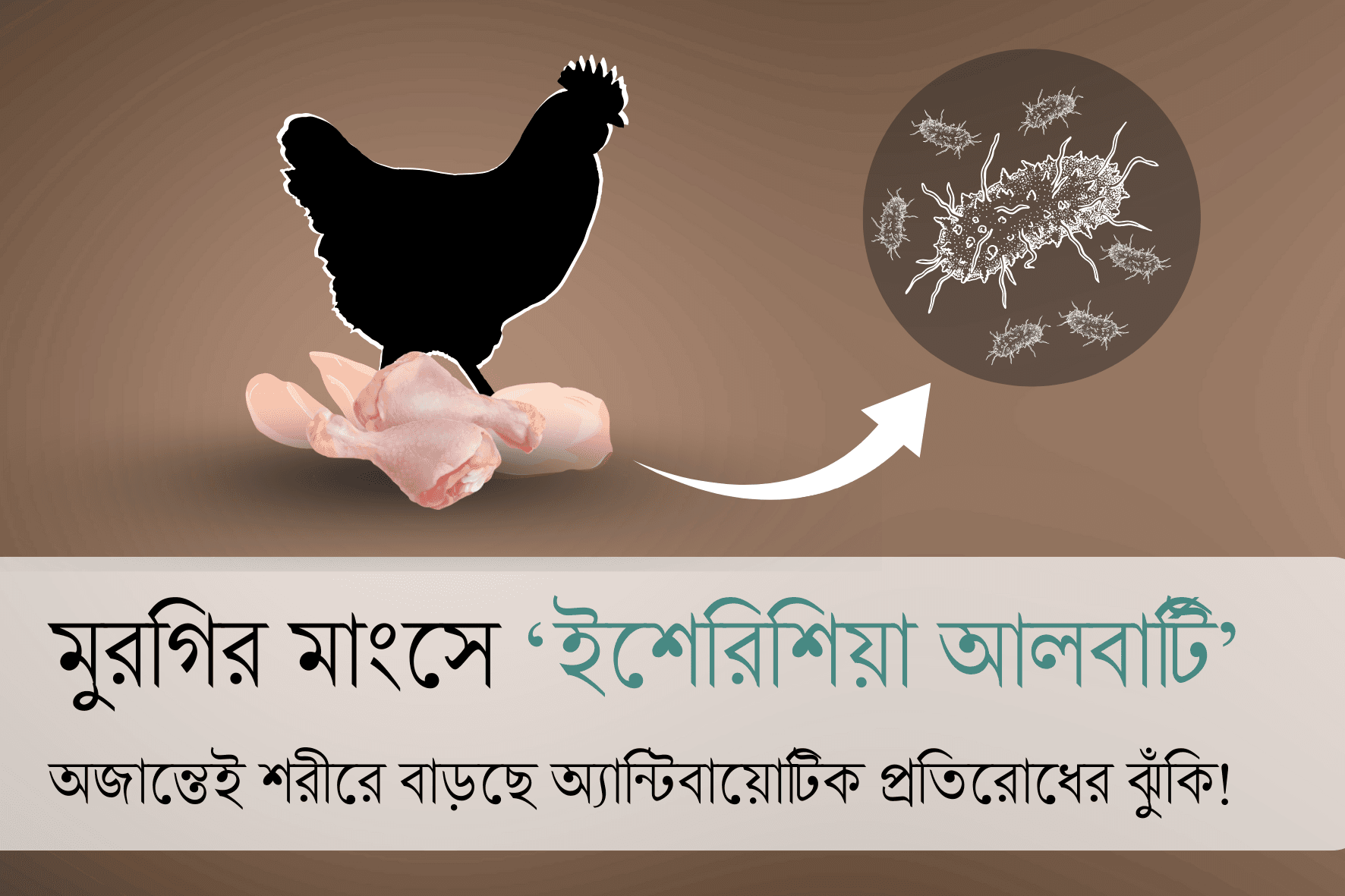


Leave a Reply