১৮৫৯ সালে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে বসে জনৈক ডাক্তার, চার্লস হ্যারিসন ব্ল্যাকলি একটা হাঁচি দিয়েছিলেন। সেই সাথে তিনি স্বর্দি, চোখ খচখচ, কাশিতেও কষ্ট পাচ্ছিলেন। সবগুলোই হে ফিভারের(Hay Fever) এর চিরাচরিত উপসর্গ। হে ফিভার সম্পর্কে অনেক দিন ধরেই মানুষ জানত। কেন বা কি কারণে হয় সে সম্পর্কে অনেকের অনেক রকম ধারণা ছিল। জনপ্রিয় গুলোর মধ্যে প্রথমেই ছিল গরম, তার পরেই ছিল ওজোন। তবে ব্ল্যাকলি প্রকৃত কারণ উদঘাটনে ছিলেন বদ্ধ পরিকর।
ঐতিহাসিক কারণেই এলার্জি সম্পর্কে কথা বলতে গেলে হে ফিভারের কথা চলে আসে। বৈজ্ঞানিক লিটারেচারে প্রথম হে ফিভারের বর্ণনা পাওয়া যায় জন বোস্টকের ১৮১৯ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। যেখানে তিনি JB নামক এক রোগীর জীবনের বিভিন্ন সময়ে catarrhus aestivus এ আক্রান্ত হওয়া এবং বিভিন্ন রকমের প্রচলিত প্রতিকার ব্যবহার করেও পুরোপুরি না সারার কথা বর্ণনা করেন। গ্রীক ভাষায় Catarrhus মানে নির্গমন, চোখ ও নাক দিয়ে পানি পড়া বুঝাতে এখানে ব্যাবহৃত হয়েছে, আরে aestivus মানে গ্রীষ্ম। যদিও তিনি কি কারণে এটা হয় সেটার কোন উপসংহার টানেননি তবে একসময় সাধারণ মানুষের মাঝে জনপ্রিয় হল খড় পঁচে গেলে যে বাষ্প বের হয় তার কারণে এটা হয়। এই ধারণা ধোপে না টিকলে নামখানা রয়ে গেলো। এর কারণ catarrhus aestivus এর মত বদখত নামের চেয়ে হে ফিভার উচ্চারণ আর মনে রাখা ঢের সহজ বলে কি না তা জানা নাই।
তো যাই হোক, জন বোস্টকের রোগী JB যে তিনি নিজেই এটা হয়তো বুঝে আপনি বুঝে ফেলেছেন। ফিরে আসি ব্ল্যাকলির প্রসঙ্গে। উনি CB নাম দিয়ে কোন রোগীকে বর্ণনা না করলে নিজের উপর নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট করে সিদ্ধান্তে আসলেন যে ফুলের রেণু নাকে প্রবেশ করলে হে ফিভার দেখা দেয়। এ তো গেল কারণ, তবে কি কৌশলে ফুলের রেণুর মত নিরীহ বস্তু এই অস্বস্তিকর রোগটা ঘটায় তা পরিষ্কার হয় আর পরে।
১৯০৬ সালে ক্লেমেন্স ফন পিরকে, একজন অস্ট্রিয়ান চিকিৎসক সর্বপ্রথম অ্যালার্জি শব্দটা ব্যবহার করেন। সেই সময়ে স্মলপক্স প্রতিরোধে টিকা হিসেবে ঘোড়ার সিরাম প্রচলিত ছিল। তার নজরে আসলে, এই টিকার দ্বিতীয় ডোজ গ্রহণ করলেই অনেক রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। তিনি সঠিকভাবে ব্যখ্যা করতে পেরেছিলেন যে এই “সিরাম সিকনেস” এর মূলে রয়েছে আমাদের ইমিউন সিস্টেম। যা সিরামে উপস্থিত কোন এন্টিজেনের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তা দেখাচ্ছে। তবে একদম সুস্পষ্ট বর্ণনা পেতে আর সময় লেগেছিল।
যেসব এন্টিজেনের কারণে অ্যালার্জি হয় তাদেরকে বলে এলার্জেন, আর এই জগতে যেকোন জৈব অথবা রাসায়নিক পদার্থই এলার্জেন হতে পারে। তবে আমাদের ভাগ্য ভালো যে একজন মানুষের দেহে সব এলার্জেন এলার্জি ঘটায়না। তবে কিছু কিছু এলার্জেন যেমন ফুলের রেণু, বিশেষ কোন ওষুধ, কোন নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের মেকআপ অথবা কোন খাবার অনেক মানুষের এলার্জির কারণ হতে পারে। এলার্জেনের সংখ্যা যেমন গণনাতীত, তেমনই এলার্জির বহিঃপ্রকাশও বহু উপায়ে হতে পারে যেমন স্বর্দি, কাশি, চোখ খচখচ করা, শ্বাসকষ্ট, ফোড়া, গোটা, পেট খারাপ ইত্যাদি। আশ্চর্যের ব্যপার এটাই যে এলার্জির অনুঘটক আর উপসর্গে এত বৈচিত্র্য থাকা স্বত্বেও ভেতরে কিন্তু সবকিছু একই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত।
এই প্রক্রিয়ার বিস্তারিত জানা যায় কার্ল প্রাসুনিতয এবং হাইনয কুসনার নামক দুই চিকিৎসকের এক্সপেরিমেন্ট থেকে, যার কিছুটা তাঁরা আবার নিজেদের উপর চালিয়েছিলেন। কুসনার রান্না করা মাছের একটা প্রোটিনের প্রতি এলার্জিক ছিলেন, কার্ল ছিলেন না। কুসইনার দেখলেন যে যদি তিনি রান্না করা মাছের দেহ থেকে ঐ প্রোটিন সংগ্রহ করে সামান্য মাত্রায় নিজের বাহুতে ইনজেক্ট করেন, সে জায়গাটা ধীরে ধীরে ফুলে উঠে, চুলকাতে শুরু করে, একটা সময় চুলকানি অন্যান্য অঙ্গেও ছড়িয়ে যায়। কাশি আসে এবং শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। তবে প্রায় ২০ মিনিট পরে উপসর্গগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।
অন্যদিকে কার্লের ওই প্রোটিন নিয়ে কোন সমস্যা ছিলোনা। যেই মাত্রাতেই, যত বাড়ই ইনজেক্ট করা হোক না কেন, তার দেহে কোন প্রতিক্রিয়াই হচ্ছিলোনা। তবে তার শরীরে যদি কুসনারের সিরাম ইনজেক্ট করা হয়, এবং তার কিছু সময় পর সেই প্রোটিন ইনজেক্ত করা হয়, তখন ঠিকি আবার একি উপসর্গগুলো কার্লের দেহে দেখা দিচ্ছিল।
যেসব এন্টিজেনের কারণে এলার্জি হয় তাদেরকে বলে এলার্জেন, আর এই জগতে যেকোন জৈব অথবা রাসায়নিক পদার্থই এলার্জেন হতে পারে। তবে আমাদের ভাগ্য ভালো যে একজন মানুষের দেহে সব এলার্জেন এলার্জি ঘটায়না। তবে কিছু কিছু এলার্জেন যেমন ফুলের রেণু, বিশেষ কোন ওষুধ, কোন নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের মেকআপ অথবা কোন খাবার অনেক মানুষের এলার্জির কারণ হতে পারে। এলার্জেনের সংখ্যা যেমন গণনাতীত, তেমনই এলার্জির বহিঃপ্রকাশও বহু উপায়ে হতে পারে যেমন স্বর্দি, কাশি, চোখ খচখচ করা, শ্বাসকষ্ট, ফোড়া, গোটা, পেট খারাপ ইত্যাদি। আশ্চর্যের ব্যপার এটাই যে অ্যালার্জির অনুঘটক আর উপসর্গে এত বৈচিত্র্য থাকা স্বত্বেও ভেতরে কিন্তু সবকিছু একই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত।
এই প্রক্রিয়ার বিস্তারিত জানা যায় কার্ল প্রাসুনিতয এবং হাইনয কুসনার নামক দুই চিকিৎসকের এক্সপেরিমেন্ট থেকে, যার কিছুটা তাঁরা আবার নিজেদের উপর চালিয়েছিলেন। কুসনার রান্না করা মাছের একটা প্রোটিনের প্রতি এলার্জিক ছিলেন, কার্ল ছিলেন না। কুসইনার দেখলেন যে যদি তিনি রান্না করা মাছের দেহ থেকে ঐ প্রোটিন সংগ্রহ করে সামান্য মাত্রায় নিজের বাহুতে ইনজেক্ট করেন, সে জায়গাটা ধীরে ধীরে ফুলে উঠে, চুলকাতে শুরু করে, একটা সময় চুলকানি অন্যান্য অঙ্গেও ছড়িয়ে যায়। কাশি আসে এবং শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। তবে প্রায় ২০ মিনিট পরে উপসর্গগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।
অন্যদিকে কার্লের ওই প্রোটিন নিয়ে কোন সমস্যা ছিলোনা। যেই মাত্রাতেই, যত বার-ই প্রয়োগ করা হোক না কেন, তার দেহে কোন প্রতিক্রিয়াই হচ্ছিলোনা। তবে তার শরীরে যদি কুসনারের সিরাম ইনজেক্ট করা হয়, এবং তার কিছু সময় পর সেই প্রোটিন ইনজেক্ত করা হয়, তখন ঠিকি আবার একি উপসর্গগুলো কার্লের দেহে দেখা দিচ্ছিল।
এই এক্সপেরিম্নটের মাধ্যমে বুঝা গিয়েছিলো যে বস্তুর কারণে অতিসক্রিতা তথা এলার্জি দেখা যায় সেগুলো মানুষের রক্তে থাকে। পরবর্তীতে জানা গেল ইমিনোগ্লোবিউলিন ই(IgE) এন্টিবডিই এই অতিসক্রিয়তার জন্য দায়ী। IgE মানুষের দেহে তৈরি হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন পাঁচটি এন্টিবডির মধ্যে অন্যতম। যেসব বি কোষ IgE তৈরি করে তাদেরকে সাধারণত চামড়ার নিচে, ফুসফুসে, অন্ত্রের প্রাচীরে পাওয়া যায়। কারো দেহে কোন কারণে কিছু কিছু এলার্জেনের সংস্পর্ষে আসার প্রতিক্রিয়ায় IgE তৈরি হয়। প্রথম বার কারো দেহে IgE তৈরি হলে তেমন কিছু হয়না। যেমন, প্রথম বার বোলতার কামড়ে হুল ফোটানোর ব্যাথা ছাড়া আর কিছু হয়না। তবে, পরবর্তিতে যদি আবার সেই ব্যাক্তিকে বোলতা কামড়ায় তাহলে মৃদু থেকে জোরালো অতি সক্রিয়তা দেখা দিতে পারে। কেন কিছু এন্টিজেনের বিরুদ্ধে এন্টিবডি কিছু মানুষের দেহে তৈরি হয়, সেই কারণটি ঠিক স্পষ্ট নয় এখনো।
প্রথমবার এলার্জেনের সংস্পর্ষে আসলে IgE তৈরি হওয়া শুরু হয়। যখন এই এন্টিবডির সংখ্যা মাত্রা অনেক বেড়ে যায়, তখনেরা মাস্ট কোষ এবং বেসোফিলের সাথে যুক্ত হয়। মাস্ট কোষ আর বেসোফিলের গ্র্যানিউলের ভেতর থাকে বিভিন্ন জৈবরাসায়নিক বিকারক, সবচেয়ে বেশি থাকে হিস্টামিন। দ্বিতীয়বার যখন এলার্জেন দেহে প্রবেশ করে এবং IgE এর সংস্পর্ষে আসে তখন মাস্ট কোষ এবং বেসোফিলে তাদের গ্র্যানিউলের ভেতরের সব রাসায়নিক এবং হিস্টামিন রক্তে ছেড়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে ডি-গ্র্যানিউলেশন, এর মাধ্যমেই এলার্জি সংক্রান্ত অপ্রীতিকর সব উপসর্গ প্রকাশ শুরু করে।
একই এলার্জেন কারো দেহে ভয়ানক আবার কারো দেহে কেন নিরীহ এই বিষয়টা পরিষ্কার জানা না গেলেও রক্তে হিস্টামিন এবঙ অন্যন্য রাসায়নিক নিঃস্বরনের পর তারা যেসব ঘটনা ঘটায় তা আমরা ভালোই জানি। হিস্টামিন যখন রক্তনালিকার সাথে যুক্ত হয় তখন সেগুলো প্রসারিত হয় এবং সেই সাথে এর প্রাচীর ভেদ করে রক্তের তরল পদার্থসমূহ বের হয়ে আসতে থাকে। এর ফলে দেহের পৃষ্ঠে এলার্জির জায়গায় র্যাশ দেখা দেয়। যদি নালিকার ভেদযোগ্যতা ছড়িয়ে যায় সারা দেহে, তখন রক্ত চাপ হ্রাস পায় এবং আক্রান্ত ব্যাক্তি লিথাল শক এ চলে যেতে পারেন।
শরীরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মাস্ট কোষ পাওয়া যায় ফুসফুসে। এরা যখন হিস্টামিন নিঃসৃত করে তখন সে ব্রংকিওলের চারপাশের পেশীতে যুক্তু হয়ে এর সংকোচন ঘটায়। যার ফলে শ্বাস প্রশ্বাস বাধাগ্রস্থ হয়। হিস্টামিনের কারণে অন্যদিকে বায়ুপথে(Airway) মিউকাস নিঃস্বরন বেড়ে যায়, সেটাও বায়ুপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটায়। আর এই প্রতিটা ঘটিনাই বিভন্ন তাল লয়ে ঘটে একেক উপসর্গ একেক মাত্রায় ঘটিয়ে আমাদের অসুস্থ করে ফেলে।

এবারে বেশ কিছু সাধারণ এলার্জি সম্পর্কে আমরা জানবো।
হে ফিভার
নামের মধ্যে জ্বর থাকলেও এটা কিন্তু জ্বর নয়, এবং খড়ের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই তা আগেই জেনেছি। বরং ফুলের রেণু, বাতাসের ধূলা, প্রাণীর লোম, পোকা মাকড়ের দেহাংশ এসবের কারণে হে ফিভার হয়ে থাকে। ডাক্তারি ভাষায় এর নাম এলার্জিক রাইনাইটিস এবং আমাদের নাকটাই এতে সবচেয়ে বেশি ভুগে। আমাদের নাক অনেক ক্ষুদ্র রক্ত নালী আর নিঃসরক গ্রন্থিতে পূর্ন। আর এদের কাজ শ্বাসের মাধ্যমে নেয়া বাতাসকে উষ্ণ ও আর্দ্র করা। আর্দ্র করার জন্য সুস্থ নাক থেকে দিনে প্রায় ১ পোয়া পরিমাণ পানি নিঃসৃত হয়ে থাকে। নাকের লোম এলার্জেনের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক ফিল্টার হিসেবে কাজ করে।
নাকের ভেতরের অংশেও থাকে IgE নিঃসরণ কারি বি কোষ এবং তার সাথে থাকে মাস্ট কোষ ও বেসোফিল। তাই নাকে প্রবেশ কারী এলার্জেনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া একি সাথে ক্ষিপ্র ও ক্ষিপ্ত। হিস্টামিনের প্রভাবে রক্তনালিকা প্রসারিত হয়ে রক্তের তরল বের হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের টিস্যুতে। এই তরল পরে বের হয় নাকের গ্রন্থি এবং ঝিলি দিয়ে নিঃসৃত হয়। এর ফলে দেখা দেয় স্বর্দি। শুধু তাই না, অস্বস্তিকর অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে তালু এবং চোখেও।
এনাফাইল্যাক্সিস
হে ফিভারের সাথে যে সব উপসর্গ দেখা যায় সেগুলো অস্বস্তিকর হলে প্রাণঘাতী নয়। তবে এমন কিছু বস্তু আছে যেগুলোর প্রতিক্রিয়া মারাত্নক। পেনিসিলিন এবং তার সমগোত্রীয় ওষুধ, মৌমাছি, পিপড়া এসবের বিষ সাধারণ এলার্জির সাথে সাথে ঘটাতে পারে এনাফাইল্যাক্সিস।
অন্যান্য এলার্জির মত এর মূলেও রয়েছে IgE এবং মাস্ট কোষ। এই প্রতিক্রিয়া এত দ্রুত যে সাথে সাথে চিকিৎসা না দিলে মারাত্নক হতে পারে। দেহে এলার্জেন প্রবেশের মিনিটের মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং বিভিন্ন উপসর্গ যেমন নিস্তেজ লাগা, শ্বাসকষ্ট, বমি বমি ভাব ও চুলকানি দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত ব্যাক্তি জ্ঞানও হারাতে পারেন। কখনো কখনো শ্বাসকষ্ট অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং রক্ত চাপ কমে যেতে থাকে। এমন হলে দ্রুত চিকিৎসা দেয়া উচিত। অন্যান্য এলার্জির মত এনাফাইল্যাক্সিস প্রথমবার এলার্জেনের সংস্পর্শে আসলেই ঘটেনা। প্রথমবার শুধুমাত্র এই এলার্জেনের স্পেসিফিক IgE তৈরি হয়ে মাস্ট কোষ এবং বেসোফিলের গায়ে অবস্থান করতে থাকে। পরবর্তী এক্সপোজার, বিশেষত যদি এলার্জেন রক্তে প্রবেশ করে অতক্ষণই IgE যুক্ত মাস্ট কোষের মাধ্যমে এনাফাইল্যাক্সিস শুরু হয়।
হাঁপানি
যেই এলার্জেনের কারণে হে ফিভার হয়, সেই একি এলার্জেন অ্যাজমার জন্য দায়ী যদি সে নাক এবং গলা পার হয়ে ফুসফুসে পৌঁছাতে পারে।
হাঁপানি এমনি একটি জটিল সমস্যা যার মূলে তাৎক্ষনিক অতিসক্রিয়তা ছাড়াও আরো কারণ থাকতে পারে। যখন নিঃশ্বাসের সাথে নেয়া এলার্জেন IgE এবং মাস্ট কোষের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফলে হাঁপানি হয় তখন একে বলে Extrinsic অ্যাজমা। আবার একই উপসর্গ অন্যান্য কারণেও দেখা দিতে পারে। কিছু কিছু মানুষে মানসিক চাপ ও দৈহিক পরিশ্রমের কারণেও হাঁপানি হতে পারে । অত্যন্ত আবেগীয় কিংবা ট্রমাটিক পরিস্থিতিতে এমন কিছু নিউরোট্রান্সমিটার নিঃসৃত হয় যেগুলা বিভিন্ন ধরনের এলার্জি ঘটাতে পারে কিংবা মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে যার মধ্যে হাঁপানি অন্যতম। অনেকের ক্ষেত্রে আবার শারীরিক পরিশ্রমের কারনেও হাঁপানি দেখা দেয়। চিকিৎসকরা এই ধরণের হাঁপানিকে বলেন Intrinsic অ্যাজমা। অনেক ক্ষেত্রেই হাঁপানির এই দুইয়ের মিশেলে হয়, যেটার সমাধানের জন্য চিকিৎসককে অত্যন্ত দক্ষ হতে হয়।
একটা পর্যায় পর্যন্ত এক্সট্রিনসিক হাঁপানি ঘটে হিস্টামিন এবং অন্যান্য প্রভাবকের নিঃস্বরনের মাধ্যমে। হাঁপানির শুরুটা IgE এবং মাস্ট কোষের উপর নির্ভরশীল। তবে ইমিউন সিস্টেমের অন্যান্য খেলুড়েও এর সাথে জড়িত হয়ে রোগটিকে জটিল করে তোলে। IgE এর মাধ্যমে যে অ্যাজমাটিক এটাক শুরু হয় তার কিছুক্ষণ পরেই শ্বেতকণিকা ফুসফুসে আক্রমণ করে, যার ফলে ফুসফুসে মিউকাসের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং এই মিউকাস হিস্টামিনের কারণে নিঃসৃত ফ্লুয়িডের সাথে মিশে ব্রংকিওলে জমা হয়।
অন্যদিকে হিস্টামিন এবং আরেক সাইটোকাইন লিউকোট্রাইনের প্রভাবে ব্রংকিওল সংকুচিত হয়ে ফুসফুসে বাতাসের আসা যাওয়ার পথ সংকীর্ন হয়ে পড়ে। আবার ফুসফুসের ভেতরে যেখানে গ্রহণ করা বাতাস থেকে ফুসফুস অক্সিজেন টেনে নেয় সেখানেও হিস্টামিনের প্রভাবে ফ্লুয়িড জমে। ফুসফুসে বাতাস ঢুকলেও রক্তে যথেষ্ট অক্সিজেন সর্বরাহ না ঘটলে মগজ বলে আরও পাম্প করো, আরও পাম্প করো। এই সবকিছু মিলিয়েই সৃষ্টি হয় মারাত্নক শ্বাসকষ্ট। ফুসফুস পাম্প করেই যাচ্ছে, অন্যদিকে বিভিন্ন স্থানে মিউকাস জমে বাতাসের আসা যাওয়া বাঁধা গ্রস্ত হচ্ছে আবার অক্সিজেন গ্রহণও প্রয়োজন মত হচ্ছেনা। এই ভোগান্তির যে শিকার হয় সেই প্রকৃত কষ্টটা বুঝে।
খাদ্যে এলার্জি
বেঁচে থাকার জন্য আমাদের খেতে হবেই। গড়ে একজন মানুষ সারাজীবনে ২৫ থেকে ৩০ টন খাবার খায়। মানুষ হিসেবে আমরা যত প্রকরণের খাবার খাই তার কোন ইয়ত্তা নাই। এই অজস্র খাবারের মধ্যে কোন কোনটা এলার্জিক হতেই পারে। তবে অন্যান্য সকল এলার্জির মধ্যে খাবারের এলার্জিটাই সবচেয়ে ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিতে পারে। প্রতি বছর বহু মানুষ এই কারণে মারা যায়। আশার কথা এই যে, বেশিরভাগ খাবার সংক্রান্ত এলার্জিই মাথা ঘ্রোরানো, বমি, পেট বেথা, চুলকানি, হাঁপানিতেই সীমাবদ্ধ। এবং একবার যদি বুঝা যায় কোন খাবারের কারণে কারো এলার্জি হচ্ছে তাহলে সেটা এড়িয়ে চললেই এটা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।
বেশিরভাগ খাবারের এলার্জিই প্রোটিনের সাথে জড়িত। সব খাবারের মত প্রোটিনেরও যথার্থ হজম শুরু হয় পাকস্থলীতে। যখন আংশিক হজম হওয়া প্রোটিন পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে , তখন অগ্নাশয় থেকে শক্তিশালী এনজাইম এসে হজম প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই প্রক্রিয়া এখানেই শেষ হয়, প্রোটিন ভেঙ্গে এমিনো এসিডে পরিণত হয়ে রক্তে মিশে যায় যা পরে অন্য প্রোটিনের সিনথেসিসে কাজে লাগে।
তবে কখনো কখনো স্বল্প পরিমাণে আংশিক হজম হওয়া প্রোটিন রক্তে চলে আসে। যাদের আলসার জাতীয় সমস্যা আছে, তাদের ক্ষেত্রে একদম ইনট্যাক্ট প্রোটিনও এমনকি অন্ত্র থেকে বের হয়ে যেতে পারে। যখন প্রোটিনের টুকরাগুলো এন্টিজেনিক হবার মত যথেষ্ট বড় তখন আর এটাকে বহিরাগত প্রোটিনের সাথে পার্থক্য করার মত কিছু থাকেনা, অতঃপর … ইমিউন সিস্টেমের প্রতিক্রিয়া।
শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষত জন্মের প্রথম ২/৩ বছরে খাবারে এলার্জি থাকাটা বেশ স্বাভাবিক। কারণ এই সময়টাতে শিশুদের পরিপাকতন্ত্র বিকশিত হতে থাকে। প্রোটিন হজমের জন্য পাকস্থলীর এসিড এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় এনজাইম থাকে কম পরিমাণে। যেসব ঝিল্লি প্রোটিনকে পাকস্থলী থেকে বের হয়ে যাওয়াকে আটকায় সেগুলো থাকে অপরিপক্ক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের এলার্জি বয়স বাড়ার সাথে সাথে চলে যায়।
সব রকম খাবারের মধ্যে এলার্জিক হিসেবে সবচেয়ে বেশি বদনাম আছে দুধ, ডিমের সাদা অংশ, মাছ এবং সয় বিনের। বিভিন্ন রকমের বাদামও ভয়ানক এলার্জি সৃষ্টি করতে পারে। বাদামের যেই প্রোটিনের কারণে এলার্জি হয় তা বাদামের তেল এ অতি অল্প মাত্রায় থেকে কারো কারো দেহে শক্তিশালী এলার্জির কারণ হতে পারে। একটা জনপ্রিয় গল্প আছে যেখানে এক লোক টুনা স্যান্ডুইচ খাওয়ার পর এনাফাইল্যাক্সিসে আক্রান্ত হন। তবে সেই স্যান্ডুইচের কোন কিছুতেই তার অ্যালার্জির হিস্ট্রি নেই। পরে জানা গিয়েছিলো যেই স্যান্ডুইচটি বানাতে যেই ছুরি ব্যবহৃত হয়েছিল সেটা কিছুক্ষণ আগেই একটা পিনাট বাটারের ক্যান খুলতে লেগেছিল।
খাবারের বিভিন্ন স্বাদবর্ধক এবং প্রিজারভেটিভও এলার্জির কারণ হতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে। অন্যান্য এলার্জির মত খাবারের এলার্জিও দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় এক্সপোজারের সময় এফেক্টিভ হয়। এই সিম্পটমগুলো শরীরের যেকোন স্থানেই দেখা দিতে পারে। আর প্রক্রিয়াও অন্যান্য এলার্জির মতই একি। IgE, হিস্টামিন, মাস্ট কোষের খেলা।
এখন প্রশ্ন আসতে পারে, কেন এই অতিসক্রিয়তা? এতে কি উপকারটা হয় আমাদের? ইমিউন সিস্টেমের যেই অংশ নীরবে নিভৃতে জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে, তার সাথে এই প্রতিক্রিয়াশীল সম্পর্কটাই বা কি? এর উত্তর আসলে আমাদের জানা নাই।
অ্যালার্জির যে ক্লাসিক প্রকৃয়া যাতে প্রধান ভূমিকা IgE এর, সেটার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন করতে পারেন, কেননা IgE ই বা কেন রয়েছে আমাদের দেহে সেটাও স্পষ্ট না। যেখানে শরীরে আর ৪ পদের ইমিউনোগ্লোবিউলিন আছে, সেখানে আবার আরেকটা ইমিউনোগ্লোবিউলিন কেন দরকার হল। হ্যাঁ প্রমাণ আছে কিছু কিছু পরজীবীর সংক্রমণ ঠেকাতে IgE এর অবদান আছে, তবে সেসব ক্ষেত্রে অন্যান্য ইমিউনোগ্রোবিউলিন সহ ইমিউন সিস্টেমের অন্যান্য অংশও সক্রিয় ভাবে কাজ করে। বিরল হলে অনেকের দেহেই IgE থাকেনা, তাদের ইমিউন সিস্টেমে তো তো পরজীবী কিংবা অন্য কোন সংক্রমণে কাবু হয়না। আর কিছু গবেষণায় ফুটে উঠেছে যে, আমাদের দেহেই এমন কিছু জটিল যন্ত্রপাতি রয়েছে যারা IgE এর উৎপাদনকে সীমিত রাখে। এটাও একটা আশ্চর্যের বিষয়, কেনই বা এক শ্রেণির অ্যান্টিবডি দেহে থাকবে যার উৎপাদন দমিয়ে রাখতে চাচ্ছি? অন্য কোন অ্যান্টিবডির ক্ষেত্রে তো এমন কোন নিয়ন্ত্রক নেই!
এই যে আরেক পান্ডা মাস্ট কোষ, আরো অনেক কোষ আছে যারা মাস্ট কোষের কাজ করে। মাস্ট কোষ না থাকায় ইমিউন সিস্টেম বিপদে পড়েছে সেটারও তেমন নজির পাওয়া যায়না। তার মানে কি এরা ইমিউন সিস্টেমে অন্যান্য অংশের তুলনায় কম প্রয়োজনীয়?
এটারও সঠিক উত্তর আমরা জানিনা। তবে আধুনিক ইমিউনলজির দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, IgE এবং সংযুক্ত অতিসক্রিয়তা সম্পর্কে জানি আর না জানি, এটা আছে, থাকবে। একটি সুরক্ষা ব্যবস্থা যেটা আমাদের হাজারো জীবাণু থেকে বাঁচিয়ে রাখছে, তাকে উপভোগের জন্য যে মূল্যগুলো আমাদের দিতে হয় তার মধ্যে অতিসক্রিয়তা একটা।
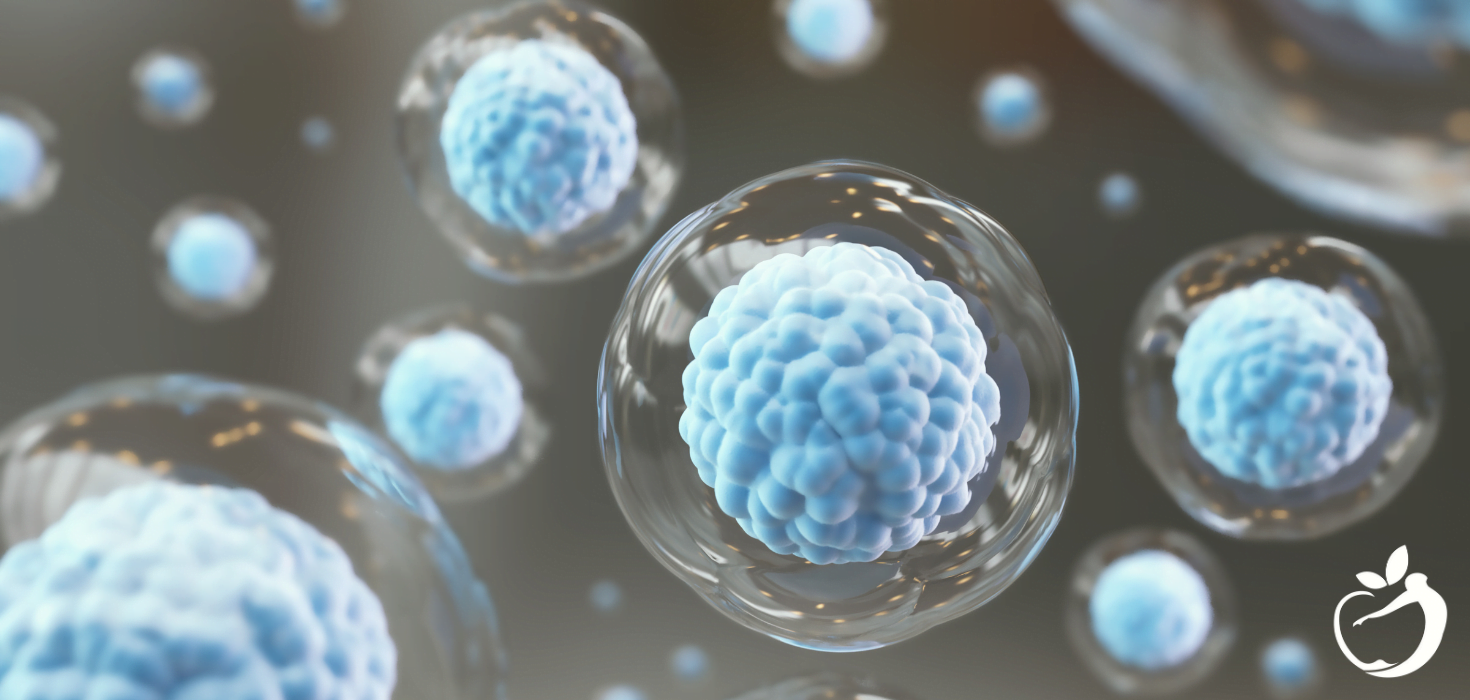
Leave a Reply