‘কোথায় কাজ? কি কাজ আছে মানুষের? অংক কষা, ইঞ্জিন বানানো, কবিতা লেখা? ওসব তো ভান, কাজের ছল। পৃথিবীতে কেউ ওসব চায়না। একদিন মানুষের জ্ঞান ছিল না, বিজ্ঞান ছিল না, সভ্যতা ছিলনা, মানুষের কিছু এসে যায় নি। আজ মানুষের ওসব আছে কিন্তু তাতেও কারো কিছু এসে যায়না। তার মধ্যে যে বিপুল শূন্যতা আছে সেটা তাকে ভরতেই হবে…’
–মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দিবারাত্রির কাব্য
এই শূন্যতা পূরনের আয়োজন চলছেই। মানুষের চাহিদা যেন বিশাল ব্ল্যাকহোলের মত। যদি শুধু ভালো দিকটাই দেখি, জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতায় উন্নতি তো কম হলোনা। উন্নতির এক পর্যায়ে মানুষ নিজের অক্ষমতা গুলো আর মেনে নিতে পারলোনা। আমরা মানুষেরা উড়তে পারিনা, তাই আমরা তৈরি করেছি উড়োজাহাজ; আমরা পানির নিচে শ্বাস নিতে পারিনা, তাই তৈরি করেছি ডুবোজাহাজ; আমরা মাথার মধ্যে বিশাল পরিমাণ তথ্য নিয়ে বিশ্লেষন করতে পারিনা, ফলশ্রুতিতে এসেছে কম্পিউটার। এই নানান রকম, নানান আকারের যন্ত্র আমাদের বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রকৌশলকে কৃতিত্বের সাথে এগিয়ে নিতে কাজে লাগছে।
যন্ত্র তৈরির সাথে সাথে আমরা সবসময়ই এমন কিছু খুঁজেছি যা আমাদের নিজেদের আরো গতিশীল, শক্তিশালী এবং চৌকশ করতে পারে। বর্তমানে বহু মানুষ ক্লান্তি এড়িয়ে কাজে মনযোগী হতে ক্যাফেইন এর ওপর নির্ভরশীল। চিন্তার অতল গভীরতা স্পর্শের জন্য কেউ কেউ নেশা জাতীয় দ্রব্যের সহায়তা(!)ও নিয়ে থাকেন। খেলাধূলার মত স্বাস্থ্যকর ক্ষেত্রেও নানা রকম আইনি ও বেআইনি বস্তুর ছড়াছড়ি যা ক্রীড়াবিদদের সর্বোচ্চ প্রদর্শনে, এমনকি নিজেকে ছাড়িয়ে যেতেও কাজে লাগে। বর্তমানে নতুন ধরনের কিছু বস্তু বা ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে যা মানসিক দক্ষতাকে বাড়িয়ে থাকে, সহজ ভাষায়- এরা আপনাকে স্মার্ট করে তোলে। তবে হরলিক্সের মত অতটা নয়(!)।
উদাহরণ হিসেবে কয়েকটা নাম বলা যায়, রিটালিন, মোডাফিনিল, অ্যাডেরাল। এই ধরনের ওষুধ তৈরি করা হয়েছিল আলঝেইমার, এডিএইচডি, ন্যাক্রোলেপ্সি এই ধরনের রোগের চিকিৎসার স্বার্থে ‘প্রেসক্রিপশন অনলি’ ব্যাবহারের জন্য। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে সুস্থ মানুষও এদের গ্রহন করছে মানসিক দক্ষতা বাড়ানোর জন্য। রিটালিন ব্যাবহার করছে মনযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে। যদিও এর সত্যিকারের প্রয়োগ অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাক্টিভিডি ডিসঅর্ডার(এডিএইচডি)এ। ন্যাক্রোলেপ্সি হল দিবানিদ্রার চক্রের সমস্যা যার ফলে মানুষ জেগে থাকার সময়ও ঘুমঘুম অনুভব করে। এই সমস্যার চিকিৎসার ব্যাবহার করা হয় মোডাফিনিল। সুস্থ মানুষেরাও এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গ্রহন করছেন আরো উদ্দীপ্ত এবং সতর্ক সময় কাটানোর আশায় । বিশেষ করে ছাত্ররা দীর্ঘ সময় পড়াশোনা করতে, শিফট-ওয়ার্কাররা চাঙ্গা থাকতে এবং ভ্রমণকারীরা জেটল্যাগ কাটাতে এ ধরণের ওষুধ ব্যাবহার করছেন। যদিও শিফট-ওয়ার্কার দের ক্ষেত্রে তাদের দিবা-নিদ্রার চক্রকে বশের আনার জন্য এরা কাজে দিচ্ছে, চিন্তার ব্যাপার এখানেই যদি তারা এসবের প্রতি বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, কিংবা যদি এই ধারনা পেয়ে বসে যে ঘুম ছাড়াই তারা চলতে পারবেন!

ন্যচার ১৪০০ মানুষের মধ্যে একটি সার্ভে পরিচালনা করে, তাদের মধ্যে ২০ শতাংশ এই ধরনের ওষুধ নন-মেডিক্যাল ইস্যুতে ব্যাবহারের কথা স্বীকার করেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে মগজের ওপর এসব ওষুধের প্রভাব এবং কার্যপ্রক্রিয়া বেশ মজার মনে হতে পারে। বিজ্ঞান অবশ্যই মজার তবে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রটাই মাঝে মাঝে ঝামেলা বাধায়। এই স্মার্ট ড্রাগ ও বেশ জটিল ধরনের নীতিগত দ্বন্দ্ব তৈরি করেছে। কেউ কেউ মনে করছেন, প্রকৃতি প্রদত্ত ক্ষমতাকে ‘টেম্পারিং’ করা কোনমতেই ঠিক নয়। শিক্ষার্থী কিংবা প্রতিযোগীতামূলক পেশাজীবিদের একটা অংশ যারা এ ধরনের স্মার্ট ড্রাগ ব্যবহার করছে, অন্যান্যদের পক্ষে তাদের সাথে পেরে ওঠা কঠিন হয়ে যাবে। ঠিক এরকম ঘটেছিল অ্যাথলেটিক্সএ বাধ্যতামূলক ড্রাগ টেস্টিং শুরু করার আগে ১৯৭০-৮০ সালে। যখন প্রতিযোগীতায় নামার জন্য স্টেরয়েড একরকম আবশ্যক হয়ে দাড়িয়েছিল। আবার কেউ বলছেন, প্রাপ্তবয়স্করা তাদের ইচ্ছেমত প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধের ব্যাবহার করতেই পারেন। যেসব কাজে দীর্ঘসময় সূক্ষ মনযোগের সাথে কাজ করতে হয়, যেমন সার্জন কিংবা পাইলটের চাকরীতে এই ‘স্মার্ট ড্রাগ’ ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারে এমন কথাও বলা হচ্ছে।
প্রতিযোগীতার বাজারে অন্যান্যদের থেকে এগিয়ে থাকতে কে না চায়? তাই শিক্ষার্থী, পেশাজীবি সবার মাঝেই এই ‘স্মার্ট ড্রাগ’ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অন্তত সেটাই মনে হয় বিভিন্ন ওয়েবসাইটে এই সংক্রান্ত লেখালেখি দেখে। অনেক ব্যাবহারকারী তার ব্যাক্তিগত ব্লগে এসবের সম্পর্কে চমৎকার লিখছেন, কিভাবে সংগ্রহ করা যায়, কিরকম মাত্রায় ব্যাবহার করতে হবে, অতিরিক্ত ব্যাবহারের ফলে কি ধরণের ক্ষতি হতে পারে সেসব জানাচ্ছেন। তবে এর ব্যাবহারের বিপক্ষেও কথা বলার লোক কম নয়। স্বল্পমেয়াদী ব্যাবহারে এর উল্লেখযোগ্য কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পাওয়া না গেলেও, দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের ফলে কোন সমস্যা হতে পারে কি না তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
যাই হোক, আশা কিংবা নিরাশার কথা এটাই যে- স্মার্ট ড্রাগ সংক্রান্ত যত খবর, সার্ভে, গবেষনা কিংবা ব্লগপোস্ট চোখে পড়ল, সবই যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রিক। অন্যান্য দেশে কি রকম কি অবস্থা তার সম্পর্কে তেমন কিছু জানা গেলোনা। তবে, যতদিন আমাদের দেশে পরীক্ষাগুলোতে প্রশ্নফাঁস এবং চাকরী-বাকরীতে মামার জোড় কার্যকর থাকবে, ততদিন আত্নোন্নয়নের এই হলিউডি পন্থা কিছুই করতে পারবেনা।






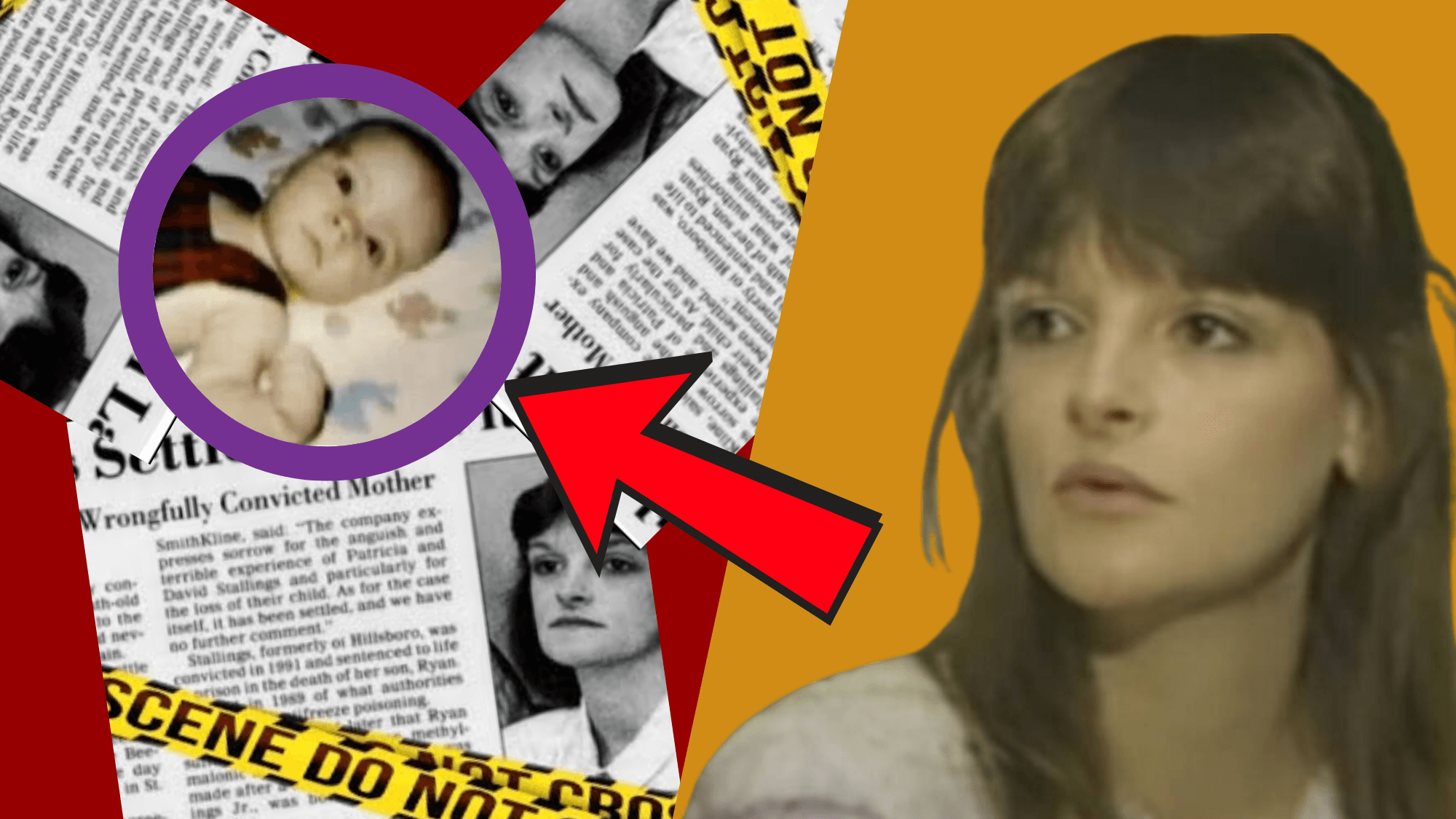

Leave a Reply