জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড নিয়ে দুই ধরণের কন্টেন্টের বড়ই অভাব ছিল! সে দু’টো হলো গাইডলাইন আর নমুনা প্রশ্ন। আমি ইতিমধ্যে একটা গাইডলাইন বিজ্ঞান ব্লগে লিখেছিলাম। এরপর সবাই অনুরোধ করায় নমুনা প্রশ্নের মিশনে নেমে গেলাম। এই পর্বে যে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা পূর্বে আমাদের ফেসবুকে গ্রুপে প্রকাশিত হয়েছিল।

১. কোষ জীবদেহের ক্ষুদ্রতম গাঠনিক একক, যেখানে প্রোটিন, রেজিন, আয়ন এবং অ্যাসিডসহ বিভিন্ন উপাদান সুষমভাবে অবস্থান করে। কিন্তু, কখনো কখনো কোষের মধ্যকার উপাদানের আধিক্য বা স্বল্পতার কারণে যাবতীয় কার্যক্রম ব্যহত হয়। একইভাবে সঠিক পরিমাণে কোষের বৃ্দ্ধি না ঘটলেও শারীরবৃত্তীয় কর্মকান্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
A. তোমার কোষে যদি রেজিনের পরিমাণ বৃধি পেয়ে প্রোটিনের চেয়েও বেশি প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে কোষ ক্ষতির সম্মুখীন হবে
B. একটি সাধারণ কোষকে একাধিক মাইক্রো অণু ও ম্যাক্রো অণুর সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে
C. আমাদের কোষে একাধিক অন্তঃকোষীয় মিথোজীবী উপস্থিত
D. কোষের অনিয়মিত বৃ্দ্ধির ক্ষেত্রে কখনোই কোনো অণুজীব দায়ী হতে পারে না
সমাধানঃ
A. প্রথমেই জানতে হবে, রেজিন কী? এটি আসলে কোষস্থ বর্জ্য পদার্থ। অন্যদিকে প্রোটিন হলো সঞ্চিত পদার্থ। যখনি কোষে রেজিনের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করবে, তখনি কোষের স্বাভাবিক কার্যক্রমের গতি কমতে থাকবে। আর যদি কোনোভাবে প্রোটিনের চেয়েও বেশি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, তাহলে কোষ পুরোপুরি অসুস্থ হয়ে পড়বে। সুতরাং, এই অপশনটি True.
B. কোষের প্রোটোপ্লাজমে Amino Acid ও মনোস্যাকারাইডের মতো মাইক্রো অণু এবং প্রোটিন, লিপিড ও পলিস্যাকারাইডের মতো ম্যাক্রো অণু বিদ্যমান। সুতরাং, এই অপশনটি True.
C. অন্তঃকোষীয় মিথোজীবী কী? যদি কোনো পরনির্ভরশীল জীব অপর একটি জীবের কোষের মধ্যে অবস্থান করে এবং সে নিজে অথবা ঐ কোষটি যদি প্রভাবিত হয়, তবে ঐ পরনির্ভরশীল জীবটিকে অন্তঃকোষীয় মিথোজীবী বলা হয়। এমনি দু’টি অন্তঃকোষীয় মিথোজীবী হলো মাইটোকন্ড্রিয়ন ও প্লাস্টিড। শুনে অবাক হলে? বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এই দু’টিকে মনেরা রাজ্য বা ব্যাকটেরিয়া ডোমেনের অধিবাসী স্বতন্ত্র জীব হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর পেছনে বিশাল কারণ রয়েছে।
যাহোক, এ দু’টি কোষীয় অংশ কোষাভ্যন্তরে অবস্থান করে নিজে উপকৃ্ত হয় এবং কোষকে সহযোগিতার মাধ্যমে উৎকৃ্ষ্ট মানের সিমবায়োসিস ঘটায়, যাকে আমরা Mutualism বলে থাকি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই অপশনটি True.
D. দেখো, প্যাপিলোমা ভাইরাস একটি ক্ষতিকর অণুজীব। এই ভাইরাসের E6 এবং E7 নামের দু’টি জিন এমন কিছু প্রোটিন তৈরি করে, যা কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রণকারী প্রোটিন অণুসমূহকে স্থানচ্যুত করে। এর ফলে কোষের অস্বাভাবিক বৃ্দ্ধি ঘটে। সুতরাং, এই অপশনটি False.

২. X- একটি প্রজাতির পপুলেশন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত হয়ে যায় এবং বিচ্ছিন্ন পপুলেশনগুলোর মধ্যে আন্তঃপ্রজনন বাধাগ্রস্ত হয়
Y- দেহকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা বা অবস্থানের পরিবর্তন
Z- অঙ্গসংস্থানিক, শারীরবৃত্তীয় বা বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যের আকষ্মিক পরিবর্তন
A. X যদি সম্পূ্র্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে Z দেখা দিতে পারে
B. Y এর কারণে জিনে প্রভাব পড়ে না
C. Z এর ফলে জিন ও ক্রোমোজোমে পরিবর্তন সংঘটিত হয়
D. X, Y ও Z প্রজাতি সৃষ্টির অন্যতম প্রধান তিনটি কারণ
সমাধানঃ
A. “X” হলো অন্তরণ বা Isolation. এটি যখন পুরো মাত্রায় অর্জিত হয় বা সম্পাদিত হয়, তখন উপপ্রজাতিতে জিন ও ক্রোমোজোম পর্যায়ে মিউটেশন সংঘটিত হয়। এই মিউটেশনের ফলে হঠাৎই বংশগতীয়, অঙ্গসংস্থানিক বা শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন সংঘটিত হয়, যা Z এর প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ, X এর সাথে Z এর সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং, এই অপশনটি True.
B. “Y” বলছে, “আমি ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন”। আমরা জানি, এই প্রক্রিয়ার ফলে ক্রোমোজোমের সংখ্যা বা অবস্থানের হ্রাস-বৃ্দ্ধি বা পরিবর্তন দেখা দেয় কিংবা এক বা একাধিক ক্রোমোজোমের জিনের সংখ্যা বা অবস্থান পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, জিন প্রভাবিত হচ্ছেই। সুতরাং, এই অপশনটি False.
C. আগেই বলেছি, Z হলো মিউটেশন, যা দুইভাবে সংঘটিত হতে পারেঃ জিনের ভেতরে পরিবর্তন এবং ক্রোমোজোমাল পরিবর্তন। অতএব, এই অপশনটি True.
D. X, Y ও Z হলো যথাক্রমে অন্তরণ (Isolation), ক্রোমোজোমাল অ্য়াবারেশন (Chromosomal Aberration) ও পরিব্যক্তি (Mutation). উদ্দীপকের তথ্যসমূহকে বিশ্লেষণ করলেই D অপশনের যথার্থতা নিরূপণ করা সম্ভব হবে।
অন্তরণের ফলে আন্তঃপ্রজনন বাধাগ্রস্ত হয়। এর ফলে প্রতিটি গোষ্ঠী এক একটি প্রজাতিতে রূপ নেয়। ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশনের ফলে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের জন্ম হয়, যা বিবর্তনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এটিই অভিব্যক্তির ধারায় নতুন প্রজাতির উৎপত্তির কারণ। মিউটেশন প্রাকৃ্তিক নির্বাচন ও জেনেটিক রিকম্বিনেশনের সাথে একত্রে একাধিক জীবে এমন প্রভাব ফেলে যে তাদের জিন ও ক্রোমোজোমে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই পরিবর্তনের ফলে জীবেরা পরস্পর থেকে এতটাই আলাদা হয়ে যায় যে, তারা আন্তঃপ্রজননে অংশগ্রহণ করতে পারে না। পরবর্তীতে তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
অর্থাৎ, প্রজাতির উৎপত্তিতে X, Y ও Z অন্যতম তিনটি অনুঘটক। সুতরাং, এই অপশনটি True.

৩. জৈব বিবর্তনের ফলে সুশৃঙ্খল অথচ ক্রমিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবের সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থা বা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়। মিউটেশন ও প্রজাতির উৎপত্তির উপর ভিত্তি করে একে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা সম্ভব। এ ধরণের অভিব্যক্তির স্বপক্ষে বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীরা বেশ কয়েকটি প্রমাণ পেয়েছেন।
A. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিউটেশনের প্রভাবে জৈব বিবর্তন সংঘটিত হওয়া অসম্ভব
B. জৈব বিবর্তনের মাধ্যমে জীবেরা প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতা অর্জন করে
C. বিবর্তনের ধারায় একই পূর্বপুরুষ হতে উদ্ভূত বংশধরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা দিতে পারে
D. সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো আসলে জৈব অভিব্যক্তির সত্যতার জন্য যথেষ্ট নয়।
সমাধানঃ
A. জৈব বিবর্তনের ৩টি মূল পর্যায় রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো “মাইক্রোবিবর্তন”। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিউটেশনের প্রভাবে যে বিবর্তন ঘটে, সেটাই মাইক্রোবিবর্তন বা Micro-evolution. এর ফলে আন্তঃপ্রজননশীল পপুলেশনে ধারাবাহিক ও ছোট ছোট পরিবর্তন ঘটে। এর মাধ্যমে প্রজাতির অধঃস্তন ট্যাক্সনের উৎপত্তি ঘটে। সুতরাং, এই অপশনটি False.
B. জৈব বিবর্তন হলো জীবদের নতুন বা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটার একটি পদ্ধতি। আর এটা ঘটে প্রয়োজনের সাপেক্ষে অর্থাৎ পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য, যেটাকে অভিযোজন বলে। সুতরাং, এই অপশনটি True.
C. সাধারণত একই পূর্বপুরুষ হতে উদ্ভূত বংশধরদের বৈশিষ্ট্যে সাদৃশ্য থাকে। কিন্তু, ভিন্ন ভিন্ন বাস্তুসংস্থানে যদি তারা বিভক্ত হয়ে যায়, তাহলে এদের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকশিত হবে। অর্থাৎ, পরস্পরের মধ্যে বড় ধরণের তফাৎ সৃষ্টি হবে। এ ধরণের অভিযোজনিক বিচ্ছুরণের কারণে সৃষ্ট বিবর্তনকে অপসারী বিবর্তন বা Divergent Evolution বলে। সুতরাং, এই অপশনটি True.
D. জৈব অভিব্যক্তির পক্ষে এতো প্রমাণ পাওয়া গেছে যে সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখলেও একটা বই তৈরি করা সম্ভব হবে। প্রমাণগুলো বিভিন্ন ধরণের। যেমনঃ অঙ্গসংস্থানিক, ভ্রূনতত্ত্বীয়, বংশগতীয়, জীবভৌগোলিক, প্রত্নজীবতত্ত্বীয়, কোষতত্ত্বীয়, শ্রেণিবিন্যাসগত, প্রাণরাসায়নিক ইত্যাদি। অর্থাৎ, জীবদের মধ্যকার সবকিছুকে জৈব বিবর্তনের আলোচনা দ্বারা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। একারণে এখন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে জীবজগতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সংঘটিত হয়, যা বংশ পরম্পরায় বাহিত হতে পারে। তাহলে, এই অপশনটা True.
এই লেখাটাতে আমি ৩টি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি যে কীভাবে প্রশ্নের অপশন গুলো নিয়ে ভাবতে হয়। পরের পর্বতেও এরকম কিছু প্রশ্ন অপারেশন করব।
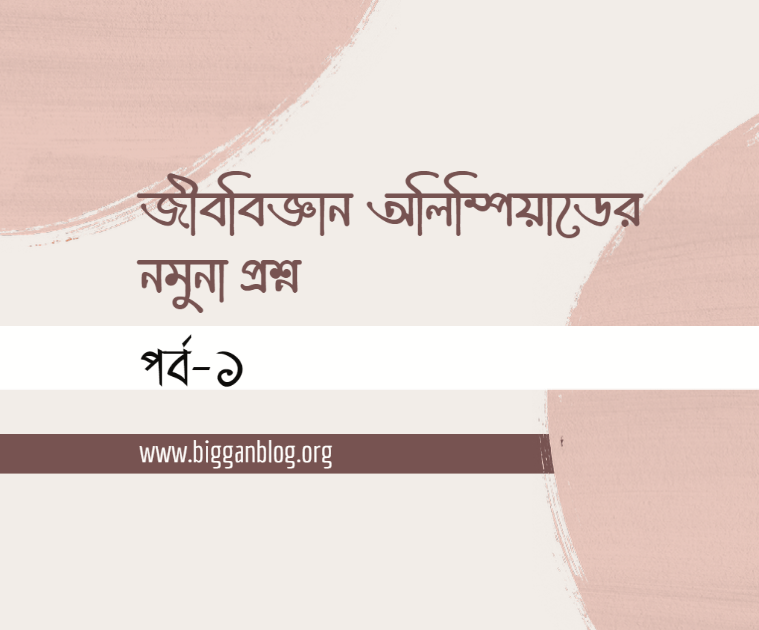
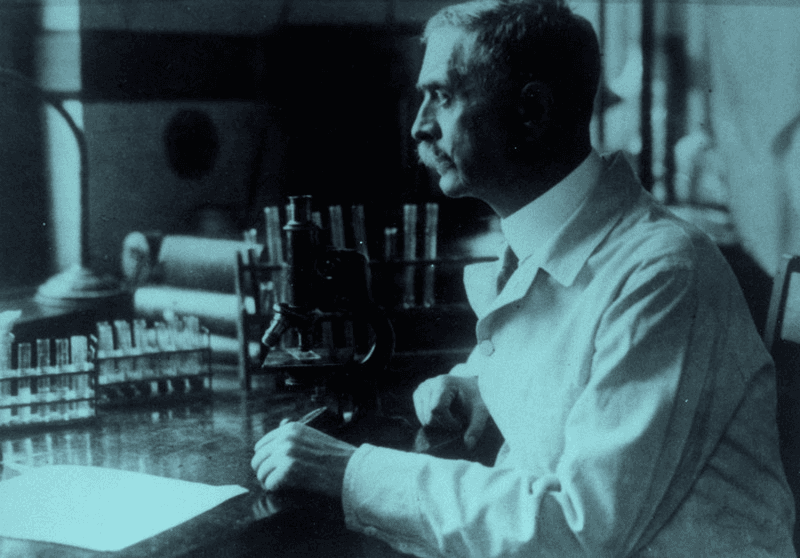






Leave a Reply