জীবমাত্র বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য গ্রহণ করে। বাস্তুতন্ত্রের প্রধান উৎপাদক উদ্ভিদ এবং খাদক প্রাণীদের খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া ভিন্ন। উদ্ভিদ তার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য কতগুলো উপাদান মাটি,পানি আর বাতাস থেকে গ্রহণ করে। এদের মধ্যে বিশেষ নয়টি উপাদান তার স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বেশি পরিমাণে দরকার হয়, যাদেরকে বলা হয় ম্যাক্রো-পুষ্টি উপাদান। নাইট্রোজেন তাদের মধ্যে অন্যতম। নাইট্রোজেন নিউক্লিক এসিড (অন্য কথায় কোষের ডিএনএ/আরএনএ), প্রোটিন আর ক্লোরোফিলের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এজন্য মাটিতে নাইট্রোজেন মাত্রা কতটুকু—তা-ই অনেকাংশে নির্ধারণ করে দেয় জমির ফলন কেমন হবে। আমাদের দেহেও নাইট্রোজেন সমানভাবে দরকারি। উদ্ভিদ কিংবা তৃণভোজী বিভিন্ন প্রাণীকে খাওয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের নাইট্রোজেনের চাহিদা পূরণ করি।
কিন্তু মাটিস্থ অন্য সকল দরকারি জিনিসের মতো নাইট্রোজেনের পরিমাণও সীমিত। উদ্ভিদকর্তৃক শোষণের ফলে নাইট্রোজেন যদি ফুরাতে শুরু করে, তাহলে জমিতে ফসল হবে না। ফসল না জন্মালে না খেতে পেয়ে মরবে পৃথিবীর মানুষ। উনিশ শতক থেকেই বিজ্ঞানীরা এই আসন্ন সঙ্কটের ব্যাপারে অবহিত ছিলেন এবং এর সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছিলেন।

নাইট্রোজেন-ঘাটতি মেটানোর অবধারিত সমাধানটি হলো মাটিতে আবার নাইট্রোজেন যোগ করা। সে-কালে যখন জল-স্থল-অন্তরীক্ষে যানবাহনের প্রযুক্তি উন্নত হচ্ছিলো,মানুষ আবিষ্কার করছিলো নানা অজানা জায়গা। দক্ষিণ আমেরিকার বেশ কিছু দ্বীপ আবিষ্কারের পর দেখা গেলো সেসব জায়গায় পাখির মল বছরের পর বছর ধরে জমে বিশাল পাহাড়ের মতো স্তূপ তৈরি করেছে। দেখা গেলো এই বস্তুটি বেশ ভালো রকম নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ। এসব স্তূপ থেকে প্রক্রিয়াকরণ এর পর পাওয়া যেত একরকম সার, যাকে বলে গুয়ানো। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই গুয়ানোর বাণিজ্য রমরমা হয়ে উঠেছিলো, এমনকি দ্বীপ দখলের নেশায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো একে অপরের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়েছিলো। বাণিজ্যযুদ্ধ এবং শক্তিশালী দেশগুলোর কাড়াকাড়ির ফলে খুব দ্রুত এই গুয়ানো’র সংগ্রহ’ও ফুরিয়ে এলো। ১৮৯৮ সালে, বিলেতের এক মশহুর রসায়নবিদ উইলিয়াম ক্রুকস এই নাইট্রোজেন-সংকট নিয়ে এক আগ্রহোদ্দীপক মন্তব্য করেছিলেন-
“[খুব দ্রুতই] আমরা এক মারাত্মক খাদ্যসংকটের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি।….এ-অবস্থা থেকে রসায়নবিদেরাই পৃথিবীকে উদ্ধার করতে পারেন। আসন্ন দুর্ভিক্ষকে কীভাবে প্রাচুর্যের উৎসবে পরিণত করা যায় এই ফয়সালা হবে ল্যাবরেটরিতে।”
বাতাসের প্রায় ৭৮% হলো নাইট্রোজেন গ্যাস। কিন্তু এই নাইট্রোজেন জীবকুলের ব্যবহার যোগ্য নয়। খুব শক্তিশালী ত্রিবন্ধনের দ্বারা যে অণুর উৎপত্তি, তাকে ভাঙা সহজ কাজ নয়। প্রাকৃতিকভাবে দুটো প্রক্রিয়ায় এই ভাঙন হতে পারে। (এক) বজ্রপাতের সময় বিদ্যুৎ ক্ষরণের ফলে প্রায় ৩০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তৈরি হতে পারে। এই তাপমাত্রায় নাইট্রোজেনের ত্রিবন্ধন ভেঙে নাইট্রোজেনের অক্সাইড যৌগ গঠিত হয়। যেমন NO (নাইট্রিক অক্সাইড), NO2 (নাইট্রোজেন-ডাই অক্সাইড)। এই গ্যাসগুলো বৃষ্টির পানির সাথে মিশে মাটিতে পড়ে এবং নাইট্রেট লবণ হিশেবে মাটিতে মিশে যায়। (দুই) Azotobacter, Beijerinckia, Rhodospirillum, Rhizobium প্রভৃতি ‘নাইট্রিফাইং’ ব্যাকটেরিয়া তাদের বিশেষ এনজাইম সহযোগে নাইট্রোজেনকে বিজারিত করে অ্যামোনিয়া(NH3) তে পরিণত করতে পারে। এই অ্যামোনিয়া আরো কিছু জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ার পর উদ্ভিদের শোষণযোগ্য নাইট্রেট আয়নে পরিণত হয়।
এই দুই প্রক্রিয়ার সমস্যা হচ্ছে এরা হয় অনিশ্চিত অথবা ধীর। মাটিতে নাইট্রোজেন ফেরানোর ব্যবস্থা এভাবে চলবে না। রসায়নবিদেরা সচেষ্ট হলেন কীভাবে বাতাসের নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন এর বিক্রিয়া করিয়ে ব্যবহারযোগ্য নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধযৌগ অ্যামোনিয়া তৈরি করা যায়। কিন্তু এ প্রক্রিয়া সফল হলো না। তাপ, চাপ ইত্যাদি বিক্রিয়ার বিভিন্ন ‘ফ্যাক্টর’ পৃথকভাবে বদল করেও তেমন সুফল পাওয়া গেলো না। এই সমস্যার সমাধান করলেন ইহুদি বংশোদ্ভূত জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রিটজ হেবার। বিশ শতকের শুরুতে ভৌত রসায়নে উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত হেবার যখন এই কাজে হাত দিলেন, তখন তার পেছনে শত বিজ্ঞানীর ব্যর্থতার ইতিহাস। তার বয়স ছত্রিশ; তার বিদুষী স্ত্রী ক্লারা রসায়নশাস্ত্রে সেসময়ের বিরল নারী ডক্টরেটদের একজন। দীর্ঘ পাঁচ বছর হেবার অ্যামোনিয়া তৈরির চেষ্টা করে গেলেন।

তার পরিকল্পনা ছিলো নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেনকে আলাদা নয়, একইসাথে বিক্রিয়া করাতে হবে উচ্চ চাপ আর উচ্চ তাপমাত্রায়; সাথে থাকবে উপযুক্ত কোনো প্রভাবক, যা বিক্রিয়ার সক্রিয়ন শক্তি কমিয়ে আনবে। মজবুত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে হেবার চালাতে লাগলেন তার পরীক্ষা। প্রাথমিকভাবে প্রভাবক হিসেবে হেবার ব্যবহার করেছিলেন দুর্মূল্য ধাতু অসমিয়াম (Os)। ১৯০৮ সনে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। প্রায় ২০০ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ (atm) এবং ৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ভাঙলো নাইট্রোজেনের সুস্থিত ত্রিবন্ধন; পারমাণবিক নাইট্রোজেন অপর তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হলো, শীতলীকৃত গ্যাস মিশ্রণ থেকে নল বেয়ে বিকারে জমা হলো এক ফোঁটা অ্যামোনিয়া। আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর পর পৃথিবীবাসীর সামনে হেবার প্রকাশ করলেন তাঁর আবিষ্কার। কার্ল বশ পরের বছর অ্যামোনিয়ার বৃহৎ পরিসরে শিল্পোৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। অসমিয়ামের পরিবর্তে এলো সস্তা লোহা-ভিত্তিক প্রভাবক। এই দুই বিজ্ঞানীর নাম মিলিয়ে অ্যামোনিয়ার শিল্পোৎপাদন পদ্ধতির নাম হয়ে গেলো হেবার-বশ প্রণালি।
জার্মানির সবচেয়ে বড়ো রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিএএসএফ চার বছরের মধ্যে এমন এক কারখানা (ওপাউ প্ল্যান্ট) বসালো যেখান থেকে প্রতি দিন প্রায় পাঁচ টন অ্যামোনিয়া উৎপাদন করা যায়। অ্যামোনিয়ার সুলভ উৎপাদন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নাইট্রোজেন-ভিত্তিক সার (যেমন ইউরিয়া)-এর ব্যবহার বেড়ে গেলো। সার ব্যবহার করে কৃষকেরা একই জমিতে পূর্বের তুলনায় চারগুণ ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হলেন। সুরক্ষিত হলো খাদ্য নিরাপত্তা, সভ্যতা এগোলো অগ্রগমনের পথে। বলা যেতেই পারে আমরা সকলে অন্তত পরোক্ষভাবে জীবনধারণের জন্য হেবারের এই আবিষ্কারের কাছে ঋণী। বিজ্ঞানের ইতিহাস যারা রচনা করেছেন, তারা অনেকেই হেবার-বশ প্রণালিকে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন বলে উল্লেখ করেছেন।

এই আবিষ্কার হেবারকে রাতারাতি ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত করলো। তিনি বনে গেলেন কাইজার-উইলহেলম বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। বিদ্যায়তনিক জগতে তার সুনাম বেড়ে গেলো। সেসময়ে জার্মানি ছিলো বিজ্ঞান-জগতের অসংখ্য শ্রেষ্ঠ মনীষার পীঠস্থান। আলবার্ট আইনস্টাইন, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, ম্যাক্স বর্ন’দের সভায় হেবারের আনাগোনা বাড়লো। বর্নের সাথে ১৯১৯ সালে তিনি প্রস্তাব করলেন বর্ন-হেবার চক্রের, যার মাধ্যমে আয়নিক যৌগের কেলাসের ‘ল্যাটিস’ শক্তি সহজে হিসাব করা যায়। ১৯১৮ সালে রসায়নে হেবার নোবেল পুরস্কার পান। কিন্তু যখন তিনি নোবেল পেলেন, তখন তার অনেক সহকর্মী এবং প্রাক্তন নোবেল-বিজয়ী তার পুরষ্কার-প্রাপ্তি অনুষ্ঠানে আসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তার নোবেল প্রাপ্তি নিয়ে উঠেছিলো সমালোচনার ঝড়। কেন? ইতিহাস-সচেতন পাঠকের মনে থাকবে সময়টা তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের!
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হেবারের দেশ জার্মানি ছিল কেন্দ্রীয় শক্তিতে, তাদের সাথে ছিলো বুলগেরিয়া, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি ও অটোম্যান সাম্রাজ্য। আর বিপরীতে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশের সমন্বয়ে মিত্রশক্তি। হেবার চেয়েছিলেন তার মেধা-বুদ্ধি দেশের দুঃসময়ে কাজে লাগাতে। যুদ্ধের কয়েক মাসের মধ্যেই জার্মানির গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক ফুরিয়ে যেতে লাগলো। হেবার দেখলেন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট চমৎকার সার হিসেবে যেমন কাজ করতে পারে, তেমনি এর থেকে ঘটতে পারে বিস্ফোরণ (২০২০ সালে বৈরুতে বিস্ফোরণের কথা স্মর্তব্য)। হেবার প্রণালী প্রথম যে কারখানায় বড় পরিসরে ব্যবহার করা হয়েছিলো, সেই ওপাউ প্ল্যান্ট’ও ১৯২১ সালে বিস্ফোরণের শিকার হয়েছিলো। যুদ্ধকালীন সময়ে হেবার পরামর্শ দিলেন সারের জন্য যেসব কারখানায় অ্যামোনিয়া তৈরি করা হচ্ছে, সেগুলোতে যেন বিস্ফোরক নাইট্রেট তৈরির কাজ শুরু করা হয়। প্রথমে জার্মান সেনাবাহিনীর উচ্চপর্যায়ের কর্তাব্যক্তিরা হেবারের পরামর্শ মানতে চায় নি, কিন্তু একসময় তার শাণিত বৈজ্ঞানিক মগজের কাছে তাদের পরাজয় মানতে হয়।

কিন্তু এত পরিকল্পনার পরেও খুব একটা সুবিধা হয়নি জার্মানির। মিত্রবাহিনীর কাছেও রয়েছে একই প্রযুক্তি, বরং তাদের সৈন্যসংখ্যা ঢের বেশি। স্বাভাবিক রণনীতি (হেগ চুক্তি,১৮৯৯) ভেঙে যুদ্ধরত দুই পক্ষই তখন রাসায়নিক অস্ত্রের পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও প্রয়োগের দিকে ঝুঁকছে। হেবার জার্মানির পক্ষে রাসায়নিক অস্ত্র পরিকল্পনার দায়িত্ব নিলেন। তার পরিকল্পনা ছিলো এমন একটা গ্যাস ব্যবহার করা যা কম ঘনমাত্রাতেও ভীষণ মারণঘাতী হবে, আবার বাতাসের চেয়ে ভারী হবে যাতে শত্রুপক্ষের ট্রেঞ্চে ঢুকে পড়তে পারে। ক্লোরিন গ্যাস এ-কাজে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলো।

১৯১৫ সালের ২২শে এপ্রিল বেলজিয়ামের ইপ্রা (Ypres) শহরে সন্ধ্যায় যখন বাতাস শত্রুবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে বইতে শুরু করেছে, হেবারের নির্দেশে জার্মান বাহিনী কয়েক হাজার সিলিন্ডার থেকে ছড়িয়ে দিলো প্রায় দেড়শ টন ক্লোরিন গ্যাস। সবুজাভ হলুদ রঙের কুয়াশার মতো ক্লোরিন গ্যাসের স্তর যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা মৃতদেহের উপর দিয়ে চলে গেল মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের দিকে। এই গ্যাস প্রশ্বাসে গ্রহণ করা মাত্রই মরণযন্ত্রণায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সৈন্যরা। তাদের দেহে যে প্রতিক্রিয়া শুরু হলো, চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় তাকে বলা হয় পালমোনারি ইডিমা। এই সমস্যায় ফুসফুসের আবরণ এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে সেখানে তরল জমতে থাকে। ফলত ফুসফুসের অ্যালভিওলাই আর রক্তনালিগুলো ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো, মুখ থেকে গলগল করে রক্ত বের হওয়ার আগে হলুদ মিউকাসে ভেসে গেলো তাদের চেহারা। প্রথম আক্রমণে প্রাণ গেল মিত্রশক্তির প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি সৈন্যের। ইতিহাসে এই ঘটনা ‘সেকেন্ড ব্যাটল অব ইপ্রা’ বলে চিহ্নিত। আর হেবার পরিচিত হলেন রাসায়নিক যুদ্ধের জনক হিসেবে। জানা যায়, হেবারের হাতে বিজ্ঞানের এই বিভীষিকাময় প্রয়োগ মারাত্মক ব্যথিত করেছিলো স্ত্রী ক্লারা’কে। এবং তিনি বেছে নিয়েছিলেন আত্মহননের পথ।
হেবারের শেষ পরিণতি
হেবারকে পদোন্নতি দিয়ে জার্মান বাহিনীর ক্যাপ্টেন বানানো হলো। যুদ্ধের বাকি সময়টায় হেবার জার্মান বাহিনীর জন্য বিশেষ মাস্ক এবং আরো রাসায়নিক অস্ত্র তৈরিতে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু মিত্রশক্তির বিজয় ঠেকানো গেলো না। উল্টো অপমানজনক ভার্সাই চুক্তির ফাঁদে পড়ে জার্মানিতে দেখা দিলো মুদ্রার মারাত্মক দরপতন ও আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা। হেবারের বিত্তলাভ যেমন ছিল আকস্মিক, তেমনই তা মিলিয়ে গেলো প্রবল মুদ্রাস্ফীতির করাল গ্রাসে। জার্মানির যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে হেবার সাগরের পানি ছেঁকে সোনা বের করার উপায় খুঁজতে থাকলেন। কিন্তু খালি হাতেই ফিরতে হলো তাকে।

হেবারের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়লো যখন হিটলারের নাৎসি বাহিনী ১৯৩৩ সালে জার্মানির ক্ষমতায় আরোহণ করলো। তার হাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কাইজার উইলহেম বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট তখন ইহুদি বিজ্ঞানীদের আঁতুড়ঘর। ইহুদি-বিদ্বেষী হিটলার সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে থেকে সমস্ত ইহুদিকে প্রত্যাহারের আদেশ জারি করলেন। হেবার পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন ইউরোপের এমাথা থেকে ওমাথা। কিন্তু সেসব দেশে তাকে চিহ্নিত করা হলো দুশমন যুদ্ধপরাধী হিসেবে। ১৯৩৪ সালে ৬৫ বছর বয়সে সুইজারল্যান্ডের বাজেল শহরে এক হোটেলে হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান এই নোবেল বিজয়ী রসায়নবিদ। আরো কয়েক বছর বেঁচে থাকলে হেবার দেখতে পেতেন, তাঁর তৈরি গ্যাসীয় কীটনাশকের (জাইক্লন বি) ফরমুলা বদলে কীভাবে তার প্রিয় রাষ্ট্র হত্যা করেছিলো বন্দি-শিবিরে আটকে থাকা হেবারের স্বজন-বন্ধুসহ কয়েক লক্ষ ইহুদিকে।
নায়ক নাকি খলনায়ক
ফ্রিটজ হেবারের জীবন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বিজ্ঞান শুধুই সত্য খোঁজার পথ। এর সাথে স্বভাবগত কোনো ভালো বা মন্দের ব্যাপার জড়িত নেই। উপরের বিবরণ পড়ে হয়তো খুব সহজেই পৃথিবীর মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাঁকে নায়ক বলে ফেলা যাবে, কিংবা ভয়াবহ রাসায়নিক অস্ত্রের উদ্ভাবনের জন্য দাগিয়ে দেওয়া যাবে খলনায়ক বলে। কিন্তু এর কোনোটাই হয়তো সুবিচার হবে না তার প্রতি। এই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে আরেকভাবে হয়তো তাঁকে দেখা যেতে পারে, যেখানে ব্যক্তি ফ্রিটজ হেবার আর গুরুত্বপূর্ণ নন। বিজ্ঞান কোনো একক ব্যক্তির আকস্মিক আবিষ্কারের ব্যাপার নয়, বিজ্ঞান হলো জ্ঞান উৎপাদন ও তার ব্যবহারের এক পরম্পরা। হেবার না করলে অন্য কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই বাতাসের নাইট্রোজেন কাজে লাগানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করতেন, হয়তো তাতে সময় কিছু বেশি লাগতো। আর রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার তো তখন দুই তরফেই চলছিলোই।

গত কয়েক শতাব্দী ধরে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সুবাদে আমাদের জীবন, আমাদের সভ্যতা অনেক দূর এগিয়ে গেছে; তার সাথে জন্ম নিয়েছে খোদ মানুষকে ধ্বংস করার জন্যেই নানান সব ব্যবস্থা। আমরা হয়তো খুব সহজেই বলে ফেলতে পারি বিজ্ঞানীরা যেন শুধু ওইসব সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামান, যেগুলো সরাসরি মানবসভ্যতার সমৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু বাস্তবতাটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিশ্রুত প্রতিটি জ্ঞান, প্রতিটি তথ্য, প্রতিটি ধারণাই আসলে একেকটা সম্ভাব্য দুমুখো ধারালো তলোয়ার। আজ যে গবেষণা হচ্ছে, সম্ভবত সেই গবেষকও বলতে পারেন না কিছু বছর বা ধরা যাক কিছু দশক পরে এর ব্যবহার কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এ কথা সেই আলফ্রেড নোবেলের ডিনামাইট কিংবা ফ্রিটজ হেবারের অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট—দুই ক্ষেত্রেই সত্যি। হেবারের জীবনচরিত আমাদের সেই চূড়ান্ত প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়—কীভাবে আমরা প্রাকৃতিক জগতকে নিয়ে আমাদের জানোশোনা এবং তার ওপর আমাদের সফল নিয়ন্ত্রণ জারি রাখতে পারি, নিজেদের ও প্রাণ-প্রকৃতি-প্রতিবেশের ক্ষতি না করে?
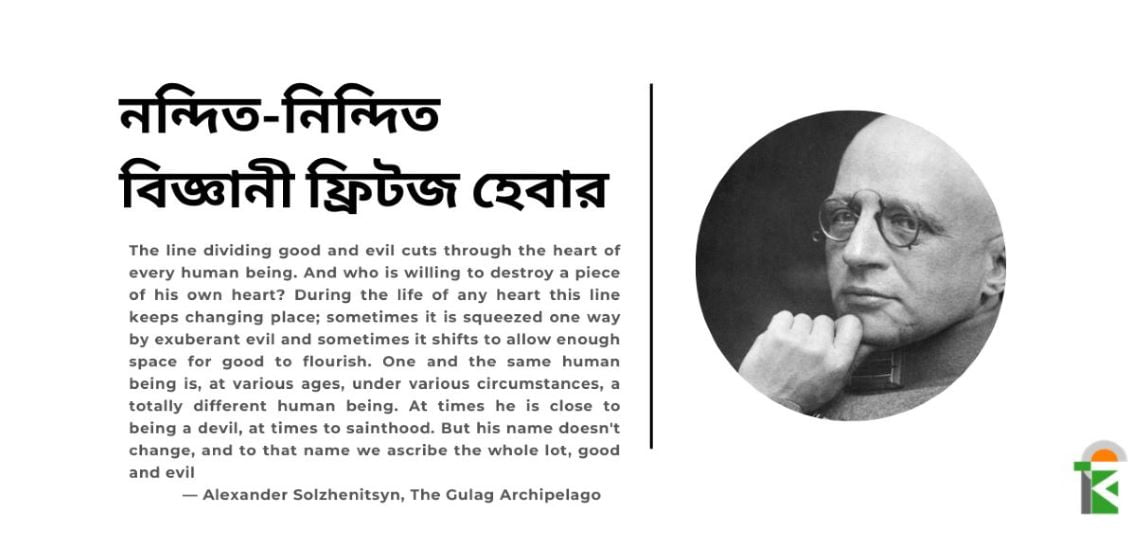
Leave a Reply